

জুন
২০২৫

প্রচ্ছদঃ সুরজিত সিনহা
লেখক/লেখিকাবৃন্দ

শারদীয়া ১৪৩২
পুজো সংখ্যার জন্য লেখা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
Email: maadhukariarticles@gmail.com
প্রচ্ছদ - সুরজিৎ সিনহা

পথশিশু
সঞ্জীব হালদার
শ্রীনগর, পূর্বপাড়া, কলকাতা
অনুগল্প

সোনারপুর প্লাটফর্মের টিকিট কাউন্টারের ধারে এক বছর তিন কি চারের শিশুকে রোজই দেখি মায়ের কোলে করে মার্বেলের মেঝেতে বসে আছে। শিশুটির মা নিত্যযাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে। একদিন শিশুটি দেখি মায়ের পাশে বসে পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। দেখে মনে হল খিদে ও অপুষ্টিতে ভুগছে। আমি একটি বিস্কুটের প্যাকেট শিশুটির হাতে দিলাম। মাঝেমধ্যে যখনই এদিকে আসি ঐ শিশুটিকে ওখানেই দেখি মায়ের কোলে বসে আছে। আমিও তাকে প্রতিবার কোনও না কোনও খাবার কিনে দিয়ে যাই। সেবার দূর্গা পূজোয় আমার এক সহকর্মী শিশুটিকে নতুন জামা দিয়েছিল। এভাবে শিশুটির প্রতি কেমন যেন মায়া জন্মে গেল এক বছরের মধ্যে। আরও এক দুমাস পর হঠাৎ করে ঐ প্লাটফর্মের টিকিট কাউন্টারের ধারে কাছে শিশুটিকে আর দেখা গেল না। আমি আরও বার দুয়েক ঐ স্থানে আসলাম কিন্তু কোনও খোঁজ পেলাম না শিশুটির। আশপাশের দোকানীরাও কোনও খোঁজ দিতে পারল না। একরাতে দুঃস্বপ্নে দেখি প্লাটফর্মের অদূরেই এক পার্কের পাশের রাস্তায় শিশুটি না খেতে পেয়ে মারা গেছে। আমি ঘুমের
মধ্যে চেঁচিয়ে উঠি, “অসম্ভব।” বছর দুই ঐ প্লাটফর্মে আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না। একদিন আমার ঐ সহকর্মীর আমন্ত্রণে আবার সোনারপুর যাওয়া হল। সেই টিকিট কাউন্টারের ধারে নতুন এক শিশু ও তার মা বসে আছে ভিক্ষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। আমি একটি পাঁচ টাকার কয়েন নিয়ে যখনই হাত বাড়িয়ে দিতে যাব তখনই ছেঁড়া প্যান্ট পরা খালি পায়ে বছর ছয়েকের এক ছেলে এসে আমার হাতটা ধরে বলল, "কাকু ভালো আছো?”
“অনেকদিন পরে এলে? আমায় বিস্কুট দেবে না?"
আমি হতভম্ব হয়ে মৃদু কন্ঠে বললাম,
"তুই কি করে জানলি আমি বিস্কুট দেবো?" ছেলেটি শুধু বলল, “আমি জানি।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তুই কোথায় থাকিস?” সে বলল,
“ঐ যে পার্কের ধারে ঝুপড়িতে থাকি কাকু।"
আমি বিষণ্ণমনে চেয়ে রইলাম প্লাটফর্মের গাড়িটার দিকে। ছেলেটি কখন যেন চলে গেছে। আমাদের দেশে এরকম পথশিশু অনেক আছে।
কবিতা
সৌভিক দাস
সাউথ গড়িয়া, বারুইপুর
এমন যদি হতো, আমি পাখির মতোন
এমন যদি হতো, আমি পাখির মতোন,
নীল আকাশে ভাসতাম, মেঘের স্বপ্নে গাথা মন।
দিগন্ত পেরিয়ে উড়ে যেতাম দূরে,
যেখানে দুঃখ নেই, নেই কোনো সুরে।
ডানা মেলে ঘুরতাম প্রান্তরের তীরে,
সাগরের গর্জন শুনতাম সুখের নীরে।
কেউ না থামাতো, কেউ না ডাকতো ফিরে,
স্বাধীনতায় ভাসতাম দিগন্তের সীমানা চিরে।
পাহাড়ের চূড়ায়, সবুজ বনানীতে,
ঘুড়তাম একা, মিশে যেতাম প্রকৃতির প্রাণীতে।
কোনো অভিমান, কোনো বাঁধন না থাকতো,
মুক্তির ডানায় আমি আকাশ ছুঁতে পারতাম।
কিন্তু আমি তো মানুষ, পাখি নই হায়,
দুঃখের বাঁধনে হৃদয় জড়ায়।
তবু স্বপ্ন দেখি, যদি একদিন পাই,
পাখির মতোন স্বাধীনতা, আকাশ হবে আমার ঠিকানাই।

অনর্থক শব্দে বধির বাঁশি
তিন পয়সার উৎসব
সরে গেছে
পিছলে যাওয়ার দিনের ক্ষত
বনিবনা নেই অক্ষত পরিচয়ের
দারিদ্র্যের সাথে
দুরন্ত ভুবনে মহিমাময় সাম্যভাব...!
এক প্রস্থ দখিনা বাতাস ছিল
যখন মগজ বারুদ ঠাসা আর
নদী-নালা-স্থলপথে...
শৌখিন তেমন কিছু নয়
একটা একতারার মতো
সাদা ভাত আর একটু তরকারি...
আর ভবিতব্য কে বলতে পারে?
উৎসব তিন পয়সার
আর সরে গেছে যাবতীয় ঝড়ের সূত্র
দেখার কোন বনিবনা নেই
সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ে ।
কবিতা
পার্থ সরকার
অদ্ভত নির্জীবতা বন্ধুমহলে
অদ্ভুত নির্জীবতা
উথলে ওঠে
বন্ধুমহলে
সদলবলে হাজির
খৈনী মুখে দুর্গন্ধ
অকাতরে উড়ে যায় পোশাক
ক্লান্ত স্নায়ু
সাদা স্রাব
নির্বাচনী প্রচারে ফিনাইল
মেতে ওঠে হাড়ভাঙা স্লোগান
ভাইয়ের ঘাড়ে ভাইয়ের নখ
তামাশা দেখে দুর্গন্ধ
অদ্ভত ভ্রাতৃত্ব বন্ধুমহলে
দলে দলে তুলে নেয় ক্ষুধা পাষণ্ড
কোন পথে
ঘাড়ভাঙা সহমরণ
বলতে পারে না
ভণ্ড তপস্বী।
কলকাতা এবং বিদঘুটে বাঙালী সমাজ
১
লাল বমি পরিষ্কার অ্যাশ ট্রে রাস্তা সূচ রক্তের নমস্কার
সামান্য অনুবাদ পায়ের গোড়ালি থেকে নন্দনের সদর দরজায়
কিন্তু অতদূর যাবে না বাড়ির ছিটকিনি আমার কিন্তু আপত্তি নেই
ঝড়ে গোলাপি আনন্দ ছড়িয়ে দিতে।
২
বস্তাপচা খুলি বস্তাপচা আবোলতাবোল
আস্তিন গুটিয়ে প্রগলভ
ফিরছে আবহাওয়া? চোখের কোণে মেঘ জন্মেছে?
আমি কিন্ত স্পষ্ট জানি আমার চোখে ছানি পড়েছে আর
আমার নাকে রুমাল চাপা
তবু দূরে পাহাড়তলির কাছে লাল হলুদ পাগল পাগলি
ছন্দে নাচে সরল গোড়ালি আমার সেখানে আমার গেরস্থালি
প্রকাশ্যে চলে আসে ধবধবে কাশ ফুল সোনালি মৌমাছি
বধ্যভূমিতে এবারো মৃত্যু হোক বিচারকের।
কবিতা
রাহুল রাজ
ঢাকা, বাংলাদেশ
কিছুই হবে না পৃথিবীর
তোমার আমার মিলন না হলে কিছুই হবে না পৃথিবীর
দুঃখগুলো পুশে রেখে বুকে, দোষ দেব সব নিয়তির।
বুকের ভেতর স্মৃতিগুলো সব যত্নে রাখবো জমা
কিছুই হবে না এই সমাজের, যদি না করি ক্ষমা।
হাজার প্রেম রোজ ভেঙে, চাপা পড়ে ইতিহাসে
কত যুগলের মন ভারি হয় হতাশার নিঃশ্বাসে।
তোমার আমার মায়ার টান আবেগের সুতোয় বাঁধা
আমাদের প্রেম আমরা বুঝি, পৃথিবীর কাছে ধাঁধা।
প্রেম নদীর উল্টো স্রোতে দু’জনের দুই তীর-
তোমার আমার মিলন না হলে কিছুই হবে না পৃথিবীর।

কবিতা
সঞ্জীব হালদার
শ্রীনগর, পূর্বপাড়া, পঞ্চসায়ের, কলকাতা
জন্মস্থান:কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত। ১৯৯২ সালে প্রথম কবিতা “বসন্তের দুপুর” প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে।
বসন্ত ও হংসদল
চল্লিশটি বসন্ত চলে গেছে দ্রুত জীবনে
আসে না ফিরে আগের কুড়িটি আর।
দেখি সরোবর মাঝে হংস একদল
যৌবন দীপ্ত তাদের ডানা ঝলমল,
ডানা ঝাপটিয়ে চলেছে ওরা সারিবদ্ধ
আলোড়িত জলে সময়কে করেছে স্তব্ধ,
বিগত যৌবনকে দিতে ফাঁকি
ওদের পথচলা এখনও বহু বাকি,
কুড়িটি বসন্ত আগে দিন ছিল রঙিন
এখন খুঁজি হংসদলের মাঝে বার্তা নবীন।

কবিতা
মো. সাইদুর রহমান সাঈদ
পটুয়াখালী, বাংলাদেশ
সুস্মিতা
পদ্ম-চরণ রেখে মোর ধুলোমাখা মলিন ভুবনে
জাগালো যে রঙিন ঊষা! গুল নাচে যেন পবনে ।
তারারা অলক হতে এসে পরে যাহার কেশ'পর,
মৃদু মৃদু কাপে যেন মধুমাখা অধর।।
কে সে লো প্রণোদিনী, কে সে বিদেশিনী কে?
যাহার মধুর কণ্ঠরাগে
যেন গাহে কোকিল ঐ সে গুলবাগে !
রিনিঝিনি রিনিঝিনি পদছন্দ তার
হৃদয়ে বাদল নামায় ভেঙে ব্যথার আধার।।
বুলবুলি তুই জানিস কি তা?
কে সে এই নন্দিতা?
তবে শোন দিয়ে মন _

যার সনে নির্জনে গভীর আলাপনে কেঁটে যায় বিভাবরী!
যার প্রেমের মধুর শারাব পিয়ে পিয়ে......ভ্রমর হয়ে ঘুরি ইশ্ক কা গুলশানে,
যার গুলবদন-দর্শন আনে আবীর আমার গুঁলিস্তানে!
আমার সব বিষণ্ণতা ,সব মালিন্য,সব অনুরাগ ধুয়ে মুছে দেয় যার পুষ্পহাসিটা,
সে যে আমার গহীনপ্রেম ,আমারই সুস্মিতা!!
এ প্রণয় পরিণয়ে পূর্ণতা পাক,
তুমি এসো হয়ে মোর পরিণীতা, আমার সুস্মিতা!!

আজ সেই বারান্দায়—হোয়াটস্ অ্যাপের প্রোফাইল পিক্চারের ভীড়।
কিংবা রবিঠাকুরকে সাথে নিয়ে সেলফি।
আছে এফ.এম.র বাণিজ্যিক পদচারণা
কিছু লোক তো বলে গেছেন—তিনিই বাঙালীর মেরা ইণ্ডাস্ট্রি।
সেই পরিধি বাড়ছে, তোমার ১৫৬ বছরেও।
ছবির ফ্রেম-এ রবিঠাকুরকে বন্দী করে,
গীতবিতান কিংবা গীতাঞ্জলীর সস্তা (সুলভ) সংস্করণে।
কিংবা ২৫শে বৈশাখের কবিতা পোস্টারে।
তুমি এসেছিলে—তাই তোমাকে নিয়ে বেশ আছি
ভালো থাকতাম, চারিদিক সুন্দর রাখতাম—
যদি তোমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করতাম।
হে রবিঠাকুর—তুমি আছ ভীষণভাবে—
তাইতো চাক্ষুষ করতে জোড়াসাঁকো যাওয়া।
জোড়াসাঁকো থেকে ফিরে
বহুদিনের সাধ পূর্ণ করে কবির আবাসে রবির জন্মদিনে।
সেই ঘর, আরাম কেদারা কিংবা দখিনের বারান্দা—সবই আছে।
আছে ছেলেবেলার রবি।
আছে বাল্মীকি প্রতিভার রবীন্দ্র কিংবা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জোব্বা পরা পদধ্বনি।
ওই মহীরুহের ছায়ায় নিতান্ত অপরিসর মনে হয় এই অট্টালিকাকে। বরং—
বোলপুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর অনেক বেশী মানানসই, জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন।
কবির প্রাণের আরাম।
জোড়াসাঁকোর সিঁড়ির বাঁকে বহু আনাগোনা—
অনুচ্চারিত স্বর—জ্যোতিদাদা কোথায় চললে?
গরমের সন্ধ্যায় যেখানে বাতাস সেবন,
কিংবা শীতে মিঠে রোদ পোহানো;
কবিতা
রথীন্দ্রনাথ বড়াল
ডঃ নগেন ঘোষ লেন, কলকাতা
আজব স্কুল
শিকারপুরে বাবলাতলায়, রোজ সকালে অবাক খেলা-
অঙ্ক করায় মেঠো ইঁদুর, জুটিয়ে নিয়ে হাজার চ্যালা।
চ্যালারা সব বদের ধাড়ি, অঙ্কে তো মন নেইকো মোটে
ইঁদুর যখন নামতা পড়ায়, তারা সবাই গাছে ওঠে।
সেই স্কুলেতে নিয়ম এমন, পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ দিলে-
একটা শামুক আঁকতে যে হয়, রংবেরঙের পেন্সিলে।
আবার যখন যোগ করবে, সাতের সাথে নয় বা বারো,
শিংওয়ালা বাঘ আঁকতে হবে, ডোরাকাটা গায়ে তারও।
ইঁদুরমশাই ভারী কড়া, নেইকো ছুটি দুটোর আগে
অঙ্ক যদি শেষ হল বা, খুলবে তখন প্রথম ভাগে।
“এই যে ভোঁদড়, মনটা কোথায়? মুখস্থ কি হয়েছে তোদের?
সকাল থেকে বলছি আমি, লম্বা হল ছায়া রোদের।“
মূষিক স্যারের ক্লাসটা শেষে, গান শেখাবে ঝিঁঝিঁরানী,
লম্বা দাঁড়ায় ছড় দিয়ে সে, সুর তুলেছে সা থেকে নি।
সঙ্গত দেয় গানের সাথে, টিকটিকি আর ব্যাঙের পোলা
কুকুর, বেড়াল, হাঁস, মুরগি, সেই সুরেতে মেলায় গলা।
গাছের ডালে ঠোঁটটি ঠুকে, তাল মেলাবে কাকের ছানা
লম্বা ঠ্যাঙের বকগুলো সব, গানের তালে নাড়ায় ডানা।
বিকেলবেলা শেষের ক্লাসে, ব্যায়াম শেখায় গোসাপ বুড়ো
হাতের ওপর ভরটি দিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে, নাড়িয়ে মুড়ো।
গাছের গোড়ায় ছোট্ট কোটর, সেখান দিয়ে বাড়িয়ে গলা
দাঁড়াশ সাপও শিখছে দেখো, কুস্তি করার নানান কলা।
কিন্তু স্কুলের শেষের প্রহর, যেই না এল, অমনি সব
লাফিয়ে পালায়, আসর ভাঙে, ছুটির পরেই কলরব।
সাপটা এবার ইঁদুর ধরে, বকটা খোঁজে ঝিঁঝিঁর ঝাঁক
কুকুরগুলো বিড়াল দেখেই সমস্বরে দিচ্ছে ডাক।।
কবিতা
ডাঃ রুদ্রজিৎ পাল
কসবা, কলকাতা
একটি আধুনিক রবীন্দ্র-কবিতা
মায়াবন বিহারিণী হরিণী
টেক্সটবুকে কখনও তো পড়িনি
তাহলে কি সব কিছু মিথ্যে?
আছে সে তো রবি-কবি-চিত্তে।
কেন তারে ধরিবারে করি পণ?
কাজ কিছু নেই বুঝি আর এখন!
ফোনে ভালো লাগছে না? আনমনা?
সাবকনশাসে তাই কল্পনা।
পরশ করিব ওর প্রাণমন-
সাথে আছে গিটার আর ট্রমবোন-
বাঁশরীর সুর খুব ক্ষীণ হায়-
পশিবে না হরিণীর কলিজায়।
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে-
কানে নয়, পকেটের স্মার্টফোনে!
চিত্ত আকুল হলে ইমোজি
কিংবা ফেসবুকে মেসেজ-ই।
গোপনে বিরহডোর আর নেই
যাহা কিছু বলা হবে সামনেই।
সাবকনশাসে থাকে হরিণী
অকারণে তাকে আমি ধরিনি।
“গহনস্বপন” যদি ভেঙ্গে যায়
মুখ রাখি আইফোন পর্দায়।
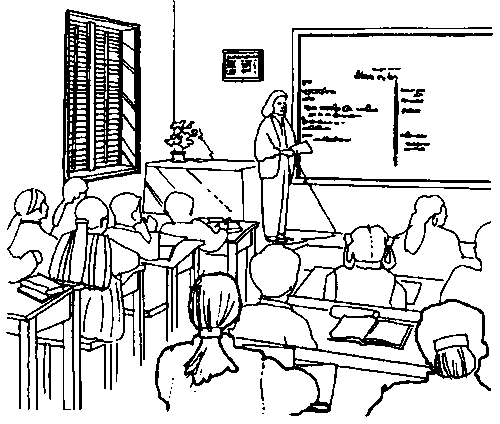


কবিতা
এহিয়া আহমেদ
বরথল কছারী গাঁও, মৈরাবারী, মরিগাঁও, অসম
শ্রমে যে জাতি দীপ্ত
নিভে যাওয়া দীপের শিখা,
তবু ছাই থেকে জ্বলি বারবার,
রক্তে লেখা ইতিহাস আমাদের,
পতন হবে শোষকের অহংকার।
শৃঙ্খলে বাঁধা স্বপ্নগুলো
কেঁদেছে আঁধার রজনী জুড়ে,
তবু সূর্যের রক্তিম আলো
আমাদের ডাকে জাগরণ উড়ে।
ঝঞ্ঝার মতো নির্যাতনের ছায়া,
আমরা দৃঢ় হয়েছি,
অশ্রুজলে গড়েছি পথ,
জয়ের বিহান হৃদয়ে তুলেছি।
শ্রমে যে জাতি দীপ্ত,
তার কি সহজে পতন হবে?
শেকল ভেঙে উদিত হবে,
দূর দিগন্তর সৌরভ ছড়াবে!
আমরা সাহসী, আমরা অটল,
আমরা আশার দীপশিখা,
অবিচল চিত্তে এগিয়ে যাব,
জাগ্রত করে নতুন দিগন্তিকা!
ঐন্দ্রজালিক
নির্জনতা পেরিয়ে ছাপোষা অন্ধকারে
যেখানে মাচার তলে লুকায় কোনো অবয়ব
তারই হাত ধরে দূরে বহুদূরে চম্পক নগরীর
আলো ফুটে বের হওয়া সদ্যজাত রঙিন আলো
সেখানে গিয়ে হাত বাড়ালেই কি হবে দৃশ্যমান?
না কি গভীর সমুদ্রে যেখানের অতল চাপ বাড়ে
ওজনস্তর ভেদ করে কোন আসমানে উঠিলে
মাটি ভেদ করে এশিয়া থেকে ল্যাটিনে
উত্তম-সুচিত্রার ছবির আর্কাইভের তলায়—
চোখ মেলিলেই কি দেখা যাবে সেই রূপ?
কুহকিনী তুমি— তোমার চুলের রাতে
নরম হয়ে আসে এঁটেল, প্যাটেল কত চৌধুরী!
রাজা আসে রাজা যায়— হানা দেয় সামন্তবাদীরা
ভেঙেচুরে মিশিয়ে দেয় সম্ভ্রমের আস্তানায়—
কবিতা
এস এম রায়হান চৌধুরী
গাজীপুর, বাংলাদেশ
কুয়াশা তুমি— সন্ধ্যে হলেই জাপটে বসো আরও
নিঃশ্বাসে আটকে যায় দূষিত-সুষিত যত হাওয়া
নদীর ধারে এলে তোমায় তোমাকে লাগে
তোমাকে লাগে আরও ঐন্দ্রজালিক—
মসলিনের মত ঢুকে যাও দেশলাইয়ের খোলে!
সবই কি প্রবল আকস্মিকতার ঘোরে?
মনোহর তুমি— তুমি হলে চম্পাবতী, খনি বেগম
পরতে পরতে কলমের দাগ হয়ে যায় মায়া
দিগ্বিদিক, ঈশানকোণ কিংবা নৈঋতের যাতায়
ছুটে আসে কত রেসের ঘোড়া— জং বাহাদুর!
হে বুনো মেঘ— শীতল হয়ে যাও আরও
নেমে এসো এই উঠোন বুকের নামায়—
যেখানে আলো, আলো, বিজলির আলোয়
আগুন ধরে যাক কাশ্মীরি আলোয়ানে!

দেহান্তর
বহুদিন হল আসে না কবিতারা,
আজও তাদের যায়নি পাওয়া সাড়া সহস্রবার ডেকে।
ফোটেনা আজ গোলাপ ফুল,
যার সুবাসের স্নিগ্ধ জোয়ার মিশত বালুচরে।
আসে না ঐ বসন্তের কোকিল পাখি,
যার ডাকে ভাঙত ঘুম উত্তুরে হাওয়ার শেষে।
ক্লান্ত পথিক, জীর্ণ পোশাক, শীর্ণ দেহান্তর,
পরাভূত তার বিজয় কেতন, বিষণ্ণ চরাচরে।
শহর তাকে দিচ্ছে ডাক, বলছে ওঠ,
কুয়াশার চাদর সরিয়ে ফেলে।
তবুও পথিকের ভাঙেনা ঘুম,
স্বপ্ন দেখে কোকিলের, নির্বাক পরিহাসে।
স্বপ্ন তাকে নিয়ে যায় সেথায়,
যেথায় পুরানো বটের নীচে কোকিলের ডিম পাওয়া যায়।
কোকিলের ক্যান্সার দম্ভ গলায়,
নিশ্চুপ কুহু ডাক দেয় শুধু সায়।
কলমের ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরে,
ঢেকে যায় তার কবিতারা স্বপ্নের তরে।
কাল থেকে কবিতারা অচেনা হবে,
পথিকের লাশে তখন পিপীলিকা রবে।
কবিতা
স্বরূপ ঘোষ
পিএইচডি ছাত্র, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা

জীবনের এই সাতটি দিন
জীবনের এই সাতটি দিনে
ভেসে বেড়ায় দুঃখগুলো।
ভেঙে পড়ে কাতর ভাবে
যন্ত্রণায়, শরীরগুলো।
মরনের পর আর কি?
থাকবো তো ভালোই সুখে,
এইভাবে দিন চলে যায়
ভাঙ্গা গড়া খেলার সাথে।
মন বলে যা চলে যা,
বেচে থেকে হবেই কী আর?
পালার এক পুতুল হয়ে, নাচ!

কবিতা
আর করবি কী কাজ?
প্রকৃতির এইত নিয়ম
যাতে নেই একটি ছুটি,
দোষ, গুন সব মিলিয়ে
দ্বন্দ্বে কাতর থাকি।
জীবনী তো এই সাত দিন
কাটবে যন্ত্রনাতে,
তারপর মুক্তি পাবে
পালার এই পুতুল হতে।
মিটে যাবে ধার দেনা সব
ছুটি পাবে শরীর হতে
জীবনের এই সাত দিন-ই
কেটেছিল দ্বন্দ্ব করে।
বিকেলের প্রেম
চোখের উপর চোখ রেখে
জানতে চাইলে
'কখন মনের কথা বলবে-
সকাল, দুপুর, বিকেল ---?'
তোমার চোখের গভীরে হারিয়ে যেতে যেতে
বললাম 'বিকেলে।'
সকালে ঘুম থেকে উঠে
অনেক ব্যস্ততা, তাড়াহুড়ো;
সোনালী রোদে স্বপ্নের ঝিকিমিকি,
পাখিরা ডানা মেলে আকাশে
অচিনপুরের ট্রেন ধরবে বলে।
সময় কোথায় কথা বলার
একান্তে দুজনে বসে।
দুপুরে মাথার উপর সূর্য,
গনগনে আগুনের তেজ
জ্বালা ধরায়;
ঘাম ঝরা শরীরে
বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধ।
দেহ শীতল করতে করতে
কথারা ঘুমিয়ে পড়ে।
তারপর ধীরে ধীরে
আলোর চমক কমে আসে,
ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে
পশ্চিমের বিছানায় আলগোছে হেলান দেয় সূর্য।
দীর্ঘ পথ পরিক্রম করার অনাবিল আনন্দে
রঙের সুরভি ছড়িয়ে
আলো ফুল হয়ে ফোটে,
পশ্চিম দিগন্তের বাগিচায়;
রাখাল মাঠ ছাড়েনি গরু নিয়ে,
পাখিরা ফিরে আসেনি নীড়ে,
ভাটার টান লাগেনি নদীর জলে;
তখন স্মৃতির রোমন্থন, অমৃত চয়ন
রূপকথার গল্পে।
তোমার হাতে হাত রেখে
সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো বাগানে
বসব মুখোমুখি,
বুকে আগুন জ্বালাবেনা
তোমার সান্নিধ্য;
সিন্দবাদ নাবিকের, তেপান্তরের মাঠের গল্প,
তোমার চোখে খুশির ঝিলিক,
আমার মন ময়ুর,
হাওয়া মন্দ মধুর মন্থর।
কবিতা
মারুতি
গায়ে অনাদি অন্ধকারের সোঁদা গন্ধ,
চোখে বিশ্ময়ের-ঘুমের ঘোর,
দুহাতের পালকিতে হাওয়ার দোলনায় সে।
কাজল মেঘ থেকে ঝরে পড়া
স্নেহের সোহাগ মাখা দুফোঁটা আশীর্বাদী জল
কি ঘুম ভাঙালো তার!
এ কোন নূতন পৃথিবী দেখছে সে -
দিগন্ত রেখায় ঘন কালো মেঘ,
সোনালী আকাশে জ্বল জ্বল করছে
টকটকে লাল নবীন অস্থির সূর্য।
ওটা কি ফল!
ওটা কি খেলনা!
পিচ্ছিল চঞ্চল নবজাতকের শরীর
লাল সূর্য ধরতে গিয়ে
দুহাতের পালকি থেকে ফসকে আঁতুড় ঘরের মাটিতে।
সে ব্যথা বুঝি মুখে লাগেনি
জেগে ছিল বুকের ভিতরে।
তাই বুঝি সে আর দেখল না
সূর্য ওঠা নদীর কপালে;
বর্ষায় দুকূল ভাঙা কলকল ডাকে
সাড়া দিয়ে ঝাঁপ দিল না মায়ার আবর্তে।
কত সূর্য উঠল,
কত সূর্য ডুবল,
নদীর বুক বেয়ে সে কোনোদিন
দাঁড় টানল না মোহনার পানে।
বুকের ব্যথা ফুটেছে নীল পদ্ম হয়ে
কালের গন্ডি পেরিয়ে তার সুরভি
স্নেহ চুম্বন আঁকে সুরক্ষা বলয় হয়ে।
তুমি আসবে বলে
মন বলছে আজ সন্ধ্যায়
তুমি আসবে।
মনের সরোবরে স্তব্ধ জলে
আকাঙ্খা্র দুষ্টু বালক বারবার
ঢিল ছুঁড়ে আলোড়ন তুলছে,
তার থেকে প্রতিফলিত আলো
ধ্রুপদী তালে আমার চোখে মুখে
রক্তিম প্রলেপ এঁকে দিয়ে যাচ্ছে।
অগছালো জিনিসপত্র সাজিয়ে
রাখতে গিয়েও থেমে গেলাম,
মনের হিসেবি ঝুঁকি
তোমার চোখে হয়তো প্রতিভাত হবে
আমার বিবশ দিনমান এমনি
কেটে যায় তোমার ভাবনায়
কাজের কাজ আর হয়ে ওঠে না।
বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম,
সন্ধ্যার কালো জাদু
পৃথিবীর শরীর ছুঁয়ে দিক্ষিত করছে
খিদের আগুনে দলিত হতে।
উতলা হাওয়া মেঘের কালো চুলে
এলোমেলো বিচুলি কাটছে,
আধফালি চাঁদের কপালে
টিপ হয়ে ফুটেছে সন্ধ্যাতারা।
আকাঙ্খার দুষ্টু বালক
আমার শরীর ভেদ করে
আকাশের বুক চিরে
লম্বা দুহাত বাড়িয়েছে
ভগবানকে আলিঙ্গন গোপন অঙ্গীকারে।
খোয়াব
আকাশে তারা -
বাউল ধরেছে গান, নদীর ধারায়,
কলকল জল স্রোত টলটলে ভরা নদী -
মাঝি জেনেছে নদীজীবন, জেনেছে মৎস্যজীবি,
আমি বুঝেছি হরপল্ কেবল গান -
মৎস্যকন্যার আগমনে শুনেছি : “ওকে ধরে আন্!”
কবিতা
ওভারব্রিজ
এক নেশাগ্রস্ত যুবকের চোখে তার নেশায় পড়ল
ভাটা, সে চাইছে আরও নেশাদ্রব্য।
এক প্রেমিকের বিমর্ষ পথচলা, ভাঙনের আভাসে
সে চাইছে নতুন কোনও প্রেমিকা।
ফুটপাতে বসা এক ক্ষুদার্ত পাগলের ক্ষিদে গড়ায়
তার বের করা জিভে।
ওভারব্রিজে রাত হলে লাইটপোস্টের আলো জ্বলে
নিভে, ওরা সবাই তখন ভাবছে
ঈশ্বর ওদের দেখছেন -
আসলে দেখছে ওদের পেট্রোলিং জিপের অফিসার।
রং
লাল রং ছড়ানো গোধূলিতে,
দেখছি আকাশে ধোঁয়া ইঁটভাটার কিনারে।
ইঁটভাটা তো নয়,
এই ধোঁয়ার উৎস অন্য কোথাও।
আমি ভেবেছি রংমশাল জ্বালিয়ে
মিছিল বেরিয়েছে।
ভুল তো হয়, কেউ হয়তো পুড়ছে,
হয়তো লাল রং ছড়িয়ে পড়ছে কোনও প্রদেশে।
ধোঁয়া উঠেছে আজ এই আকাশে,
কাল উঠবে ছাই।
আমার আছে
আমার আছে মুক্ত আকাশ, দূর দিগন্ত -
আকাশ ভরা নীল,
আমার আছে স্বপ্ন-সবুজ মাঠের ছন্দ,
শাপলা ফোটা বিল।
আমার আছে স্বপ্ন অশেষ সম্ভাবনা,
বই-খাতা, ইস্কুল,
আমার আছে বাংলা ভাষার গর্ব গাঁথা -
রবীন্দ্র- নজরুল।
আমার আছে স্বদেশ -মাটি, মায়ের আঁচল,
বৈশাখী -রেল, কুটুম বাড়ি,
আমার আছে বাবার আদর, মাটির পুতুল-
মেলায় কেনা মিষ্টি হাঁড়ি।
কবিতা
রওশন মতিন
বিরামপুর, দিনাজপুর, বাংলাদেশ
আর জন্মে সুখের আশায়
চৈত্রের সকালে কোনো শীতের বাতাস
সুখের জানালায় তোলে নিরানন্দ সুর,
বাগানের ফুলগুলো ঝরে যায় অশান্ত আবেগে -
ক্লান্ত শিশিরে জ্বলে চিতার চমক।
অরন্য মাংসাশী বৃক্ষের মত অদ্ভুত ক্ষুধাতু্র,
সন্ত্রস্ত লোকালয়ে আকাল-উপবাস-
শোকের মাতম, কাফেলা -কাফন,
সিডর-সুনামিতে ধুয়ে -মুছে যায়
স্বপ্নের নেশা যত্নের আবাদ।
তবু বিদ্ধস্ত বসতভিটা আঁকড়ে থাকি জোঁকের মতো,
অনাহারী হাড় দিয়ে বুনি সবুজ সকাল,
আর জন্মে এ বসতভিটে হয় যেন সুখের বাগান।

যদি পাই সেই অনশ্বর চেতনার স্পর্শ,
জিজ্ঞাসিব তাঁরে -
কে বুনেছে বিভেদ অসত্যের গভীর খাদে?
কে প্রশ্রয় দেয় শোষণের উদ্ধত আস্ফালনে?
আজও প্রতারণার মুখোশধারী নেতা ঘোরে,
স্তুতিমুখর অন্ধত্বের দ্বারে লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা;
অযুক্তির অলৌকিক ধোঁয়ায় অপরাধী বাঁচে,
মানবতার বেদীতে চলে স্বার্থের নির্লজ্জ বলিদান।
স্পর্শে না তাঁরে ভেট,
মোহের বাঁধনে তিনি আবদ্ধ নন-
দৃষ্টিতে তাঁর ন্যায়ের অনন্ত প্রখরতা বিদ্যমান।
আমি খুঁজি সেই কর্মমুখর পথ-
যেখানে সততা ছিন্ন করে কুসংস্কারের বন্ধন,
প্রজ্বলিত হয় যুক্তির অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ।
সংগ্রহ করিব সেই জ্ঞানালোকের কণিকা
নিরলস কর্মীর প্রজ্ঞা হতে-
বিলাবো নিঃস্বার্থে সেই সত্যের অমৃতধারা,
গড়িব নব সমাজ মানবতাবাদের দৃঢ় বুনিয়াদে।
কবিতা
ডক্টর সুব্রত ভট্টাচার্য্য
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া
দিব্যধামের দিগন্ত
কে দেখাবে সেই অভ্রভেদী পথ -
যেখানে কর্মের জ্যোতিতে সত্যের অধিষ্ঠান,
নিঃশব্দ অনুসন্ধানে অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্থান?
ধর্মের সংকীর্ণ গলি নয়, শাস্ত্রের জটিল বাঁধন নয় -
হৃদয়ের মুক্ত প্রান্তরে বাজে সত্যান্বেষণের আহ্বান।
সহস্রাব্দের ধুলিমলিন পথে প্রশ্ন আজ দীপ্ত শিখা -
ধর্ম কি জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, নাকি কুসংস্কারের কুটিল জাল?
কার জানা সেই ধ্রুব পথের দিশা-
নক্ষত্রখচিত সুদূর নীহারিকায়?
কর্মীর বিনিদ্র চোখে প্রখর জিজ্ঞাসা-
অন্ধবিশ্বাসের ঘূর্ণিতে ভাসে শুধু ব্যর্থতার হাহাকার।
লক্ষ নীরব শ্রমিকের ঘাম ঝরে,
মানবতার তপ্ত নিঃশ্বাসে গলে স্বার্থপরতার হিমশৈল।
প্রযুক্তির ডানায় কি মিলবে মুক্তির আলোকচ্ছটা ?
ঘুচুক সকল আরোপিত বিশ্বাস-
আত্মার প্রজ্ঞা জাগুক কর্মের নিবিড় আলিঙ্গনে,
সরাসরি সেই সত্যের মুক্ত প্রাঙ্গণে।
ধর্মের নামে চলে ক্ষমতার আস্ফালন,
ভেকধারীর উপদেশে জন্মে দাসত্বের শৃঙ্খল।
স্বঘোষিত ত্রাণকর্তাদের বাগাড়ম্বরে
বিলীন হয় স্বাধীন চিন্তার স্পর্ধা,
আত্মসমর্পণে নিঃস্ব হয় বিবেকী মানুষ।
দুই হাজার কুড়ির দুর্যোগ উন্মোচন করলো ভণ্ডদের স্বরূপ-
বদ্ধ উপাসনালয়ের বিপরীতে জেগে রইলো নিঃসঙ্গ মানবতার প্রশ্ন-
কোথায় শুশ্রূষা, কোথায় সহানুভূতির স্পর্শ?
কপটদের ছলনা আজ সুস্পষ্ট,
মানবতার নামে চলে বিশ্বাসভঙ্গের বীভৎস নৃত্য।
জাগুক শুভবুদ্ধির বজ্রকণ্ঠ-
ভাঙুক মিথ্যার প্রাচীর, চূর্ণ হোক অন্ধত্বের অভ্রভেদী স্তম্ভ।
রাজনীতি ক্ষণিকের রঙ্গমঞ্চ,
ধর্মও কালের স্রোতে হয় বিলীন-
অবিচল রয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান,
আলোকিত করে চিরন্তন সত্যের দিগন্ত প্রজ্ঞান।
চাই কর্মে নিবেদিত মানব সমাজ,
নির্মল সত্যে যারা করবে আত্মপ্রতিষ্ঠা দৃঢ়।
সভ্যতা আজ সংকটের কিনারে স্তম্ভিত-
তাই মিনতি, হে বিবেক জাগ্রতকারী-
জাগাও ধ্রুবপদে ন্যায়ের তেজোদীপ্ত মশাল,
করো উদ্ভাসিত মানবমুক্তির জয়োল্লাস।
রক্তাক্ত জুলাই
আমরা ছাএসমাজ তো ভুল কিছু চাই নি
চেয়েছিলাম যৌক্তিক অধিকার,
যৌক্তিক দাবি চাওয়ায়
হয়ে গেলাম রাজাকার।
ছাএসমাজের যৌক্তিক দাবি
কোটা সংস্কার,
মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীকে হত্যা করলো
কে দেখবে মা- বাবার হাহাকার।
এ কোথায় বাস করছি
এ কেমন স্বাধীন দেশ,
স্বাধীন হয়েও কেমন জানি
রয়ে গেল পরাধীনতার রেশ।
জুলাই মাস জুড়ে হলো
কতো নির্যাতন; জুলুম ও কত খুন,
কতো মায়ের বুক খালি হলো উপার্জনক্ষম সন্তান হারালো তাজা প্রাণ।
কবিতা
ইসরাত জাহান নাদিয়া
ঢাকা, বাংলাদেশ
শহীদ আবু সাঈদ
কোটা আন্দোলনে নেমেছিলো আমার ভাইটি,
কিভাবে কেড়ে নিয়ে গেল তাজা প্রাণটি?
শহীদ আবু সাঈদ ভাইটি পড়তেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে,
সন্তানকে হারিয়ে পুরো পরিবার আজ অসহায়।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্রটি,
আজ প্রয়াত এই মেধাবী ভাইটি।
ভাইটির জন্য করার আছে শুধুই এখন দোয়া,
দেশের অগণিত মানুষের আছে ভাইটির জন্য মায়া।

মেডিক্যাল
আমরা তো সেদিনই মারা গিয়েছি,
যেদিন ............মাফিয়া, দালাল, মেডিক্যাল কলেজের মালিক হয়েছে –
আমরা সেদিনই মারা গিয়েছি –
যেদিন জয়েন্ট এন ট্র্যান্স –এর সরকারী তালিকা
ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের চেম্বারে ঢুকে গ্যাছে শাঁসাল মেয়েকে নিয়ে ।
তীব্র মার্সিডিজ নিয়ে।
আমরা সেদিনই মারা গিয়েছি –
যেদিন সরকারী হাসপাতালে সই করে প্রণম্য এমডি, এমএস , এফআরসিএস, এমআরসিপি, এফসিসিপি রা
আমাদের সামনে দিয়ে একে একে
শীততাপনিয়ন্ত্রিত কর্পোরেট হসপিটাল এ ঢুকে গ্যাছে –
আমরা তো সেদিনই মারা গেছি –
যেদিন প্রাইভেট ম্যানেজমেন্ট থেকে আলট্রাসোনোগ্রাফি, এক্স-রে আর অপারেশন, ব্লাড ব্যাঙ্ক আর রক্ত পরীক্ষার রেট চার্ট আর টার্গেট আমাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে-
আমরা সেদিনই মারা গেছি যেদিন
এমসিআই ইন্সপেকশান-এ এমডি পাশ ডাক্তার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছে – “কিছু অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না তো?-
আসলে আমরা সত্যি কথা বলতে কি –
মারা গেছি উনিশশ সাতচল্লিশ সালে -
নিম্ন-মধ্যবিত্ত যে কবিতাগুলো লেখা হয়নি
কবিতা লেখার অক্ষরগুলো আকাশে বোঁবোঁ করে ঘুরছে –রানওয়ে ক্লিয়ার না থাকায় প্লেনগুলো যেমন আকাশে চক্কর মারে – আমার লেখাগুলো ঠিকঠাক ল্যান্ড করতে পারছে না – ঘুরেই চলেছে , ঘুরেই চলেছে – পাক খেয়ে, পাক খেয়ে - । আমি গড়িয়ার ছোট্ট গলির ভাড়া বাড়ি আঁকতে চাইছি কবিতা দিয়ে – কিন্ত আমাদের অতি প্রিয় ব্যবসা - কবিতা আমাদের বসিয়ে দেয় – হয় গড়িয়াহাট ব্রিজের নিচের গাড়িগুলোর সাইডে মুরগীর পালক রান্নার পাশের ভাঙা প্লাস্টিক – এর টুলে – বা লেক গার্ডেনস –এর হলুদ সোফা সেটে এসি আর শ্যাম্পেন হাতে হাল্কা গানের সাথে –কবিতাকে দাঁড় করিয়ে দেয় বেলুন হাতে গাড়ির কাঁচের বাইরে –বা এসি স্করপিও –র বিলাস ভ্রমণের সিটে –কিন্তু আমি নিম্ন মধ্যবিত্তের পোষ্টাপিসের এমআইএস থেকে কবিতাকে বেরতে দেখি ধুঁকতে ধুঁকতে, অকালে নিভে যাওয়া যৌনতাহীন ভাড়াটে কর্পোরেশন – এর জলের সংসারের ভিতর থেকে ,সাদা , খালি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কবিতাকে বেরোতে দেখি , বারো হাজার টাকা স্যালারির একমাত্র রোজগেরে ছেলেটার বাবার ক্যান্সার ধরা পড়ার প্রথম দিন হাসপাতালে নিয়ে যাবার ট্যাক্সি থেকে,
কবিতাকে বেরোতে দেখি , যারা এই বিরিয়ানি অধ্যুষিত বইমেলা চত্বরে ল্যান্ড করতে না পেরে ভোঁ ভোঁ উড়ে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে ..................
কবিতা
ডঃ বিশ্বজিৎ মজুমদার
ঢাকা, বাংলাদেশ
শিক্ষিত গরীবের ডায়েরী
গরীবের ডায়েরী বা এই জাতীয় ........................কারণ যেমন ডাক্তাররা বলেন রোগীদের “আপনারা এসব বুঝবেন না”, তেমনি যারা গরীব, তারা কবিতা লিখবে না, আর বড়লোকরা কবিতা লেখে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে।
লক্ষ কোটি টাকার ভাসা ভাসা কিছু হিসেব আর উলালে নাচা ছাড়া আমাদের আর টম এন্ড জেরি শো –এর –মত –আমাদের কিছু করার নেই –এভাবে কি রাতে হাইওয়েতে অপিসের কাজে এক শহর থেকে আরেক শহরে দুফুট গর্ত গুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এলআইসি পলিসি গুলো দুলে ওঠে –যখন আমাদের হাওড়ার জমির পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা ছেড়ে দিতে হয় – যখন আমাদের মাইনে দাঁড়িপাল্লায় উঠে অন্যদিকে বন - জঙ্গল – পাহাড়ের উপর পে-লোডার এগিয়ে যায়্ ...... আর দেয়াল ওঠে ............ আর দেয়াল ওঠে...... আর দেয়াল ওঠে আমাদের মার্কশিটগুলোর উপর......... দেয়াল ওঠে ............ আর যৌবন ছেড়ে আমাদের মার্কশিটগুলো অকালে ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে যায়............... আর বিক্রি হয়ে যায় আমাদের মেয়েদের যৌবন ............ আর আমাদের সামনে ধর্ষিত হয় আমাদের বইগুলো – আর আমাদের রক্তাক্ত শবের উপর দিয়ে কিছুই – হয়নি – অবহেলায় গান বাজাতে বাজাতে চলে যায় স্করপিও আর স্কোডা আর ডাস্টার আর বি এম ডবলু ..................।
রবীন্দ্র জয়ন্তী -এখন যেমন দেখছি
কবিতায় আর গল্পে বেঁধেছি তান –
সকাল থেকেই ঠাকুরের জয়গান ।
অথচ মেরেছি গলা টিপে ধীরে ধীরে –
বসন্ত গান তবু আসে ফিরে ফিরে –
কবেই ব্রাত্য জর্জের সাথে যুদ্ধ –
বিশ্বভারতী করেছিলো দ্বার রুদ্ধ ।
সে সব কথা কি আমরা ভুলেছি আজ ?
মধ্যমেধার সর্বব্যাপী কাজ –
তবে আজ এটা বলতেই হবে আমায় –
মধ্যমেধারা ব্যবসা করেই কামায় !
এই ঠাকুরের ব্যবসা করেই কাল –
জগাই মাধাই হয়ে গেছে লালে লাল –।
প্রোমোটার থেকে চানাচুরওয়ালা ছোট -
বই বাজারের আসল নকল MOTTO-
কতো জলসার হিসেব চুকায় শেষ –
মধ্যমেধায় অধ্যুষিত যে দেশ -
খোলো খোলো দ্বার ,রাখিওনা ভেসে আসে-
PUBLIC TOILET এর GATE এর পাশে ।
সঙ্গীত তাই শুধুই TRAFFIC JAM এ –
অন্য বাঙালি নিজস্ব বং ঘ্যামে ।
আমার শিক্ষা –সরণির অভিজ্ঞতা
ANDROGEN, ESTROGEN HORMONE BALANCE এর সাথে ওজো র সম্পর্ক বিবেকানন্দ যেখানে একেবারে স্পষ্ট করে গিয়েছেন –সেখানে প্রফেসার-এর চাকরীটা রেডিও জকি মেয়েটা কেন পেলো-এটা নিয়ে আমি প্রশ্ন করব না –যেখানে রামকৃষ্ণ পই পই করে আলাদা আলাদা মানুষের ক্ষমতার কথা বলেছেন –আমি সেটা নিয়েও বলব না – যেখানে আমার বিদেশে যাবার ভিসাটা হিজবিজবিজ কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল আস্ত –ধনেপাতা সহ –আর আমি সেই বেড়ালটার কথাও বলব না যে কিনা আমার সাত বছরের গবেষণার দিনগুলোতে প্রফেসারের টেবিলের নীচে ঘুরে বেড়াতো লেজ ফুলিয়ে –আমি সেইসব চেয়ারম্যানদের সম্বন্ধেও বলব না –যাদের চেম্বারে ঢোকার জানালায় মই লাগানো থাকত –আর আমি নিজস্ব একটা মই যোগাড় করে লাগিয়ে যেদিন রাত্রে ঘুমোতে গেছি –পরদিনই দেখি মইয়ের সব কাঠ আগুন হয়ে জ্বলছে ফার্নেসে –সারা রাত্তির –আমি সেই মই বা রাত্তিরের কথাও বলব না -তবে এই টুকু বলতে পারি –
ওজো প্রাপ্তির সাজ –সরঞ্জামগুলো এখন খুব সহজেই পেয়ে যাই –গোপনে ।অভিজ্ঞতায়
ডঃ পার্থ মুখার্জি
পার্থদার ছেলেটা অঙ্কে তিন পেয়েছিল। পার্থদার তাতে কিছু যায়, আসেনি-কারণ এমবিবিএস, এমএস, এফআরসিএস অক্ষর মালার সারি-তিনটে নার্সিংহোম তিনবার বিড়ি টানতেই দেখলাম সত্তর লাখ প্যাকেজ ........................বেশ জমিয়ে ক্যান্টিনে লুচি –মাংস-আলুর ছক্কা –বিরিয়ানি খেয়ে এমবিবিএস এর ঢেকুর তুলতে লাগলো। এর পরের গল্প পরিপাটি এক কোটির রেডিওলোজী এমডি আর এমসিআই রেকগনাইজড অজানা বনের মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার। এদিকে আমার ছেলেটাকে আমি রোজ চ্যবনপ্রাশ –গাঁদালপাতা –ব্রাহ্মী –রেন এন্ড মারটিন –বাংলা ব্যকরণ –ভূগোল –কেন পড়া জরুরি –স্পোকেন ইংলিশ –এর পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর হেঁচকি –এআইইইই –র পা ধরে টানাটানি –তারপর মিশিমাখা শিখি পাখা সরু সরু গানে গানে –সেমিস্টার আর নম্বরের সুর –তাল –ছন্দ –নিরানন্দ –আনন্দ পেরিয়ে –ইউপিএসসি –সরকারী পরীক্ষা –সা রে গা মা পা ধা নি –ভার্সেস বন দপ্তরের জমি ঘেরা করিতকর্মা কাকা-ভাইপো .........একা অভিমুন্য ...........................এটা কি চ্যালেঞ্জ না ভবিতব্য ?
ছোট গল্প
রূপোর
সরস্বতী
বর্ণালী ঘোষদস্তিদার

গুণমনি কাঁড়ার জোরসে বাইক ছুটিয়ে বাড়ির সামনে এসে তীক্ষ্ণস্বরে একটা হর্ন মেরে দাঁড়ালো। গুণমনির গিন্নি পুঁটুরানি তো অবাক! এইসময় তার পতিদেব সাধারণত ফেরে না! কিন্তু আজ এসেছে। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে পুঁটু ভাবে।
আজ সকালবেলায় শো কেসে অনেক দিনের জমে থাকা পুরোনো আবর্জনা পরিষ্কার করে গেছিল গুণমনি। আধভাঙা রংচটা কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলগুলো মা বেঁচে থাকতে ফেলতে পারতো না। এখন নির্দ্বিধায় সরিয়ে দিয়ে সাফ করে দিল জঞ্জাল। খানিক খালি হলো শো-কেস। নতুন কিছু আসবে বোধহয়। ঠাঁই পাবে শূন্য জায়গায়। কিন্তু বস্তুটি কি সে সম্পর্কে পুঁটির কাছে কিছুই ভাঙেনি গুণমনি।
আজকাল ইশকুলের পঠনপাঠন সেরে হর দিনই গুণমনিকে গভর্নিং বডির কেষ্টবিষ্টু থেকে শুরু করে এলাকার পঞ্চায়েত লিডার এমএলএ দের বাড়ি ধর্না দিতে হয়। এই করেই আলিশান বাংলো বানিয়েছে গুণমনি। দাদা পরশমণি চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত। ছোটভাই রতনমণি কলেজে পড়ছে। মেজো গুণমনিই বৈষয়িক ব্যাপারে খুব চৌকস। ইশকুল মাস্টারি একটা জুটিয়েছে সে। কিন্তু তাতে কতোই বা আয় হয়। তাছাড়া ক্লাস ফোর পাশ nগুণমনির তো চাকরিই হয়েছিল চিরকূট দেখে। সে আজ প্রায় দশবছর হলো।
পুঁটির সঙ্গে রামবাবুদের আমবাগানে এক ভর গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে দাদাদের হাতে বেবাক ধরা পড়ে গেছিল গুণমনি আর পুঁটু। ব্যস পুঁটুর দাদারা এলাকার সব বড়ো বড়ো মাতব্বর…..বললো “আমার বুনের ইজ্জত লুট করেছিস ওকে বিয়ে করতে হবে তোকে। নাহলে দেবো তোকে ফাঁসিয়ে।”
গুণমনির তো ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার যোগাড়।nকাঁচুমাচু মুখ করে দাদাদের পায়ে পড়লো গুণমনি “পুঁটুকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু পুঁটুকে ঘরে তুলবো সে রেস্ত আমার কই?”
বছর দুই আগে বাপ মারা যাবার পরই পুঁটুর দুই দাদা ঘনশ্যাম আর রাধেশ্যাম ভাবছিল বোনটাকে কি করে পার করা যায়। খাবার পেট একটা কমে।
পুঁটুও ইশকুল যেতো রোজ। কৃষ্ণভামিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। দু’একবার ফেল করলেও টেনেটুনে ক্লাস নাইন অবধি উঠেছিল। কন্যাশ্রী পেলো। কিন্তু এখন আর লেখাপড়ায় মন বসে না। ইশকুলের পথেই পরিচয় গুণমনির সঙ্গে। মেয়ে ইশকুলের সামনে অনেক ছেলের ভীড়ে গুণমনিও ঝাড়ি মারতো। ভীড় জমাতো আরও অনেক জোয়ান মদ্দ। কারো বোন পড়ে কারো বা দিদি। গুণমনিরও কেউ হয়তো পড়ে কৃষ্ণভামিনীতে। সেই সুবাদে গুণমনির রোজ ইশকুলে যাতায়াত।
অনেক মেয়ের ভীড়ে পুঁটুরানিকেই খুঁজতো গুণমনির চোখ। ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটিয়ে চোখের ইশারায় কিছু বলতে চাইতো ওর মন। শেষমেশ সত্যিই একদিন পুঁটু মন দিয়ে বসলো গুণমনিকে। আসলে পুঁটুর মনও আশ্রয় চাইছিল। বাবা থাকতে বোনের ওপর দাদাদের হম্বিতম্বি তেমন টিঁকতো না। কিন্তু বাবা গত হবার পর পুঁটির ওপর দাদাদের খবরদারি বড্ড বেড়ে গেল। সব্বসময় চোখে চোখে কড়া নজরদারি। পুঁটু কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে, সব বিষয়ে তাদের কৌতূহল।
দুই দাদাই দিনরাত হাঁকায় “বাবা মরে গেচে বলে ভাবিস না যে তুই খুব স্বাধীন হয়ে গেচিস। যখন-তখন যা খুশি করবি। এখন আমরাই তোর গার্জেন। আমাদের কথার বেচাল হলে না মজা দেখিয়ে ছাড়বো।”
দাদাদের অতিশাসনে হাঁপিয়ে উঠেছিল পুঁটি। দাদারা কি সত্যিই তার গার্জেন? না পুলিশ-দারোগা? মা কেও দেখে পুঁটি দাদাদের দাপটে কেমন সিঁটিয়ে থাকে সদ্যবিধবা মানুষটা। কথায় কথায় মা র ওপর চোটপাট করে। যেন এই বাড়িটাকে এই পরিবারটাকে কিনে রেখেছে দুজন ষন্ডাগন্ডা পুরুষমানুষ।
গুণমনি আড়ালে দিনরাত বলে “তোমাকে পেয়ে আমি ত্রিভুবন ভুলে গেছি পুঁটি। কবে যে তোমাকে আমার ঘরে আমার ইস্তিরি করে নিয়ে গিয়ে তুলবো? তোমাকে কোনো কষ্ট পেতে দেবো না পুঁটুরানি দেখো। তুমি রাজরাজেশ্বরী হয়ে মহা আরামে থাকবে আমার বাড়িতে।”
এসব কথা পুঁটুর কানে গুণমনি বলে বটে কিন্তু তার সে ক্ষমতা কোথায়? পুঁটুরানির জীবনের দায়িত্ব নেবে এমন আর্থিক সামর্থ্য নেই গুণমনির। না আছে স্থায়ী চাকরি না ব্যবসাপাতির আয়।
পুঁটু কিন্তু নড়বার নয়। সম্পূর্ণ মনটাই সে দিয়ে বসেছে গুণমনিকে। বেশ জোর গলাতেই জানিয়ে দিয়েছে দাদাদের, গুণমনি কাঁড়ার ছাড়া কাউকেই সে বিয়ে করবে না। আইবুড়ো হয়ে থাকবে সারাজীবন তবু গুণমনি ছাড়া কারুর গলাতেই মালা দেবে না। তাকে এই স্পষ্ট কথা বলার সাহস জুগিয়েছে গুণমনিই। তার গলায় ব্যক্তিত্বের জোরালো আওয়াজ উঠেছে গুণমনিরই গুণে।
কিন্তু গুণমনি যে পুঁটুকে ঘরের বৌ করে নিয়ে যাবে….তার পায়ের তলার মাটিটাই তো শক্ত নয়। নড়বড়ে। এখান-ওখান পার্টির খিদমত খেটে কিছু পয়সাকড়ি কখনও আসে কখনও কিছুই না। পেটে বিদ্যেও তেমন নেই যে ভদ্রলোকের মতো চাকরি-বাকরি একখানা জোটাবে। ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তবে পার্টিতে বাধ্য অনুগত ছেলে হিসেবে কদর আছে তার। ভোটের সময় মাটি কামড়ে পড়ে থেকে টার্মের পর টার্ম দলকে জেতানো তো আছেই এছাড়াও কতো যে কাজ……..পাড়ায় অশান্তি লাগলে পুলিশ বা সরকারি জনপ্রতিনিধি সেখানে পৌঁছোনোর আগেই চলে গিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করা,হাট-বাজারে সওদাকারিদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে দলের ফান্ডে পৌঁছে দেওয়া, দরকারে - অদরকারে দাদাদের হুকুম তামিল করা, এমন নানা কাজে একদম আয় হয়না তা নয় কিন্তু সেসব খুবই অনিয়মিত অনিশ্চিত। বিয়ে-থা করে সংসার ফেঁদে বসলে তো এরকম করে চলবে না। ফিক্সড ইনকাম কিছু থাকতেই হবে। এছাড়া দলের এটা সেটা করে বাড়তি রোজগার সে তো আছেই।
দলের যে মাতব্বর দাদার ফরমাস খাটে গুণমনি,তাঁর শিক্ষা দপ্তরে খুব জানাশোনা। খোদ মন্ত্রীর সঙ্গে অষ্টপ্রহর ওঠাবসা। তাঁর অনুগ্রহেই সরকারি প্রাইমারি ইশকুলে হঠাৎই একটা চাকরির অফার পেয়ে গেল গুণমনি। মাস্টারের পদে চাকরি। মাস গেলে ভালো বেতন। বিনিময়ে পার্টি ফান্ডে দিতে হবে দশলাখ টাকা।
পুঁটুকে বললো গুণমনি। পুঁটুই পরামর্শ দিল “তোমার ভাগের কিছু জমি বেচে ওই টাকা দিয়ে দিয়ে চাকরিটা নিয়ে নাও। মাস্টারদের এখনও কতো সম্মান সমাজে।”
আসলে বাবা মারা যাবার পর দাদাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ পুঁটু মাঝেমাঝেই ভাবতো, যদি একটা চাকরি-বাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় তো দাদাদের নাকে ঝামা ঘষে দেবে। মা কে সঙ্গে নিয়ে সে আলাদা হয়ে যাবে দাদাদের সংসার থেকে। কিন্তু যতো উঁচু ক্লাসে উঠতে লাগলো পড়াশুনো কঠিন হোল। বন্ধু-বান্ধবরা টিউটরের কাছে পড়ে। সে উপায় পুঁটুর নেই। ওদিকে ততদিনে জৈবিক নিয়মে তার জীবনে এসে পড়েছে গুণমনির আহ্বান। সব মিলিয়ে নিজের জীবনে স্বনির্ভর হবার স্বপ্ন একসময় মিলিয়ে গেল পুঁটুর। সে গুণমনির স্বপ্নেই বিভোর হয়ে গেল।
জমি বেচে লাখদশেক টাকা পার্টি ফান্ডে দিয়ে ইশকুল মাস্টারির চাকরিটা পেয়ে গেল গুণমনি। আর সরকারের ঘর থেকে অন্যান্য টিচারদের মতোই তার নামেও বেতন আসতে লাগলো।
বছর না ঘুরতেই পুঁটুর দাদাদের কাছে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললো গুণমনি
“পুঁটুরানিকে আমি ভালোবাসি। সেও ভালোবাসে আমায়। আমরা বিয়ে করতে চাই।”রাধেশ্যাম ঘনশ্যামও দেখলো এই মওকা। বাপমরা মেয়েটাকে ইশকুল টিচার পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারলে বোনটাকে পার করাও হবে। পাড়াপড়শিও ধন্যধন্য করবে। ঠিক তাইই হলো। শেষমেশ চাকরির জোরেই পুঁটুরানিকে অত্যাচারী দাদাদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে বিয়ে করে ঘরে তুললো গুণমনি। তার মনে হোল পুঁটু বড়ো পয়মন্তি। তার পয়েই এই সরকারি চাকরি। পরিবারে এমনিই গুণমনির কদরটা একটু বেশিই ছিল। আনপড় চাষাভুসো বাড়ির ছেলের সামাজিক পরিচয় এখন ইশকুল মাস্টার। সেই সুবাদে পুঁটুরও কদর খানিক বেড়ে গেল। গুণমনি আর পুঁটু মহানন্দে সংসার করতে লাগলো। বাবা গত হতে বাবার কেনা জমির অংশ প্রমোটারকে দিয়ে বেশ কিছু টাকার মালিকও হলো গুণমনি। বাড়লো ব্যাংক ব্যালান্স। ফিরিতে ফ্ল্যাটও পেলো একখানা। পৈতৃক বাড়িটাকে সংস্কার করে হালফ্যাশনের বাংলোবাড়ি বানালো। একখানা গাড়িও কিনেছে গুণমনি। তবে বেশিরভাগ সময় সে বাইকই চড়ে। ইশকুলে যাতায়াত করে ওই মোটরবাইকটিতেই। পালিশ করা চকচকে শরীরটায় সাফারিসুট - বুট পরে সে যখন বাইক হাঁকিয়ে যায় পুঁটুরানির মনটা ভরে ওঠে। তার মন বলে, কথা রেখেছে গুণমনি। তাকে সত্যিই রাজরানি করে রেখেছে। কিন্তু এর মধ্যে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে স্বামী গুণমনির কান্ডে বেশ লজ্জাই পেল পুঁটু। ক্লাস সিক্সের একজন ছাত্র গুণমনি স্যারকে একটা অঙ্কের প্রসেস জিগ্যেস করেছিল…….গুণমনি তো ক্লাস সিক্স পাশই করেনি, কি করে অঙ্ক নিজে কষবে? ছাত্রকে শেখাবেই বা কেমন করে? শুধু সেই
মুহূর্তে ছাত্রটার পাকামি দেখে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রটাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে অঙ্ক শেখার শখ মিটিয়ে দিয়েছিল গুণমনি। সে খবর টিভিতে দেখেছে সবাই। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়ে গেছে। রাতের বিছানায় গুণমনির লোমশ বুকে হাত রেখে পুঁটু জিগ্যেস করলো “তুমি তো মাস্টারমশাই। ছেলেটা অঙ্ক জিগ্যেস করলো তুমি তাকে মারলে কেন? শিখিয়ে কেন দিলে না?"
গুণমনি অস্বস্তিতে পড়ে জবাব দিল “ওসব বাজে খবর। ভুল খবর। ওসব বিশ্বাস কোরো না।”
“কিন্তু টিভিতে যে দেখালো। মোবাইলেও ফুটলো…ওই তো তোমার বুলু সাদা জামাটা তো দেখাও গেল…..”।
“আরে পুঁটু ও অন্য লোক। আমি কখনও এ কাজ কত্তে পারি?”
পুঁটু চুপ করে রইল। মিডিয়া নাম বলে নি কিন্তু ছবি দেখিয়েছে। একটু আবছা কিন্তু বেশ বোঝা গেছিল যে ওটা গুণমনি। ঘটনা ঘটেছে অঘোরনাথ ইন্সটিট্যুশনে। ওখানেই মাস্টারি করে গুণমনি। পার্টির ক্ষমতাশালী দাদার দৌলতে পাওয়া চাকরি। পুঁটুর খারাপ লেগেছিল খুব। ছেলেটাকে না মেরে অঙ্কটা টুকে নিয়ে বাড়িতে এলে পুঁটুও একটু চেষ্টা করে দেখতে পারতো কষা যায় কি না……কিন্তু পুঁটুর এখন করণীয়ই বা কি? সোমত্ত বোনের ওপর দাদাদের উদয়াস্ত গা জোয়ারির অসময়েই গুণমনি তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলেছিল। সেই স্বামীর সঙ্গে বেইমানি সে করবে কেমন করে? তাছাড়া এরকম একটু-আধটু তো হতেই পারে। ওই ইশকুলে মাস্টারি করেই তো মাস গেলে মোটা টাকা বেতন ঘরে আনে গুণমনি। তাতেই তো সংসারের যাবতীয় শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আগের মতো চাল নেই চুলো নেই বাউন্ডুলে হয়ে থাকলে থাকতো নাকি পুঁটুর এতো সুখ?
“কি? কি আবার ভাবতে শুরু করলে আমার পুঁটুরানি? এখন এসো তো আমার কাছে…….বলেই সবল বাহু দিয়ে গুণমনি চওড়া বুকের ওমে টেনে নেয় পুঁটুরানিকে। আদরে আদরে ভুলিয়ে দেয় সব সংশয় সন্দেহ মনের খটকা।
এভাবেই বেশ চলছিল গুণমনি আর পুঁটুর সুখী দাম্পত্য। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই কি মন ভরে? আর্থিক সাচ্ছল্য এসেছে অনেক। কিন্তু বড়ো পদে থাকতে না পারলে সামাজিক সম্মান তেমন জোটে না। দলের লোকদের পদিয়ে পটিয়ে খানিক কাঠখড় পুড়িয়ে ইশকুলের গভর্নিং বডির সদস্যপদ পেলো গুণমনি। হোমরাচোমরা না হলে কি লোকে মান্যিগন্যি করে? এখন এই পদের জোরেই গুণমনির জুটবে নানা উপহার, উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক। এখান-ওখান বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ। অন্য শিক্ষকরা নিজেদের স্বার্থ মেটাতে পায়ে গিয়ে পড়বে তার। সে রাজনৈতিক নেতাদের মতো ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে বলবে “খুব চেষ্টা করছি। যতো তাড়াতাড়ি পারি আপনার ফাইলটা কমপ্লিট করে দেব।” তারপর ফাইল ফেলে রেখে দেবে মাসের পর মাস। যারা উদয়াস্ত তাকে তেল দেবে, টু-পাইস ঘুস দেবে শুধু তাদেরই ফাইল নেড়েচেড়ে দেখবে গুণমনি।
দেখতে দেখতে দলের যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে বহু উদ্দেশ্যই সাধন হলো গুণমনির। শুধু সমস্যা ইশকুলের হেডমিস্ট্রেস ওই চপলা মুখার্জি? তাঁকে নিয়ে বেজায় ঝামেলায় থাকে গুণমনি। একনম্বর টেটিয়া মহিলা। প্রতিটা কাজ এক্কেবারে নিয়ম মেনে কড়া আইন ফলো করে নিখুঁত করে করবেন উনি। গুণমনি ভাবে এই মহিলাকে একবার হাত করতে পারলে সব সমস্যা মিটে যেতো। কিন্তু মহিলা মেয়ে তো নয় যেন নিরেট শক্ত বাদাম। ভাঙা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, চতুর্দিকের অগোছালো এলোমেলো ঢালাও দুর্নীতি আর অসততার মধ্যে থেকেও উনি কি করে যেন নিজেকে রাজহাঁসের ডানার মতো নিষ্কলঙ্ক রেখেছেন, নিজের হাত এতোটুকুও ময়লা করেননি সেটা খুবই বিস্ময়ের। টাকাকড়ির লোভ, পদের মোহ, এসব প্রলোভন জয় করা কি এতোই সহজ? গুণমনি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে। চপলা দেবীর সততার শক্তির কাছে বারবার গো-হারান হেরে যেতে হয় গুণমনিকে।
একশো বছরের পুরোনো অঘোরনাথ ইনস্টিট্যুশনের নতুন বিল্ডিং হয়েছে। নাম “অঘোরনাথ শতবার্ষিকী ভবন”। অঘোরনাথ সেন ছিলেন এই এলাকার একজন বিদ্যোৎসাহী মানুষ। ধনী ও সমাজহিতৈষী। একশো বছর আগে তাঁরই নির্দেশে বসতবাটিটির একাংশে তৈরি হয় এই ইশকুল। শুরু হয়েছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় দিয়ে। এখন এলাকার অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শতবর্ষের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর এর একটি বিশেষ ভবন তৈরি হয়েছে। স্থানীয় এমএলএ দ্বারোদ্ঘাটন করবেন। এমনিতে সম্বৎসর বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন কাজ নিজেদের দায়িত্বে চালায়। কিন্তু এ বাদেও চপলা দেবী ইশকুলের যে কোনো বড়ো কাজের আগে মিটিং ডাকেন। সবাইকে নিয়ে বসে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেন। এবারও তার অন্যথা হলো না। অতিথি অভ্যাগতদের বরণ করার জন্য কিছু উপহার প্রদান প্রয়োজন। এমনিতে শতবর্ষ নামাঙ্কিত মেমেন্টো, উত্তরীয়, একটি করে চারাগাছ আর মিষ্টান্নর ব্যবস্থা তো করাই হয়েছে। এর সঙ্গে একটি সুন্দর উপহার দিলে মন্দ হয় না। সভায় সবাই একমত হয়। কিন্তু কি সেই উপহার? “কলকাতার এক নামকরা দোকানে পাওয়া যায় রূপোর সরস্বতী। শতবর্ষপ্রাচীন ইশকুলে সমাগত অতিথিবর্গকে এমন একটা মহার্ঘ্য উপহার এই যেমন একটা রূপোর সরস্বতী দিলে কেমন হয়?” গুণমনি প্রস্তাবটি দেয়।
“এর দাম কতো গুণমনিবাবু? কোনো আইডিয়া আছে আপনার?” চপলা দেবী প্রশ্ন করেন।
“দুহাজারের মতো হবে আন্দাজ” গুণমনি জবাব দেয়।
“বাবা তাহলে তো দাম ভালোই। কখানা কিনতে হবে আমাদের? এমএলএ সাহেবের জন্য একটি বাইরের একাডেমিক অতিথি দুজনের জন্য দুটি ,আর একটি এক্সট্রা তিন চারটি কিনলেই তো হবে না কি?” চপলা দেবী বলেন।
“না মানে আমি বলছিলাম মঞ্চে তো পরিচালন সমিতির সদস্যরাও থাকবেন…..একই মঞ্চে থেকে তিনজন পেলেন আর বাকি রা পেলেন না এটা ভালো দেখায় কি?” গুণমনির যুক্তি।
“কিন্তু বাকিরা তো এই স্কুলেরই শিক্ষক গুণমনিবাবু…….তারা নিজেরাই নিজেদের উপহার দেবেন?এটা কেমন কথা?”
সভায় উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষকরা চপলা দেবীর মতেই সায় দেন।
ইতিহাসের শিক্ষক রমা বসু বলেন “আরে আমাদেরই তো স্কুল। আমরা হলাম হোস্ট। আমাদের অতিথি ওঁরা। অতিথিদের উপহার তো আমরা দেবো। আমরা নেবো কেন?”
“আমিও সেটাই ভাবছিলাম। অতিথিদের উপহার দিয়ে বরণ করে নেবো আমরা। সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের উপহার নেওয়ার প্রশ্ন নেই।“ চপলা দেবী বলেন।
সভায় উপস্থিত অন্য সদস্যরা এই প্রস্তাবেই সায় দিলেন। পরিকল্পনা মতো তিন/চারটি রূপোর সরস্বতী কিনে আনা হোল। অতিথিদের জন্য। আসল দিনটি এলো। অতিথিরা এলেন। নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। তাঁদের উপহার দেওয়া হোল একটি রূপোর সরস্বতী, একটি চারাগাছ, একটি মেমেন্টো, একটি শতবার্ষিকী নামাঙ্কিত উত্তরীয়, ও একটি মিষ্টান্নের প্যাকেট।
গভর্নিং বডির সদস্যদের নাম ডেকে মঞ্চে তোলা হোল। সবাই একে একে উঠলেন। উঠলেন বর্ষীয়ান শিক্ষকরাও। কিন্তু গুণমনি কোথায়? সঞ্চালক বারবার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন “পরিচালন সমিতির মাননীয় সদস্য গুণমনি কাঁড়ার…. আপনাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি……” কিন্তু গুণমনি নেই……কোথায় গেল সে?
রূপোর সরস্বতীটা তার নতুন বাড়িতে বেশ মানাতো। বাড়িতেও কতো কদর বাড়তো তার। এসব ভাবতে ভাবতে বিকেলবেলায় সাধারণ সময়ের ঢের আগে মুখ কালো করে একরকম লুকিয়ে বাড়ি ফিরে এলো গুণমণি।
“রূপোর সরস্বতীটার জন্য আজ শো কেসটা সাফ করেছিলাম জানো পুঁটু?”
পুঁটু আর গুণমনির বিয়ের দশবছর কেটে গেছে। পুঁটুর এখন সাহস বেড়ে গেছে অনেক। পুঁটু বললো “ঘরে রূপোর সরস্বতী সাজিয়ে কি তুমি তোমার বিদ্যে ঢেকে রাখতে পারবে? তোমার ঘরে ও জিনিস না মানায় না। ওতে সরস্বতীর অপমান। বরং যার ঘরে মানায় সরস্বতী তাঁর ঘরেই যান”।
গুণমনির কিন্তু মন মানে না। এলাকার এমএল এর হাত থেকে হাসিমাখা মুখে রূপোর সরস্বতী নিচ্ছে সে এমন একটা ছবি শো-কেসে বাঁধিয়ে রাখা গেল না। ফেসবুকেও দেওয়া গেল না। তার মনটা কেমন খচখচ করতে করতে থাকে। সব হলো ওই হেডমিস্ট্রেস চপলা মুখুজ্যের জন্য। আচ্ছা অদ্ভুত মহিলা। অমন লোভনীয় রূপোর সরস্বতী মূর্তিটা…..নিজেও নিলেন না, কাউকে নিতেও দিলেন না? রাগে গজগজ করতে থাকে গুণমনির ভেতরটা।
পাশাপাশি মনটাও “কু” গাইতে থাকে….. বেশ ক’বছর আগে কেমন করে গুণমনি এই মাস্টারির চাকরিটা পেয়েছিল সে রহস্য যদি জেনে যান চপলা? কিম্বা কেমন করে গুণমনি হলো গভর্নিং বডির সদস্য….
হেডমিস্ট্রেস চপলা মুখার্জির চোখের দিকে তাকালেই আজকাল আত্মবিশ্বাসে বড়ো রকম টান পড়ে গুণমনির।
চেনা বটতলা
রথীন্দ্রনাথ বড়াল
ডঃ নগেন ঘোষ লেন, কলকাতা
প্রবন্ধ

‘বটতলার বই’ তথা বটতলার আদি প্রকাশনার সাথে আমার পরিচয় মামাবাড়ির সূত্রধরে। ইতিহাস খুলে দেখলাম উনিশ শতকে বাঙালী মননে শিক্ষা চেতনা আসার সাথে সাথে প্রকাশনার তাগিদ প্রকাশ পায়-সেই সূত্র ধরে বেশ কিছু ছাপাখানা তৈরী হয় মূলতঃ উত্তর কলকাতা বা আদি কলকাতায়। যেমন, গরাণহাটা, আহিরীটোলা, চিৎপুর, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি। বিষয় বৈচিত্র্যে এই ‘বটতলা’ অভাবনীয়। সমাজজীবনের চলন সহজ সরল ভাষায় সেই লেখকরা লিখে গেছেন মনের ভাব অনাবৃত রেখে। বটতলার ইতিহাস কিছু গ্রন্থকার লিখেছেন। বটতলার কিছু বই সংরক্ষণ করে প্রকাশনাও হয়েছে। এই বটতলার দেড়শ-দুশ বছরের ইতিহাস – ৬০-৭০ দশকে এই বই পাড়াকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই প্রাচীন প্রকাশনার কিছু ঝলক পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের উদ্দেশ্য।
বটতলার বিস্তৃত অবস্থানের মধ্যে আমি যে বটতলার কথা লিখতে বসলাম – সেটা কলকাতার আদি চিৎপুর রোডে অবস্থিত। বর্তমানে নাম হয়েছে ‘রবীন্দ্র সরণী’। সার্থক নাম। ঠাকুর পরিবারের জোড়াসাঁকো বাড়ির খুব কাছে আর রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্কুল ‘ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী’র ঠিক বিপরীতে সারি সারি প্রকাশনা সংস্থা, নানা যাত্রা কোম্পানীর সাথে সহাবস্থান করত। যেমন - ‘টাউন কলিকাতা লাইব্রেরী’, ‘সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী’, ‘ডায়মণ্ড লাইব্রেরী’ প্রভৃতি। এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্ভাগে একমাত্র ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর সগৌরব উপস্থিতি দেখতে পাই। বাকীরা বাংলা প্রকাশনার আধুনিক ধারায় তাল রাখতে না পেরে বোধহয় অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে। এবার দেখে নেওয়া যাক—এই প্রকাশকরা কি ধরনের বই প্রকাশ করত বা ছাপত। যাত্রাপাড়ায় অবস্থানের জন্য বোধহয় মূলতঃ যাত্রার বই প্রকাশিত হত এখান থেকে। এছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি প্রকাশ করে সারা বাংলাকে, বিশেষতঃ পুরোহিত শ্রেণীকে সমৃদ্ধ করে এসেছে এই প্রকাশনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—দূর্গাপূজা পদ্ধতি, কালীপূজা পদ্ধতি, সরস্বতীপূজা পদ্ধতি ইত্যাদি। গ্রাম্য সংস্কৃতির মেরুদণ্ড যাত্রাপালা। আজকের টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিডিও, সিনেমা, তারপর আধুনিক ইণ্টারনেটের প্রভাবে যাত্রার সেই ঝনঝনানো বাজনা আজ অনেকটাই স্তিমিত। কিন্তু ৬০, ৭০, ৮০-র দশকে ছিল যাত্রার রমরমা। সেই যাত্রার আতুরঘর এই প্রকাশনাগুলো। আমার মাতামহ বা দাদুর প্রকাশনা সংস্থা ছিল—‘সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী’। বাংলার অন্যতম প্রাচীন প্রকাশনা। পরে এই ‘সুলভ কলিকাতা’—ভাগ হয় ‘টাউন কলিকাতা লাইব্রেরী’ ও ‘সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী’
নামে পাশাপাশি দুই ভায়ের দোকানে। বিখ্যাত যাত্রার পালাকার ছিলেন শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে। ব্রজেন দে’র পালা করার জন্য সব যাত্রা কোম্পানী মুখিয়ে থাকত। সুলভের কর্ণধার শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ধরের ব্রজেনবাবুর সাথে সখ্যতার খাতিরে ওনার সবচেয়ে বেশী পালা ছাপা হয় এই ‘সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী’ থেকেই। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত অনেক পালার প্রকাশক ছিলেন দাদু। পূজাপদ্ধতি, যাত্রাপালার পাশাপাশি ‘হঠযোগ সাধনা’, ‘যাদু প্রদর্শন’, ‘হস্তবিচার’ ইত্যাদি বিষয়েও বটতলার বই সমান জনপ্রিয় ছিল। গল্প শুনেছি – এখনকার পি. সি. সরকার মানে প্রদীপ সরকারের বাবা প্রতুল সরকার। তাঁর গুরু ছিলেন গণপতিবাবু।এই মুহূর্ত্তে তাঁর পদবী মনে পড়ল না। তাঁর যাদুবিদ্যার বই-র প্রকাশক ছিলেন দাদু। তাঁর একটি মেয়ে দ্বিখণ্ডিত করার খেলায় দাদুর অনুমতিক্রমে আমার বড় মাসীকে নিয়ে যেতেন।
বটতলার বই-এর গল্প থেকে অন্য গল্পে চলে এলাম। এই বটতলার প্রকাশকরা বাংলা সাহিত্যের নবপ্রাণ সঞ্চারক হলেও—আর্থিক ভাবে অধিকাংশজনই সম্পন্ন হতে পারতেন না। তার একটা কারণ এইসব বইয়ের অতি স্বল্পমূল্য। বিক্রি যদি হয় পাহাড় প্রমাণ, লভ্যাংশ - একটি ছোট ঢিপি। কিন্তু তাঁদের কম্প্রোমাইজ-এর (বাংলা প্রতিশব্দ না জানা থাকায় লিখলাম) বা প্রচারের কোন পরিকল্পনা ছিল না। দাদু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন—‘আমরা প্রকাশক, বই-এর গুরুত্ব বুঝে খদ্দের আসবে। কিন্তু রিটেলারদের অসুবিধা, সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হয় খদ্দের ধরার জন্য।’
পাহাড় প্রমাণ বিক্রির কথা বললাম। কিন্তু তার পরিমাণ সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা নাই। ভাষা ভাষা ধারণা হয় পোস্টে আসা চিঠিপত্র দেখে। বটতলায় কাউণ্টার বিক্রির চেয়ে বেশী বিক্রি ছিল গ্রামগঞ্জ থেকে আসা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। এই চিঠি আসত প্রধানতঃ পোস্টকার্ডের মাধ্যমে। ইনল্যাণদও মাঝে মাঝে আসত। বিশ-পঁচিশটা পোস্টকার্ড একসাথে করে বাণ্ডিল করা হত। সেইরকম অজস্র বাণ্ডিল এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হত। সেটিও পাহাড়ের আকার ধারণ করলে কি করা হত ঠিক মনে নাই। সেই সময় এই বটতলার বই-এর চাহিদাকে জনপ্রিয়তা না বলে ‘সামাজিক প্রয়োজনীয়তা’ বলে চিহ্নিত করাই ঠিক হবে। সামাজিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে – এই বই-এর চাহিদাও কমতে থাকে। এইসময় দরকার ছিল দক্ষ হাতে আধুনিকীকরণ। সেটা বোধহয় সম্ভব হয়নি উত্তরসুরীদের অক্ষমতায়। ফলে সেই প্রকাশনার ধারা আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি—পরবর্তী প্রজন্ম ঐতিহ্যকে সম্মান না করে অর্থ উপার্জনের নানা পথ বেছে নিয়েছে হয়ত। সেই সব বই-এর ভগ্নাংশ হয়ত কলেজ স্ট্রীটের কোন প্রকাশক রক্ষা করে চলেছেন আগামী গবেষণার আকর হিসাবে। বাংলার আদি প্রকাশনার প্রবাহমান স্রোতের ইতিহাসটুকু অন্ততঃ রক্ষিত হোক।
প্রবন্ধ
আমরা
বাঙালি
অনিশা দত্ত
সল্টলেক, কলকাতা


লেখিকা পরিচিতি: প্রাক্তন অধ্যাপিকা (ফলিত গণিত) বর্ধমান উইমেন্স কলেজ নামী পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখিকা, পুস্তক প্রণেতা আকাশবাণী কলকাতায় প্রাক্তন কথক। সায়েন্স এ্যসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর পক্ষে ‘বিজ্ঞান মেলা ‘ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক।
ইদানীং একটা শব্দ প্রায়ই শোনা যায় ‘বাঙালিয়ানা’। শব্দটা হয়ত ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। বরং শুদ্ধ ভাষণে বলা যাক বাঙালির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন বা বঙ্গসংস্কৃতির উপস্থাপনা, প্রাচীন ঐতিহ্য ও বহমান সভ্যতাকে উত্তরোত্তর সংস্কৃত ও সমৃদ্ধতর করে তোলাটাই ‘বাঙালিয়ানার’ সার্থকতা। এক সময় বলা হত, ‘What Bengal thinks today, India will think tomorrow.’ অর্থাৎ আমাদের বাংলা হল, ভারতের পথপ্রদর্শক। ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়ার সময় বাংলার চরম সর্বনাশ করে গেছে, “বঙ্গভঙ্গ”। আমরা ছোটবেলা থেকে জেনেছিলাম, পূর্ববঙ্গ- পশ্চিমবঙ্গ। তারপর আমাদের যৌবনে ভাষা - আন্দোলনে জয়ী হয়ে গর্বিত পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল পৃথক রাষ্ট্র। ঘোষিত হল নতুন নাম, ‘বাংলাদেশ‘! ব্যক্তিগত আবেগে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, পূর্ববঙ্গর নতুন নামকরণ হল বাংলাদেশ আর আমরা একপেশে পশ্চিম বাংলা। ‘আ মরি’ বাংলা ভাষা, মোদের গরব মোদের আশা’ - এতো আমাদেরও ভাবাবেগ। ‘কোথায় ফলে সোনার ফসল, সোনার কমল ফোটেরে! সে আমাদের বা্ংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে‘। এই একই ভাবনায় পশ্চিম বাংলা ও আপ্লুত থাকে। কবিগুরুর বঙ্গ প্রণতিতে, ‘বা্ংলার বায়ূ, বাংলার ফল, ….পুণ্য হউক, পুণ্য হউক…’এ তো দুই বাংলারই প্রাণের কথা। কিন্ত পূর্ব বাংলা, ‘বা্ংলা দেশ’ নামেই জিতে গেল। একটা সময় গেছে, যখন বাঙ্গালী সমাজ ঘোর কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। তখন বঙ্গদেশকে ‘আচারের তুচ্ছ মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলেছিল গ্রাসি’….। সে সময়ে, বিশ্বকবি বড় বেদনায় সখেদে ব্যাঙ্গোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ‘সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি’ ‘সেই তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার আজ দূরীভূত। সঙ্কীর্ণমন্যতা থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালী, বিশ্ব দরবারের মুক্ত অঙ্গনে পা রেখেছে। সমাজ-সংস্কারে, সাধনায়–সংগ্রামে, কর্মনিষ্ঠায়-মননে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বাংলার অব্যাহত অগ্রগতিতে পথ দেখিয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গসন্তান,……
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ…. কত নাম করব! বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সতেরো কোটি ছুঁইছুঁই, আর পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ কোটি। অর্থাৎ এখন সাত কোটির বদলে সাতাশ কোটি বাঙালির যৌথ দায়িত্ব বাংলার ঐতিহ্যকে সদা গৌরবোজ্জ্বল করে তোলা। বা্ংলার ইতিহাসে স্থাপত্য-ভাস্কর্য, চারুকলা-কারুকলা ইত্যাদির অবদান অনন্য। হস্তশিল্প–কুটিরশিল্প, মৃৎশিল্প, তন্তশইল্প–ঢাকাই শাড়ি, বাটিক-ছাপা, সুদৃশ্য কাঁথা সীবন, মুর্শিদাবাদ রেশমী শাড়ি, সবই বাংলার স্বকীয়তা। লোক-সংস্কৃতিতে লোকনৃত্য, পল্লীগীতি, বাউল গান ইত্যাদি এখনও সমান জনপ্রিয়। বাংলার ঢে্ঁকি ছাঁটা চাল, আচার, বড়ি, মোয়া, মোরব্বা, আমসত্ত্ব ইত্যাদি আজও আদরণীয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য বাংলার মিষ্টান্ন বৈচিত্র্য। এগুলি তো ‘বাঙালিয়ানা’র ই এক অঙ্গ।
বাঙ্গালী আবেগপ্রবণ জাতি। ‘বুকভরা মধু, বাংলার বধূ….. মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে’। বাঙ্গালী পরিবারে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা-সখ্যতার মাধুর্য, কর্তব্য-দায়িত্ব, শ্রদ্ধা-সহবৎ এর মর্যাদা, সর্বোপরি ত্যাগের মহিমা যে কোনও জাতিকে পরাজিত করবে। কিন্ত ক্ষোভের বিষয়, ইদানীং বঙ্গ সংস্কৃতি খানিক অবক্ষয়ের দিকে। বাঙালির সমাজ ও সংসার যে বন্ধনে আবদ্ধ থাকত, তা’ এখন আর তেমন সুদৃঢ় নয়। কালের যাত্রায় সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়, সমাজে সংসারে পরিবর্তন আসে। কিন্তু Universal Moral Values বা বিশ্বজনীন আদর্শ মূল্যবোধ অপরিবর্তনীয়। চিরন্তন শাশ্বত।
নূতন প্রজন্মের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে ‘আমার জীবন, আমার’, যা নিঃসংশয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির পরিপন্থী। বাংলার ঐতিহ্যে মজ্জায়-মজ্জায়, মর্মে-মর্মে যে সনাতন নীতি নিহিত রয়েছে তা’ স্বার্থসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক নয়। সাবেক বাঙালিয়ানার অন্তরের অনুভব হল, ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।‘ বাঙালি যেন তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সদা গৌরবোজ্জ্বল রেখে বলতে পারে, ‘আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে ব্রজ বঙ্গে।‘ দুই বাংলারই প্রাণের আকুতি হল, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’।
গল্প

"প্রেম কখনো শুধু মধুর স্মৃতির গল্প নয়; এটি কখনো কখনো হয়ে ওঠে জীবনের গভীরতম বিষাদের প্রতিচ্ছবি। কিছু সম্পর্কের শেকড় মাটির গভীরে পোঁতা থাকলেও তাদের ডালপালা ছড়ায় না, ফুল ফোটে না। তবুও সেই অসম্পূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে থাকে এক অনন্য সৌন্দর্য, এক নিঃশব্দ সুর। কারণ প্রেমের পূর্ণতা তার প্রকাশে নয়, বরং হৃদয়ের নিঃশব্দ অনুভবে। এই গল্প এমনই এক অসম্পূর্ণ প্রেমের, যেখানে স্বপ্ন, ত্যাগ, আর অনুভূতির গভীরতাই একে বিশেষ করে তুলেছে। এখানে সময়ের সীমানা পেরিয়ে ভালোবাসা বেঁচে থাকে, যদিও তার পূর্ণতা অধরাই থেকে যায়।"
নগাবান্ধা গ্রামের এক কোণে নদীর ধারে ছোট্ট একটি মাটির বাড়ি। বাড়িটির মালিক কৃষ্ণচূড়া গাছটির মতোই পরিচিত, নাম কাজলপ্রিয়া। কাজলপ্রিয়া ছিলো গ্রামের গর্ব। নগাবান্ধার মেয়ে হয়েও সে উচ্চশিক্ষার আলোয় আলোকিত। তার মেধা আর সৌন্দর্য যেন এক অনন্য মিশ্রণ।
কাজলপ্রিয়ার বাবা রাজীব চৌধুরী ছিলেন একজন কৃষক। তিনি মেয়েকে নিয়ে গর্ব করতেন, কিন্তু তার বয়স বেড়ে চলেছে। ফলে তার একটাই চিন্তা ছিল, কাজলপ্রিয়ার বিয়ে। কাজলপ্রিয়া অবশ্য বিয়ের কথা ভাবতেই পারত না। তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষক হয়ে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার আলো দেখানো।
কিন্তু সময় তো কারো জন্য থেমে থাকে না। রাজীব চৌধুরী কাজলপ্রিয়ার বিয়ের কথা পাকা করলেন পাশের গ্রামের ধনী জমিদার পরিবারের ছেলে রায়হানের সঙ্গে। রায়হান ছিলো সুদর্শন এবং বেশ উচ্চাভিলাষী। কিন্তু কাজলপ্রিয়ার মন তাকে কখনোই আপন করতে পারল না।
কাজলপ্রিয়া জীবনে তখন প্রবেশ করলেন কাজি। শহরের কলেজ থেকে সদ্য পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরেছেন। কাজলপ্রিয়ার মতোই বিনয়ী এবং শিক্ষানুরাগী। কাজি একদিন গ্রামের লাইব্রেরিতে কাজলপ্রিয়ার সাথে দেখা হয়েছিল । প্রথম কথোপকথনেই তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূচনা হলো।
কাজি বললো,
“তুমি তো খুব ভালো লিখো, কাজলপ্রিয়া। তোমার লেখাগুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমি চাই, গ্রামের মেয়েদের জন্য তুমি কিছু একটা করো।”
কাজলপ্রিয়া মৃদু হেসে বললো,
“আমারও তাই ইচ্ছে, কিন্তু সংসারের দিকটা তো দেখতে হবে। বাবা চান আমার বিয়ে হয়ে যাক।”
কাজি একটু চুপ করে থেকে বলল,
“তাহলে কি স্বপ্নগুলো মরে যাবে?”
কাজলপ্রিয়ার চোখে জল এলো। কিন্তু সে মুখ তুলে দৃঢ় কণ্ঠে বলল,
“স্বপ্ন কখনো মরে না, কাজি। আমি জানি, কোনো না কোনোভাবে আমার স্বপ্নপূরণ হবেই।”
এরপর থেকে তাদের দেখা হওয়া আরও বাড়ল। কাজি আর কাজলপ্রিয়ার বন্ধুত্ব একসময় গভীর হয়ে উঠল। তবে এই সম্পর্ক নিয়ে কেউ মুখ খোলেনি। কাজলপ্রিয়া জানতো, তার জীবন সহজ নয়। তবুও তাদের হৃদয় একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল।
একদিন রায়হানদের পক্ষ থেকে কাজলপ্ৰিয়ার বিয়ের তারিখ ঠিক হলো। পুরো গ্রামে বিয়ের আয়োজন নিয়ে হৈচৈ শুরু হলো। কাজলপ্রিয়া মনে মনে অস্থির। কাজির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা আর সামলাতে পারল না। সে গোপনে কাজির কাছে গেল।
“কাজি, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল,” কাজলপ্রিয়া কাঁপা গলায় বলল। কাজি শান্ত কণ্ঠে বলল,
“আমি জানি, কাজলপ্রিয়া। বিয়ের খবর শুনেছি। আমি কিছু বলতে চাইনি, কারণ তোমার বাবা বহুৎ কষ্ট করে তোমাকে মানুষের মত মানুষ করেছে, আর আমি হঠাৎ করে তোমার জীবনে এসে এত বড় প্রতারণা তোমার বাবার সাথে করতে পারবো না। তোমার বাবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাধা
হয়ে দাঁড়ানোর অধিকার আমার নেই।”
কাজলপ্রিয়া চোখের জল ধরে রাখতে পারল না।
“কিন্তু আমি কি সুখী হতে পারব, কাজি? আমার তো স্বপ্ন আছে, লক্ষ্য আছে। রায়হান আমাকে তা পূরণ করতে দেবে তো?”
কাজির মনেও তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে কাজলপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,
“তোমার ইচ্ছা, তোমার স্বপ্ন, তোমার জীবন—এই সবকিছুই তুমি নাও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করবে। কেউ যদি তোমাকে বোঝার চেষ্টা না করে এবং তোমাকে সমর্থন না দেয়, তবে তুমি নিজেই নিজের শক্তি হয়ে ওঠো। হয়তো আমাদের পথ এক নয়, কিন্তু আমি জানি, তুমি একদিন ঠিক সবার মন জয় করবে এবং সফলতা অর্জন করবে।”
সেদিন কাজি আর কাজলপ্রিয়ার মধ্যকার কথাগুলো যেন এক অনন্ত বিষাদের প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়ে গেল। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। কাজলপ্রিয়া অনেক চেষ্টার পরও কাজির সঙ্গে আর দেখা করতে পারল না।
বিয়ের পর কাজলপ্রিয়া শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। রায়হান ছিল আধুনিক মানসিকতার মানুষ, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কাজলপ্রিয়া তার লেখালেখি চালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু রায়হানের পক্ষ থেকে সাপোর্ট পাইনি। ধীরে ধীরে কাজলপ্রিয়ার স্বপ্নগুলো স্থগিত হতে লাগল।
অন্যদিকে কাজি তার স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত ছিল। সে গ্রামের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করল, যেখানে মেয়েরা বিনা পয়সায় পড়াশোনা করতে পারবে। কাজলপ্রিয়ার অনুপ্রেরণা তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।
দশ বছর পর, একদিন কাজলপ্রিয়া গ্রামে ফিরে এলো। বাবা মারা গেছেন, তাই পৈতৃক বাড়িটা দেখতে এসেছিল। কাজির সঙ্গে আবার দেখা হলো পাগলাদিয়ার ধারে। আজকাল কাজির সাহিত্য জগতে একটা চর্চিত নাম। কাজলপ্রিয়ার অনুপ্রেরণাই কাজি একজন সফল সাহিত্যিক। কাজির চোখে কাজলপ্রিয়াকে দেখার সেই গভীরতা এখনো অটুট।
“তুমি ভালো আছ তো?” কাজি জিজ্ঞেসা করল।
কাজলপ্রিয়া ম্লান হেসে বলল,
“ভালো আছি। সংসারের দায়-দায়িত্বে ভালো না থেকেও ভালো থাকার অভিনয় করতে শিখেছি। কিন্তু তোমার কাজগুলো দেখে মনে হয়, আমার স্বপ্নগুলো আজ তোমার হাত ধরে পূর্ণতা পেয়েছে।”
কাজি কোনো কথা বলল না। তাদের সম্পর্ক কখনো প্রকাশিত হয়নি, কখনো পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু তাদের হৃদয়ে যে ভালোবাসা ছিল, তা কোনো বাধায় থামেনি।
সেদিনের পর কাজলপ্রিয়া আর কাজির কখনো দেখা হয়নি। কাজলপ্রিয়া ফিরে গেল তার বাস্তব জীবনে, আর কাজি ডুবে রইল গ্রামের মানুষের কল্যাণে এবং সাহিত্য জগতে।
তাদের ভালোবাসা হয়তো অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতাই তাদের জীবনকে আরও অর্থবহ করে তুলেছিল।
"অসম্পূর্ণ প্রেমই আসলে প্রকৃত প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করে। কাজলপ্রিয়া ও কাজির ভালোবাসা কখনো প্রকাশিত হয়নি, তবুও তাদের হৃদয়ের বাঁধন ছিল চিরন্তন। স্বপ্ন আর বাস্তবতায় তারা একে অপরের থেকে দূরে থাকলেও তাদের অনুভূতিগুলো অক্ষত ছিল। অসম্পূর্ণতার এই গল্পই শেখায়, প্রকৃত প্রেম কখনো দাবি করে না; বরং ত্যাগ আর সম্মানের মাধ্যমে আরও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। জীবনের পথে চলতে গিয়ে তারা আলাদা হয়ে গেলেও, তাদের ভালোবাসার স্মৃতি চিরকাল একে অপরের হৃদয়ে রয়ে গেছে। কারণ, কিছু ভালোবাসা শব্দের চেয়ে অনেক বড়, যা শুধু অনুভূত হয়, বলা যায় না।"
গল্প

একটি শহর ছিল, যেখানে সবকিছুই ছিল নিষিদ্ধ।
একমাত্র টিপ-ক্যাট খেলাটাই নিষিদ্ধ ছিল না। শহরের পেছনের তৃণভূমিতে লোকেরা জড়ো হতো এবং একসাথে টিপ-ক্যাট খেলে দিন পার করে দিত।
যেহেতু সবকিছু নিষিদ্ধ করা হয়েছিল একই সময়ে এবং মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে, সেহেতু কারোরই কোনো অভিযোগ ছিল না কিংবা মানিয়ে নিতে কারও কোনো সমস্যা হচ্ছিল না।
এভাবেই চলে গেল একবছর। একদিন নগর পিতার মনে হলো, সবকিছু নিষিদ্ধ করে রাখার আর কোন কারণ নেই। একজন বার্তাবাহককে পাঠানো হলো শহরের মানুষদের কাছে।
বার্তাবাহক জানতেন সবাইকে কোথায় পাওয়া যাবে। তিনি সেই তৃণভূমিতে ছুটে গেলেন—
“শোনো, তোমরা এখন মুক্ত। যা ইচ্ছে করতে পারো এখন থেকে।”
নাগরিকেরা টিপ-ক্যাট খেলতেই থাকল।
“বুঝেছ?”, বার্তাবাহক চেঁচিয়ে বলল।
“তোমরা এখন মুক্ত। যা ইচ্ছে করতে পারো।”
“আচ্ছা”, নাগরিকেরা উত্তর দিলো। “আমরা টিপ-ক্যাট খেলছি।”
বার্তাবাহক তাদেরকে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিতে লাগলেন। তারা চাইলেই তাদের জন্য সুন্দর এবং উপযুক্ত পেশাগুলোকে আবারও বেছে নিতে পারে। কিন্তু, নাগরিকেরা তার কথায় পাত্তা না দিয়ে টিপ-ক্যাট খেলতেই থাকল। এক মুহূর্তের জন্যও থামল না।
ব্যর্থ হয়ে বার্তাবাহক ফিরে গেলেন নগর পিতার কাছে এবং তাকে সব জানালেন।
“সহজ ব্যাপার”, নগর পিতা বললেন। “টিপ-ক্যাট খেলাটাই নিষিদ্ধ।”
এই ঘোষণা শোনার পরেই নাগরিকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তারা অনেককে মেরেও ফেললো।
তারপরে সময় নষ্ট না করে আবার টিপ-ক্যাট খেলতে ফিরে গেল।
★টিপ-ক্যাট — ডাংগুলি খেলা
গল্প

আব্দুল হক তাহলে সত্যিই মারা গেছেন।
কে যেন বলল "লাশের মুখটা একটু খুলে দাও"।
লাশ কথাটা তাঁর মৃত্যুকে যেন প্রত্যয়িত করল, হক সাহেব নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, আবার তিনি সালেহার পাশে গিয়ে শুতে পারবেন। ছেলেদের হাজার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি সালেহাকে উঠোনের পশ্চিমদিকে কলতলার পাশে কবর দিয়েছিলেন। আসলে সালেহাকে না, হক সাহেব সেদিন পাড়ার প্রোমোটার মুন্নার হাতে এই সাত কাঠা জমিসহ বাড়িটা তুলে দেওয়ার জন্যে তাঁর তিন ছেলের সম্মিলিত অশুভ প্রয়াসের কবর দিয়েছিলেন।
এই সময়টা সমস্ত লাশের মত হক সাহেবেরও বেশ ভালো লাগছিল। মেজ বউটা অসময়ে চা খেতে চাইলে চায়ের কাপটা এমন ভাবে সামনে এনে রাখত, যে প্রতিবারেই হক সাহেব প্রতিজ্ঞা করতেন চা খাওয়া ছেড়ে দেবেন... সেই মেজ বউটার কান্না দেখে হক সাহেব বেশ মজা পাচ্ছিলেন। নেহাত লাশ, নইলে হাসির আওয়াজ সকলেই শুনতে পেত। প্রতিবেশী মান্নান মোল্লা, যে কিনা পাঁচিল দেওয়ার সময় গা জোয়ারি করে, মাস্তান ডেকে হক সাহেবের জমিতে প্রায় দেড় ফুট ঢুকে এসেছে, সেও কত কি ভালো ভালো কথা বলছে। হক সাহেবের বমি পাচ্ছিল, তবে লাশেদের কিনা বমি হয়না!কিন্তু এরা এত দেরি করছে কেন? আত্মীয়-পরিজন প্রায় সকলেই তো এসে গেছে। গোসল দেওয়াও হয়ে গেছে সেই কখন! আর কোন ব্যবস্থাই তো হচ্ছে না। মাটি দেবে কখন এরা?
হক সাহেব সালেহার পাশে, কাছাকাছি যাওয়ার জন্যে একটু বেশিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।
হঠাৎ বাইরে একটা গাড়ির শব্দ। বড় খোকার ছোট ছেলেটা এসে খবর দিল ম্যাটাডোর এসে গেছে। ম্যাটাডোর কি হবে? ভেবে পাচ্ছিলেন না হক সাহেব।
এমন সময় দোতলার সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েক জনের পায়ের শব্দ... ঐ তো তাঁর তিন ছেলে, সঙ্গে
মৌলানা সাহেব। কানে ভেসে এল মৌলানা সাহেবের কন্ঠ, "তাহলে তোমরা সবাই একমত? কিন্তু হক সাহেব তো প্রায়ই বলতেন, এখানেই, ভাবীর পাশেই তাঁর মাটি দেওয়া হবে ঠিক হয়ে আছে"।
বড় ছেলে বলল, "আসলে চাচা, সবারই ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই জায়গার অভাব দেখা দেবে। তাছাড়া দেশে তো অনেকেই আছে, আর আমরাও তো যাব মাঝে মধ্যেই"।
ছাঁৎ করে উঠলো হক সাহেবের বুকটা, মারা গিয়ে না থাকলে এই ধাক্কায় দু'নম্বর স্ট্রোকটা নিশ্চিত বাঁধা ছিল। এরা তাঁকে দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কবর দেবে?
হক সাহেবের কেমন একটা ঘোর ঘোর লাগছে। যেন সমস্ত শব্দ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। চারপাশের শব্দগুলো যেন ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই সময় খাটিয়াটা নড়ে ওঠে। খুব ধীরে। হক সাহেব স্পষ্ট টের পান, তাঁর খাটিয়াটা নড়ছে। খাটিয়াটা উঠছে। তিন ছেলে আর এক নাতির শক্ত চওড়া কাঁধে হক সাহেবের পলকা শরীরটা সহজেই উঠে যায়। ম্যাটাডোরের পিছনের কাঠ নামানোর শব্দ হয়। হক সাহেব চারটে শক্ত কাঁধে চেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। উঠোন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ওরা কি তাহলে এই উঠোনটা আর রাখবে না? একটা আম গাছ আর দুটো পেয়ারা গাছ পেছনে পড়ে থাকে। হক সাহেব চলে যাচ্ছেন। চলে যাচ্ছেন। তিনি টের পাচ্ছেন তিনি দূরে কোথাও চলে যাচ্ছেন, দূরে... বহুদূরে। তিনি আর কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না।
সব কিছু কেমন নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। হঠাৎ কেমন তীব্র একটা ইচ্ছে হলো হক সাহেবের। সালেহার কী হবে? সালেহা বিবি? তাঁর প্রবল ইচ্ছে হতে থাকলো খাটিয়ার ফাঁক দিয়ে সালেহার কবরটা একবার দেখার। একবার। কলতলার একেবারে পাশেই। অন্তত একবার। কিন্তু কী করে দেখবেন...
আব্দুল হক তো মারা গেছেন!
প্রবন্ধ
বাংলার
পূর্ব-পশ্চিম
রথীন্দ্রনাথ বড়াল
ডঃ নগেন ঘোষ লেন, কলকাতা

আমেরিকায় পৌঁছে অবাক হয়েছিলাম বাসে চেপে। গাড়ীর স্টিয়ারিং উল্টোদিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের ডানদিকের বদলে বাঁদিকে। আপ-ডাউন রাস্তার চলনও উল্টো। থাকার ঘরে ঢুকে দেখলাম—আলো-পাখা জ্বালানোর সুইচ্ উল্টো। মানে আমাদের দেশে – নীচে নামালে আলো জ্বলে – ওদেশে ওপরে ওপরে তুললে আলো জ্বলবে। আজ আমেরিকার আর ভারতের বৈপরিত্যের কথা বলতে বসিনি। বলতে চেয়েছি—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিদিনের ব্যবহারিক বৈপরিত্য।
মামাবাড়ি গেলে দেখা হল বেবেদিদিদের সাথে। খেলাধূলা-খাওয়াদাওয়া চলতে থাকত। আমরা ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ না করে কিছু মুখে দিতাম না। কিন্তু বেবিদিদি ও আরো ওই বাড়ির দাদাদিদিদের দেখতাম—দিব্যি, ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃরাশ সারতে। তাদের দাঁতমাজা স্নানের আগে। জানিনা এই ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের সব জায়গায় চালু কিনা। মুখ ধোওয়ার পর স্নান। আমরা স্নান করতাম খাওয়ার মানে মধ্যাহ্নভোজের আগে। কোনোদিন বাদ পড়লে—সেদিন আর স্নান করা হত না। কিন্তু অপরপক্ষে দেখতাম খাওয়ার আগে স্নানের বাধ্যবাধকতা না থাকা। আগে করলেও চলে পরে করলেও চলে। স্নানের আগে সারা অঙ্গে সরিষার তেল আর মাথায় নারকেল তেল মাখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গের দাদা-দিদি-বন্ধুদের মধ্যে এই বাধ্যবাধকতা ছিল বলে মনে হয়নি বরং স্নানের পর তেল মাখার প্রচলন ছিল কিংবা আছে বলেই মনে হয়। আর একটি বিষয়—গামছার ব্যবহার। গামছা ঘটিদের জীবনযাপনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। বাবা-কাকা-দাদুদের স্নানের আগে পরে গামছা পরে কাটাতে দেখেছি। আর আমদাদুতো জীবনটা কাটিয়ে দিলেন গামছা পরেই। শখ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালো গামছা আনানো অনেক ঘটি বাবুদের অভ্যাস ছিল। বিশেষতঃ বাঁকুড়ার গামছা কিংবা উড়িষ্যার গেরুয়া গামছা। এই গামছা প্রীতি ওপার বাংলার মানুষের বোধহয় কম। গামছার পরিবর্তে অন্য প্রথা নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল।
স্নানের পরই আসে খাওয়ার কথা। এর বৈচিত্র্যের কথাতো বলে শেষ করা যায় না। কিছু কথা উল্লেখ করি—যেগুলো চোখে পড়েছে। ভুল কিছু বললে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। প্রথমে বলি, পান্তা খাওয়ার কথা। আমরা ঘটিরা তো ভুলেও পান্তা খাব না। অরন্ধনের একদিনই এই পান্তাভাত অল্প করে খাওয়া হত। অথচ ওপার বাংলার মানুষের মধ্যে পান্তা খাওয়ার মধ্যে বিপুল ভালবাসা দেখেছি। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের মাছ আর শাকপাতা খাওয়ার অভ্যাসও—পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেকটা আলাদা।
নানারকম শাক, মান, কচু, ওল ইত্যাদির ব্যবহার এপার বাংলার মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু ওপার বাংলার মামীমা, দিদাদের হাতের এইসব নিরামিষ পদ আমায় বার বার মোহিত করেছে। মাছের বৈচিত্র্য সত্যিই বাংলাদেশকে মানে পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলাকেই সমৃদ্ধ করেছে। রুই, কাতলা, ইলিশ, চিংড়ির জনপ্রিয়তা দুই বাংলায় থাকলেও— দুই বাংলার জন্য দুটো আলাদা তালিকা অবশ্যই আমি তৈরী করে দিতে পারি। পশ্চিমবাংলা—পারশে, ট্যাংরা, তপশে, ভাঙ্গ, গুরজারি, নেদশ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর পূর্ব বাংলার—আর, বোয়াল, চিতল পাবদা। এই চারটি মাছ আমরা ছোটবেলায় খাওয়ার সুযোগ পায়নি। পশ্চিমবাংলার তালিকার মাছ পূর্ববঙ্গের ভাইবোনেরা কতটা খেয়েছে ঠিক জানা না থাকলেও—ব্যবহারের প্রকট বৈপরিত্য অবশ্যই ছিল আছে। বেলে, গুলেও পশ্চিমবাংলার প্রিয় মাছ। ভেটকি, পমফ্রেট দুই বাংলারই প্রিয়। আর শুঁটকি মাছের নানা পদ—একান্তই পূর্ববঙ্গের। এই বঙ্গের কাউকে আমি শুঁটকি চাখতে দেখিনি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে মূল পার্থক্য বোধহয়—পরিশ্রম, অধ্যাবসায় আর মানসিকতায় সেক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে কম করে ৫ গোল দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার বাঙালীদের মধ্যে এক বড় অংশকে দেখেছি—কোন উদ্যোগ ছাড়া পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে। কেউ কেউ পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেনি। বরং সংকুচিত হতে হতে সেই সব ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। আমার মামাবাড়ীর ঐতিহ্যশালী সুপ্রাচীন বটতলার বইয়ের ব্যবসার কথা মনে আসে। অন্যত্র সে আলোচনা করব। মা-মাসী-কাকীদের কোনোরকম চাকরীক্ষেত্রে যোগদানের উৎসাহ দেখিনি কিংবা সামাজিক পরিস্থিতি সেকাজে বিরত করেছে। অপরপক্ষে পূর্ববাংলার মানুষদের কঠোর পরিশ্রমে ও কৃচ্ছ্বসাধনে এই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী পদে তাদের যোগদান উল্লেখযোগ্য। ওপার বাংলার মা-মাসীরাও স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেছেন কিংবা ক্ষুদ্র সংগঠন/ব্যবসায় মনোনিয়োগ করেছেন। অলসতা সর্বক্ষেত্রে এবাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে। অপরপক্ষে উদ্যম ওপার বাংলার মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে একটু একটু করে। এপার বাংলার মানুষ তাদের পাঁচমহল বাসস্থান রক্ষা করতে পারেনি। ভাড়া দিতে দিতে এক এক মহল হাতছাড়া হয়েছে। তারপর পুরোটাই প্রোমোটরদের দখলে। ওপার বাংলার কাকুরা, জ্যেঠুরা নিঃস্ব অবস্থায় এসে এক কামরা ঘরে অবর্ণনীয় কষ্ট করে—আজ তারা সুস্থ পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের অধিকারী হয়েছেন। অপরপক্ষে, এ পারের অট্টালিকায় বট-অশ্বত্থের ঝুড়ি প্রায়শই দেখা যায়—যেগুলির সংস্কার করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। তাই ধ্বংস ক্রমশই ত্বরান্বিত হচ্ছে।
গল্প


"কাল আসবে তো আমাদের দোকানের নববর্ষের পুজোতে? পুজোর পরে ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাবো। মা বলে দিয়েছেন তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে। কালকে আমার গানের প্রোগ্রামও আছে। মা বাবার সাথে দেখা করে দুজনে মিলে যাবো সেখানে। জানো তো একটা বড়ো এন.জি.ও এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে।"
নীলার কথাতে আকাশ নিরুৎসাহী ভঙ্গিতে বলে -
"কাল আসতে পারবো না নীলা, সরি। কাল আমি একজন বিশেষ মানুষের সাথে দেখা করতে যাবো।"
আকাশের না শুনে নীলার খারাপ লাগে। ও আশা করেছিলো যে আকাশ নিশ্চয়ই কাল ওদের দোকানের নববর্ষের পুজোতে যাবে। নীলা আর আকাশ দুই বছর হলো একটা সিরিয়াস সম্পর্কে রয়েছে। গত মাসে দুজনের বাড়িতে ওদের সম্পর্কের ব্যাপারটা জানাতেই দুজনের মা বাবা বেশ খুশিই হয়েছেন।আকাশের মম অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন ছেলের বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু কোন অজানা কারণেই ওনার ছেলে বারবার নানা বাহানা করে বিয়েতে রাজি হয়নি।
আকাশ একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। পুজোর পর ও মুম্বাইতে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তাই এই শ্রাবণ মাসেই আকাশের সাথে নীলার রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলতে চান আকাশের মম রমাদেবী।
"কোথায় যাবে তুমি?"
নীলার প্রশ্নটা শুনে উত্তর না দিয়ে ওকে একটা পাল্টা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসে আকাশ,
"আচ্ছা নীলা যদি বিয়ের পর মুম্বাইতে আমি আমাদের সাথে একজনকে নিয়ে এসে রাখি তোমার কোন আপত্তি আছে? এই ব্যাপারে আমার বাড়িতে তুমি কখনো কিছু বলবে না কিন্তু। এটা আমার রিকোয়েস্ট।"
নীলা ওর কথা শুনে বেশ অবাক হয়।এই মানুষটার সাথে ও দুবছর সম্পর্কে আছে। এখনও ও এই মানুষটাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। অবাক চোখে নীলা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।
"উত্তর দিলে না নীলা?"
"তুমি কি চাও বলো তো?গত দুবছর ধরে দেখছি বছরের কিছু বিশেষ দিনে আমি তোমাকে দেখা করতে বললেই তুমি আসো না। গতবার কলাভবনে আমার গানের প্রোগ্রাম ছিল নববর্ষের দিন।সেখানে তোমাকে ইনভাইট করলাম তুমি এলে না। তোমার নাকি কোন বিশিষ্ট মানুষের সাথে দেখা করার আছে।অদ্ভুত লাগে আমার! বছরের শুরুতে লোকে তার বিশিষ্ট মানুষদের সাথে দেখা করে।আমি ছাড়াও তোমার জীবনে অনেক বিশিষ্ট মানুষ আছে দেখছি!"
কথাগুলো বলে নীলা আকাশের দিকে তাকায়।
ওর কথার কোন উত্তর দেয় না আকাশ।একটু চুপ করে থেকে বলে
"তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে নীলা। যাক গে আজ উঠি। দোকানে যেতে হবে কিছু কেনাকাটি করতে। চলো তোমাকে গাড়িতে করে নামিয়ে দিয়ে যাই তোমার বাড়িতে।"
"নো থ্যাংক্স।তার আর দরকার নেই।"
নীলা রেগে গিয়ে হুট করে চেয়ার থেকে উঠেই গটগট করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে চলে যায়।আকাশ ডাকতে গেলেও নীলা একবারের জন্য থামে না।রেস্টুরেন্টের বাইরে গিয়ে ও ওলা বুক করে বেরিয়ে যায় নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে।
আকাশ বিল মিটিয়ে আস্তে আস্তে রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বের হয়। নিজের দামী গাড়ি চালিয়ে ও গড়িয়াহাট অঞ্চলে একটা শাড়ির দোকানে আসে। নিজে পছন্দ করে দুটো দামী শাড়ি কিনে নিজের বাড়ি ফিরে আসে ও।
ওদিকে নিজের বাড়িতে গম্ভীর মুখে ঢোকে নীলা। ড্রয়িং রুম পেরিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার সময় নীলার মা ওকে ডাকেন।
"নিলু মা এদিকে আয় একটু।"
"মা শরীরটা ভালো লাগছেনা। পরে আসছি।"
অহেতুক একটু বাজেভাবেই মাকে কথাগুলো বলে ফেলে নীলা। মুডটা ওর এমনি খিঁচড়ে আছে।মায়ের কথাও যেন ভালো লাগছেনা।
ওর মা এগিয়ে আসেন ওর দিকে। ওর গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখেন।তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। নীলা ওনাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে
"কিছু বলবে?"
"কি হয়েছে রে তোর? শরীর খারাপ?"
উৎকন্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন উনি। মায়ের অহেতুক উদ্বিগ্নতা এই মুহূর্তে বিরক্ত লাগে ওর। তবুও ও স্বাভাবিকভাবে বলে,
"ওই মাথাটা একটু ধরেছে আর গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। কাল প্রোগ্রাম আছে। একটু রেস্ট করলে ঠিক হয়ে যাবে।"
মাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ও নিজের ঘরে চলে যায়।
পিছন থেকে ও মায়ের কথা শুনতে পায়।
"চা পাঠিয়ে দিচ্ছি তোর ঘরে।একটু খেলে মাথা ব্যাথা কমবে।"
নীলা সিড়ি দিয়ে দোতালায় নিজের ঘরে যেতে যেতে বলে,
"আমি এখন চা খাবোনা। ওষুধ খেয়ে ঘুমাবো। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।"
নিজের ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দেয় ও। মুখ ভার করে বাইরের জামাকাপড়েই খাটের ওপর বসে থাকে নীলা। অনেক অভিমান ভিড় করেছে ওর মনের ভিতরে। ও চুপ করে ভাবতে থাকে আকাশ ওকে কি মনে করে! ওর কথার কোন দাম নেই নাকি আকাশের কাছে?
অনেক চিন্তা ভাবনা করেও নীলা বুঝতে পারে না মুম্বাইতে ওদের সাথে বিয়ের পর কে থাকবে। এবার ওর নববর্ষটা একদম মাটি করে দিলো আকাশ ঠিক গতবারে যেমন করেছিলো। গতবার আকাশ ওর অনুষ্ঠানে আসবে না ওকে বলেছিল। কিন্তু ওর স্টেজে ওঠার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও গ্রিনরুমে আকাশকে ফোন করে গেছে। ও আশা করেছিলো শেষ মুহূর্তে আকাশ অন্তত আসবে।কিন্তু আকাশ আসেনি। খুব খারাপ লেগেছিলো ওর। তবুও ও আকাশকে কিছু বলেনি।
নীলা ঠিক করে কালকের দিনটা কেটে গেলে ও সরাসরি আকাশের সাথে কথা বলে সবকিছু খোলসা করে নেবে। এভাবে ও আর নিজের মনে গুমরে মরতে পারবে না।
**********
আজ নববর্ষ। নীলার বাড়িতে ওর মা বাবা সকাল সকাল একদম তৈরি হয়ে পড়েছেন ওদের দোকানে যাওয়ার জন্য। নীলার তখনও দেখা নেই। বাধ্য হয়ে নীলার মা ওকে নিচতলা থেকে জোড় গলায় ডাকতে থাকেন -
"নিলু মা আর কতক্ষন?"
"আসছি মা।"
নীলা উত্তর দেয়। ওর মা আবার ডাকতেই যাচ্ছিলেন সেসময় ও ওপরের ঘর থেকে নিচে নেমে আসে। আজ ও একটা হলুদ লাল কম্বিনেশনের ঢাকাই শাড়ি পরেছে। তার সাথে পড়েছে ম্যাচিং করে হালকা জাঙ্ক জুয়েলারী। আর খোঁপায় দিয়েছে মোটা জুঁই ফুলের মালা, সাথে মুখে স্বল্প প্রসাধন।
"কি সুন্দর লাগছে যে তোকে নিলু। কিন্তু তোর মুখটা এত শুকনো কেন রে?"
বাবার কথাতে ও একটু কষ্ট করে হাসে। আজ প্রোগ্রামটা না থাকলে এভাবে ও সেজে দোকানের পুজোতেও যেত না।
"মা আজ আকাশ আসতে পারবেনা। ওর কিছু কাজ পরে গেছে।"
শহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে পৌঁছাতে এই গরমে গাড়িতে বসেও বেশ হাঁপিয়ে যায় নীলা।যদিও ড্রাইভার বাতানুকুল যন্ত্রটা চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ও রাজি হয় নি। ওর আবার সেটা সহ্য হয় না।
ওলা থেকে নেমে সামনে এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধাশ্রমটি দেখতে পায় ও। আশ্রমের সামনেই বেশ অনেকখানি বাগান রয়েছে। সেখানেই সামিয়ানা খাটিয়ে সুন্দরভাবে এন. জি. ওর উদ্যোগে সাজানো হয়েছে। সামনেই সারি সারি চেয়ার পাতা। আবাসিকরা সবাই সেখানে বসে আছেন। নীলা জানতে পারে মোট পঞ্চান্নজন আবাসিক এখানে থাকেন।
নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সব আর্টিস্টদের সম্মাননা প্রদান করার পর একজন আর্টিস্ট গান শুরু করেন। তারপর নীলা স্টেজে ওঠে। মাইক নিয়ে গান শুরু করে নীলা। গান গাইতে গাইতে সামনের চেয়ারে দৃষ্টি পড়তেই ও অবাক হয়ে যায়। একি এ কাকে দেখছে ও! আকাশ বসে আছে একদম সামনের আসনে।মনটা ওর খুশিতে নেচে ওঠে। একটু অদ্ভুতও লাগে অবশ্য। ও কাল রাগের মাথায় আকাশকে বলতেই ভুলে গেছিলো ওর প্রোগ্রামের ভেন্যুর কথা। তাহলে ও কী করে যে আসলো এখানে........।
সুন্দর করে নানা গান দর্শকদের সামনে পরিবেশন করে নীলা। অকস্মাৎ পাওয়া খুশি যেন ওর গানের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সত্যি ও মন থেকে আজ সকালে চেয়েছিল বছরের প্রথম দিনটা অন্তত একবার হলেও ও আকাশের সাক্ষাৎ পায়। ভগবান মনে হয় ওর মনের কথা শুনেছেন।
ওর গান শেষ হয়।করতালিতে সবাই ওর গানের জন্য ওকে অভিনন্দিত করে। ও ধীরে ধীরে স্টেজ থেকে নিচে নেমে আসে। অনুষ্ঠান শেষ হলে এনজিওর একজন কর্মকর্তা ওর সাথে কথা বলতে আসতেই নীলা দেখতে পায় আকাশও ওর দিকেই আসছে। ও ওনার সাথে কথা শেষ করে আকাশের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর সাথে কথা বলতে যায়। নীলা একমুখ হাসি নিয়ে আকাশকে জিজ্ঞেস করে,
"তুমি আমাকে নববর্ষে এই সারপ্রাইজটা দেবে আগেই ঠিক করে রেখেছিলে? তাই না?"
"এর থেকেও অনেক বড় কিছু।"
আকাশের উত্তর শুনে চোখ দুটো বড় করে আকাশের দিকে তাকায় নীলা। ও বুঝতে পারেনা আকাশ ওকে কি বলতে চায়।
"এদিকে এসো।"
ততক্ষনে আবাসিকরা সবাই নিজেদের ঘরে চলে গেছেন। আকাশের পিছু পিছু ও একটি ঘরে এসে উপস্থিত হয়। ও দেখে একজন বৃদ্ধা একটা নতুন শাড়ি পরে খাটের ওপর বসে হাসি মুখে মিষ্টি খাচ্ছেন। বৃদ্ধা ওকে দেখেই ফোকলা দাঁতে মিষ্টি করে হেসে বলে ওঠেন,
"আয় নাতবউ। নাতি আমাকে তোর কথা বলেছে। খুব হেঁয়ালি করেছে না তোর সাথে? খুব দুষ্টু ছেলে। আমি ওকে বকে দেবো। ও তোকে বলেনি না আমি তোদের জ্বালাতে তোদের সাথে বোম্বে যাবো?"
নীলা অবাক হয়ে বৃদ্ধার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।
"কি গো কি হলো?"
"মানে ইনি কি তোমার ঠাকুমা? তোমার মা তো বলেছিলেন উনি..."
ওর কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আকাশ বলে,
"হ্যাঁ উনি আমার ঠাম্মা। মম বাড়তি ঝামেলা না পোহানোর জন্য অনেকদিন আগে, তখন আমি কলেজে পরি সেসময় ওনাকে এখানে দিয়ে গেছেন। বাবা মমের সাথে অশান্তির ভয়ে কোনদিন ওনার ওপর কথা বলেন না। আমি বলতে গেলেও মম অনেক অশান্তি করেছে। আমি ঠিক করেছিলাম যেদিন বাইরে যাবো ওনাকে আমার সাথে করেই নিয়ে যাবো। তাই সেদিন তোমাকে বলেছিলাম। আমি ওনাকে আমাদের সাথে নিয়ে যাবো মম আর বাবাকে সে কথা বলতে চাই না। যে মানুষটা ওদের কাছে মৃতা সে কোথায় আছে ওদের সেটা না জানলেও হবে।"
ওদের দুইজনের কথার মাঝেই বৃদ্ধা নীলাকে কাছে ডাকেন।
"এদিকে আয় তো নাতবউ। মিষ্টি খা। নাতি এনেছে। জানিস আমি খুব মিষ্টি খেতে ভালোবাসি।"
নীলা এগিয়ে এসে বৃদ্ধাকে প্রণাম করে বলে,
"শুভ নববর্ষ ঠাম্মা।"
বৃদ্ধা নীলার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বলে "বছরটা খুব ভালো কাটুক তোদের।"
ফোকলা দাঁতে হেসে দুজনের মুখে মিষ্টি তুলে দেন আকাশের ঠাম্মা আর নীলার দিদিশাশুরি হাসিদেবী। ওনার মনে হয় এবারের নববর্ষটা সত্যি অন্যরকম।
রুডি
নুপূর রায়চৌধুরী
গল্প


আজ বেস্পতিবার, তাড়াতাড়ি উঠে গেছে নিনা, অ্যালার্ম-ঘড়ির সাড়ে পাঁচটার হাঁকডাকের অনেক আগে, আসলে উত্তেজনায় কাল রাত থেকেই ঘুম উধাও, আজ যে রুডির পিয়ানো কনসার্ট। সব ঠিকঠাক পারবে তো? হয়ত ঠিক সময়ে স্টেজেই উঠতে চাইল না; অথবা অডিটোরিয়ামে অত লোক দেখে ভয় পেয়ে স্টেজ থেকে নেমে আসতে চাইল, যদি, –কী হবে তাহলে? —--- নাহ, এসব উল্টোপাল্টা চিন্তা করে মনকে অশান্ত করার কোনো মানে হয় না, নিজেকে শাসন করে নিনা। তাছাড়া মিস্টার গিলফোর্ড আছেন না, উনি একই একশ! ঠোঁটের কোণে একচিলতে হালকা হাসি ফুটে ওঠে নিনার।
ডাইনিং রুমের কফি মেকারটা বিপ বিপ আওয়াজ করছে, ওর কাজ শেষ হয়েছে, ফ্রেঞ্চ ভ্যানিলা কফির গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে | ধূমায়িত কফির কাপ হাতে করে বসার ঘরে চলে আসে নিনা । এটা ওর খুব প্রিয় জায়গা, একদিকে কাঠের ফ্রেমের কাচ-দরজা, সেটা খুললেই ছোট্ট একটা ব্যালকনি; অন্যদিকটায় ফ্লোর-টু-সিলিং-কাচের টানা উইন্ডোওয়াল; দুইয়ে মিলে প্রকৃতির সাথে ওর একান্ত যোগাযোগের সেতু রচে । মধ্যপশ্চিম আমেরিকায় শীতকাল খাতা-কলমে তিন মাসের জন্য হলেও এর স্থায়ীত্ব আরও অনেক বেশি। শীত যেন আর শেষই হতে চায় না। তীব্র তুষারপাত ও হাড়কাঁপানো শীতে ব্যালকনিতে যাওয়ার কথা ভাবলেই নিনার কান্না পায়। কিন্তু ওই জানালা দিয়ে তাকালেই এক লহমায় বাইরের প্রকৃতির খোলা প্রান্তরে পৌঁছে যায় নিনা ।
এখন অবশ্য এখানে বসন্তকাল, শীতের কনকনে ঠান্ডা কমে গিয়ে দিনের তাপমাত্রা ৬০ -৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছেপিঠেই ঘোরাঘুরি করে এইসময়। রোজ নয়, মাঝেসাঝে বৃষ্টিও হয়। জানালা দিয়ে বাইরের ছোট্ট বাগানটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিনা। সেখানে এখন নতুন ফুলেদের মেলা বসেছে। সবার প্রথমে অবশ্য ব্লাডরুটগুলোই কচি সবুজ ঘাসের ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করেছিল, কবে যেন প্রথম চোখে পড়ল নিনার? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই তো গেল বুধবারেই-- ওরা কিন্তু বুনোফুল– সাদা সাদা আট-টা করে পাপড়ি আর উজ্জ্বল সোনালি-কমলা কোরক। খুব বড়ো নয় কিন্তু ফুলগুলো, নিনার বুড়ো আঙুলের চেয়ে আর এই এত্তটুকু মাত্র বেশি হবে হয়ত। সূর্যের আলোয় চোখ খোলে আর রাত্রি হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই সপ্তাহে দেখছে ক্রোকাস, ড্যাফোডিল, স্নোড্রপ, আর হায়াসিন্থগুলোও পাপড়ি মেলেছে। টিউলিপ রানীর সাজগোজ এখনও শেষ হতে একটু দেরি আছে, সে এলেই ফুলেদের বসন্ত-বাহার কানায় কানায় ভরে উঠবে। নিনার মনটাও খুশিতে বাচ্চা মেয়ের মতো নেচে উঠল। আর কী আশ্চর্য্য! এই মুহূর্তে নীল আকাশের বুকে পাখির পালকের মতো একপাঁজা যাযাবর মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে হাজির হয়েছে, নিনা র মনটাকে কোন এক স্বপ্নিল সম্ভাবনাময় বেলাভূমিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলেই বুঝি ওরা যড়যন্ত্র করছে । নিনার ছেঁড়াখোঁড়া, জীবন-পথ যেন উত্তরণের নতুন এক দিশা খুঁজে পেতে চলেছে ।
আদ্যিকালের দেয়াল ঘড়িতে সকাল ৮-টার বাজনা বাজলো, নাহ, আর গড়িমসি নয়, কনসার্টে যা যা পরবে রুডি সে সব গোছ করে রাখাই আছে–সাদা ফুলহাতা শার্ট, নেভি-ব্লু স্যুট, মেরুন বো-টাই, আর কালো ড্রেস-শু; নিজের জন্যও একটু চকমকে পোশাক বাছতে হবে, কত লোকজন আসবে আজকের আসরে, হাবিজাবি ভাবে যাওয়া যায় নাকি সেখানে? তা মায়ে-পোয়ে সেজেগুজে তৈরি হয়ে বেরোতে বেরোতে অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু বেশি সময় তো লাগবেই । আজ সারাদিনের ব্যস্ততা, স্কুলের পর রুডির ড্রেস রিহার্সাল, তারপর সন্ধেতে কনসার্ট | নাহ, ছেলেটাকে এবার ঘুম থেকে না তুললেই নয়, রুডির ঘরের দিকে দ্রুত পা বাড়ায় নিনা, দেখতে দেখতে কত বড়ো হয়ে গেল রুডি, এই তো সেদিন ওকে নিয়ে এল, নিনার নিস্তরঙ্গ জীবনে সে এক উত্তেজনাময় দিন গেছে বটে!
চোখ বন্ধ করলেই এখনও সব পরিষ্কার দেখতে পায় নিনা । সেদিনের কাজটা নেওয়ার একটুও ইচ্ছা ছিল না ওর, ওই ধরণের বাচ্চাদের সম্বন্ধে তো ওর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, কীভাবে ম্যানেজ করবে ওদেরকে সারাটা দিন? মেলিসা আগের দিন কত কী বলল ওদের সম্বন্ধে: সময় সময় নাকি সাংঘাতিক অবুঝ আর বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে ওরা । এই তো দুবলাপাতলা চেহারা নিনার-সামলাবে কী করে ওদের? নাহঃ, সাইন-আপ করার সময় তো এত কিছু মাথায় আসেনি, তাছাড়া জব-ডেস্ক্রিপশনে সেরকম বিশদভাবে কিছু বলাও ছিল না। যাক গিয়ে, কপাল ঠুকে চলেই যাওয়া যাক, সেরকম হলে সুপারভাইসারকে বলবে না হয়, উহ, আগে থেকেই এত বেশি বেশি চিন্তা করে না ও! বাতিকগ্রস্ত হয়ে গেল নাকি? দূর দূর! দেখতে দোষের কী? নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে, হারাবার তো কিচ্ছু নেই! গাড়িতে স্টার্ট দেয় নিনা ।
বেশি দূরে নয়, মিনিট পনেরোর মধ্যেই স্কুলটায় পৌঁছে যায় নিনা । খুব সুন্দর টানা একতলা বিল্ডিং, সামনেই রংবেরঙের ফুলের কেয়ারী, বাচ্চাদের খেলার জন্য একটা ছোট্ট লাগোয়া মাঠ, সেখানে একধারে গুটিকয় দোলনা, টিটার-টটার, জাম্পার, স্যান্ড-ক্যাসল, সব রয়েছে । নিনা বিল্ডিং-এর ভিতরে ঢুকে সইসাবুদ করার পর একজন ভদ্রমহিলা এসে ওকে ২২১ নম্বর ঘরে নিয়ে গেলেন |বেশ বড়ো মতন একটা ক্লাসরুম, তিনটি করে চেয়ার আর ডেস্ক সামনে পিছনে দুই সারিতে পাতা, ছেলে মেয়ে মিশিয়ে ছয়জন বাচ্চা’র জায়গা- -চারজন ছেলে আর দুটি মেয়ে | ওদেরকে এক ঝলক দেখে নিনার মনে হলো সকলেরই বয়স নয়-দশের মধ্যেই হবে, যে যার ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে আছে, শুধু একটা লম্বা, রোগা মতো সোনালী চুলের ছেলে কাঁচের জানালার গা ঘেঁষে রাখা একটা উঁচুমতো টানা লম্বা ক্লোসেটের ভিতরে পাতা একটা টেবিলের উপর পিছন ফিরে বসে মাথা নিচু করে কী যেন করছে আর মাঝে মাঝে অস্ফুটে কিছু একটা বলছে । অদ্ভুত তো, সবাই যে যার জায়গায় বসে আছে, ও ওখানে কেন? একটু অবাকই হলো নিনা ।
ক্লাস টিচার মিসেস স্মিথ একজন বয়স্ক শ্বেতাঙ্গিনী, তিনি বাচ্চাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নিনাকে ওনার টেবিলের কাছে ডেকে নিলেন । নিনা হেসে বাচ্চাদেরকে নিজের নাম, পরিচয় বলল | ও লক্ষ করল, পড়ুয়াদের মধ্যে তেমন কোনো হেলদোল হল না, যে যা করছিল, সেটাতেই ব্যস্ত থাকল, দু-একজন নিনার দিকে চকিতের জন্য চোখ ফেরাল বটে, কিন্তু নিনা ঠিক বুঝতে পারল না, ওরা ওকেই দেখল নাকি পাশে দাঁড়ানো মিসেস স্মিথকে ।
মিসেস স্মিথ এবার বাচ্চাদের নিজেদের নাম একেক করে বলতে বললেন, দু-চারবার অনুরোধ উপরোধের পর ওরা নাম বলল বটে, কিন্তু নিনা শুধু মেয়ে দুজনের নামই বুঝতে পারল-রোজা আর কেলি, বাকিদের জড়ানো গলায় বলা শব্দগুলো থেকে সে কিছুই উদ্ধার করতে পারল না । খুব বাঁচোয়া, মিসেস স্মিথ ওদের বলা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আরেকবার করে ওদের নামগুলো উচ্চারণ করছিলেন । নিনা মনে মনে ছেলেদের নামগুলো ঝালিয়ে নিল জশুয়া, কেলেব, আর ডেভিন । আচ্ছা, ক্লোসেটের ভিতরে বসা ছেলেটার নাম তো জানা হলো না । ওর সাথে কি পরে পরিচয় হবে? কে জানে! কিন্তু জেনেই বা কী হাতিঘোড়া হবে? ওরা তো নিনাকে পাত্তাই দিচ্ছে না!
নিনার চকমকে হাসিটা বোধহয় এখন একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, মিসেস স্মিথ ওর হাতের উপর আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বললেন, 'তুমি নতুন তো,কদিন গেলেই দেখবে ওরা তোমার কাছে আসার চেষ্টা করবে, ওদের রিসেপশনটা ঠিক আর পাঁচটা বাচ্চার মতো নয়, কিন্তু আমি বলছি, ওরা তোমায় ওদের মতো করে লক্ষ করেছে, যাও না, যাও, ওদের ডেস্কের কাছে গিয়ে দেখো ওরা কে কী করছে ।'
ঘরে আরো দুজন সাহায্যকারী ছিল- জো আর লেক্সী, ওরা বাচ্চাদের জলখাবার সাজাচ্ছিল, নিনার মনে হলো, এই সুযোগে ছেলেমেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে । নিনা একজন একজন করে বাচ্চাদের ডেস্ক-লাগোয়া টিচারের চেয়ারটায় গিয়ে বসল, ওদের সাথে 'ভাব জমাবার চেষ্টা করল । হ্যাঁ, এবার ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, নিনার সাথে ওরা হাই-ফাইভ' করল, কেউ কেউ এক চিলতে হাসিও উপহার দিল । নিনা লক্ষ করছিল ওদের সকলের মধ্যেই একটা ব্যাপারে মিল আছে, একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করে ওরা: কেউ ক্রমাগত দুলে চলেছে, কেউ ক্রমাগত মাথা নিচু করে নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো একইভাবে বারংবার নেড়ে চলেছে, একজন তো আবার মিনিট পাঁচেক পর পরই উত্তেজিতভাবে চেয়ার থেকে টুকুস করে উঠে দাঁড়াচ্ছে আর বিচিত্র আওয়াজ করে দু-চারটে হাই-জাম্প গোছের লম্ফঝম্প দিয়ে নিচ্ছে, কেউ বা মাথা নেড়ে নেড়ে ক্রমাগত জড়িয়ে জড়িয়ে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বলে চলেছে। মজার ব্যাপার, ওরা প্রত্যেকেই ওদের নিজস্ব পৌনঃপুনিক ব্যবহারে এতটাই অভ্যস্ত এবং স্বচ্ছন্দ যে, সেখান থেকে বের করে এনে অন্য কিছু করানোর চেষ্টাটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হচ্ছিল - সে লেখাপড়াই হোক, অথবা গানবাজনা বা আঁকাআঁকি। ‘এই যে ম্যাডাম, আপনি একটা ঘটিরাম’ - নিজেকে নিজে মুখ ভ্যাংচাল নিনা।
আচ্ছা, ক্লোসেটে বসে থাকা ফিনফিনে সোনালী-চুলের ওই ছেলেটার কি নাম? ও কি ওর ডেস্কে ফেরত আসবে না? জিজ্ঞেস করবে নাকি মিসেস স্মিথকে? ভাবতে ভাবতেই দেখল, মিসেস স্মিথ ক্লোসেটের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন, নিনা অমনি জিজ্ঞেস করল, ‘মে আই কাম উইথ ইউ, মিসেস স্মিথ?’
‘সিওর, এন্ড প্লিস কল মি টিশা’-ঘাড় ঘুরিয়ে এক টুকরো মিষ্টি হেসে বললেন তিনি। নিনার খুব ভাল লাগল মিসেস স্মিথের এই কাছে টেনে নেওয়ার ভঙ্গিটি, ও টিশার পিছু পিছু চলল।
‘হাউ আর ইউ রুডি? ইট'স টাইম টু জয়েন দা ক্লাস, প্লিস গো ব্যাক টু ইওর সিট্’- টিশা ছেলেটাকে ডাকলেন, কিন্তু সে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। টিশা এবার নিনাকে সামনে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন, ‘লুক হিয়ার রুডি, উই হ্যাভ এ নিউ পারসন ইন আওয়ার রুম’ – ধীরে ধীরে এবার মাথা তুলল ছেলেটা, ওর সমুদ্রের মতো নীল দুটো আয়ত চোখের শ্লথ দৃষ্টি নিনার দিকে বেশ কয়েক পলের জন্য স্থির হলো, তারপর আস্তে করে সে বলে উঠল ‘নিনা’, আর পরমুহূর্তেই মাথা নিচু করে ডুবে গেল আবার নিজের জগতে। রুডির মুখে নিজের নামটা শুনে পুরো চমকে উঠল নিনা, বুকের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল, নিয়মের শিকলে আষ্টেপিষ্টে আগলানো রোবটের মতো যে জীবন সে দিনরাত যাপন করে, সেগুলো কেমন তুচ্ছ হয়ে গেল। কত দিনের লুকিয়ে থাকা একটা গভীর দীঘল শ্বাস বুকের খাঁচা ভেদ করে বাইরে বেরিয়েই কেমন রুমঝুম পায়ে নাচ করা কিশোরীর মতো হালকা হাওয়া হয়ে ওর চারপাশেই ঘুরঘুর করতে লাগল; দিয়া মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ছিল- পরম পাওয়ার আনন্দে না অবিশ্বাসে? -- কে জানে– সেই ফুরফুরে বাতাস মিহি পরশে খুলিয়ে দিল ওর আঁখিপল্লব। ছেলেটা তাহলে ক্লাসঘরের সব কথা-বার্তাই শুনেছে, আশ্চর্য তো!
টিশাও হেসে উঠলেন, ‘ভেরি গুড লিসেনিং রুডি, তুমি আজকে সারাটা দিন নিনা-র সঙ্গেই কাটাবে, লেখাপড়া, গান-বাজনা, খেলাধুলো সবেতে নিনা আজ তোমায় সাহায্য করবে, ওর কথা ঠিকঠাক শুনবে কিন্তু, তবেই তো নিনার ভালো লাগবে, আর তাহলেই তো পরের দিন আবার আসবে তোমার কাছে। জানো তো নিনা, আমাদের রুডি পিয়ানো বাজাতে কিন্তু দারুণ ওস্তাদ।আজ রুডির সাথে লাস্ট পিরিয়ডের মিউসিক ক্লাসে গেলে তুমি নিজের চোখেই আবিষ্কার করবে সেটা।’
নিনা ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না, টিশার এই কথাগুলো রুডি শুনল কিনা। রুডির সব মনোযোগ তার হাতে ধরা একটা ছোট্ট স্টাফড খেলনা সাদা হাঁসের উপরই ন্যস্ত, সেটাকে সে হাতের মুঠোতে পুরে রেখেছে, মাঝে মাঝেই মুঠো খুলে পরখ করে দেখছে, সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা, আর অস্ফুটে কী সব বিড়বিড়িয়ে বলছে। নিনা কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, অবাক হওয়ার পালা এবার ওর, পরম মমতায় রুডি হাঁসটার গায়ে হাত বুলাচ্ছে, আর ডাকছে ‘আফ্লাক, আফ্লাক’।
নিনা রুডির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আফ্লাক টা কী সুন্দর দেখতে, তুমি বুঝি ওকে খুব ভালোবাসো রুডি?’ কে জানে কী বুঝল রুডি, সে মাথা নিচুই করে থাকল।
‘জানো তো আমারও একটা ওরম আছে,’ তবে তোমারটার মতো অত মিষ্টি নয় মোটেই!’
এবার কিন্তু চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল রুডি, যদিও সে দৃষ্টি ঠিক কোথায় নিবিষ্ট, তা ঠাওর করতে পারে না নিনা, কিন্তু তার শেষ কথায় রুডির মুখটা যে, হাসি হাসি হয়ে গিয়েছে, সেটা মোটেই নিনার দৃষ্টি এড়াল না।
‘এসো রুডি, আমরা ডেস্কে ফিরে যাই’
রুডি কিন্তু এবার বিনা বাক্যব্যয়ে ক্লোসেট থেকে নেমে এল, নিনার হাতটা নিজে থেকেই ধরল, এবং গুটি গুটি পায়ে নিজের ডেস্কে এসে চুপটি করে বসল। নিনার বুক উত্তেজনায় ধুকপুক করছে, শুনেছে ওর কথা, শুনেছে রুডি। আজ সকালে এ এক দারুণ পাওয়া ওর। মিসেস স্মিথও বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছেন, রুডিকে ক্লোসেট থেকে ডেস্কে এনে বসানোটা একটা চ্যালেন্জিং কাজ বটে!
সেই ওদের প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ, নিনা আর রুডির।
এরপর সারাটা দিন ২২১ ঘর, জিমনেসিয়াম, আর্ট, আর ক্যাফেটেরিয়া-র মধ্যে স্পেশাল-এডুকেশনের ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে ঠিকঠাক একটিভিটি করাতে করাতে জো আর লেক্সীর সাথে সাথে নিনারও একদম হাঁপ ধরে গেল; এখন মিউসিক ক্লাসটা উৎরালেই কেল্লা ফতে; আজকের এসাইনমেন্ট ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যাবে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিনা। কিন্তু দিনের সবথেকে বড়ো চমকটা বোধয় ওর জন্য এতক্ষণ তোলা ছিল।
পিয়ানোর সামনে বসে এইমুহূর্তে সুরের বিচিত্র ঝড় তুলেছে যে ছেলেটা, সে কে? রুডি?
দুর্বোধ্য আওয়াজে কিছু একটা বলতে বলতে একশবার যে খেই হারিয়ে ফেলে, খুব সাধারণ কোনো নির্দেশ পালন করায় ও যার প্রবল অনীহা, সামান্য একটা কাজ ও যে ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ নয়, সেই রুডি? কিন্তু এ তো এখন এক সম্পূর্ণ অন্য মানুষ!
নিনা অবাক হয়ে লক্ষ করে, কী সাবলীলভাবে রুডির আঙ্গুলগুলো নেচে বেড়াচ্ছে পিয়ানোর কিবোর্ডের উপর, সুরের তালে তালে রুডি হাসছে, মাথা দোলাচ্ছে, আর ওর সোনালী চুলগুলো পাল্লা দিয়ে নেচে নেচে উঠছে। কী অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য! ভালোলাগায় বুঁদ হয়ে যায় নিনা, ওর চোখ মুদে আসছে সংগীতের মূর্ছনায়।
‘কি মিস নিনা, কেমন লাগছে আমাদের রুডির বাজনা?’ মিটিমিটি হাসছেন মিউসিক টিচার দীর্ঘদেহী সৌম্যকান্তি মিস্টার রবার্ট গিলফোর্ড?
‘কী করে সম্ভব হলো এসব মিস্টার গিলফোর্ড?’ প্রশ্ন করে নিনা।
মিস্টার গিলফোর্ড একটু হেসে দুই হাত প্রসারিত করেন আকাশপানে। তারপর বলেন, ‘স্বরক্ষেপ চেনার, সুর অন্তস্থ করার এবং সংগীতের অন্তর্নিহিত আবেগকে নিজের ভিতরে অনুভব করার একটা সহজাত ক্ষমতা নিয়েই রুডি জন্মেছে। God works in mysterious ways’ - ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান গিলফোর্ডের চোখে কেমন এক মেদুরতা।
‘কিন্তু এতসব শেখালেন কীভাবে ওকে আপনি?’
‘আমি বারোটা কর্ড ছাড়া রুডিকে কিন্তু আর বিশেষ কিছুই শিখাইনি,’ গিলফোর্ড বলেন।
মানুষটা কি জাদু জানে? নিনার চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছোঁয়া- ‘স্কেল, ইন্টারভ্যাল, পিয়ানোর খটোমটো ব্যাকরণ? কিচ্ছু না?’
‘নাহ, একদমই না,’ মাথা নাড়েন গিলফোর্ড। ‘আমার মনে হয়েছে যে ওসবের বোঝায় ওকে জর্জরিত করে তুললে, ওর নিজস্ব ক্ষমতাগুলোই হয়তো চাপা পড়ে যাবে। আমি বাজিয়েছি, রুডি শুনেছে; একবার নয় বারবার, তারপর ভুল-ঠিক বাজাতে বাজাতে কখন যেন সুরটা ওর বুকের গভীরে একেবারে সেঁধিয়ে গেছে, ব্যস, আমায় আর নতুন ক'রে কোনো নির্দেশ দিতে হয়নি, সদ্য শেখা সুর নিজের ইচ্ছেমতো নাগাড়ে বাজিয়ে গিয়েছে রুডি, দীর্ঘ সময় ধ'রে, অক্লেশে, ক্লান্তিবিহীনভাবে, এইভাবেই দিনে দিনে ওর হাত খুলেছে। পিচ চেনার, সুর মাথায় ধ'রে রাখার এবং পিয়ানোর কিবোর্ডে কোথায় কখন আবেগের মোচড় দিতে হবে, কানে শুনে শুনেই সে সব তুলে নিয়েছে রুডি, সময়কালে তা ঠিকঠাক প্রয়োগও করেছে।
‘কিন্তু ও পিয়ানোর নোটগুলো আত্মস্থ করল কী ভাবে?’
‘হ্যাঁ, একদম শুরুর দিকে সেটা একটু চ্যালেন্জিং ছিল, আমি পিয়ানোর কিবোর্ডের উপর রঙিন স্টিকার-কোটেড নোটগুলো লিখে রাখতাম, ওতে রুডির খুব সুবিধে হয়েছিল।’ মন্ত্রমুগ্ধের মতো গিলফোর্ডের কথাগুলো শুনছিল নিনা।
তারপর বেশ কটা সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, অন্য অনেক কাজের সুযোগ থাকলেও নিনা কিন্তু তা নেয়নি, ও এই কাজটাকেই ধরে রেখেছে। একটু কঠিন লাগলেও কাজটা নিনার কিন্তু খারাপ লাগছে না মোটেই, বরং ভোর হতে না হতেই ২২১ নম্বর ঘরের বাচ্চাগুলো বিশেষ করে ওই সোনালী চুলের সমুদ্র-নীল চোখো রুডি নামের ছেলেটা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে; সেই ডাক অস্বীকার করে এমন সাধ্য কৈ নিনার! আর কী অদ্ভুত! স্কুলে থাকাকালীন রুডির সব দায়িত্বভার এখন থেকে নিনাকেই দিয়েছেন টিশা। কি করে জানলেন উনি নিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা?
রুডির সঙ্গেও নিনার যেন কেমন একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে; এরকম নয় যে, রুডি ওর সব কথা শোনে, কিন্তু নিনা লক্ষ্য করেছে, দিনের শুরুতে আফ্লাককে হাতের মুঠোয় ধ’রে, স্কুলের ব্যাগপত্র সামলে, স্পেশাল-এড-বাস থেকে যখন ছেলেমেয়েরা একেক ক'রে নেমে আসে, তখন ওদের অভ্যর্থনা করার জন্য স্কুল-বিল্ডিঙের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হাসিহাসি মুখগুলোর ভিতর কাউকে উদভ্রান্তের মতো খোঁজে রুডির অস্থির চোখ আর নিনাকে দেখতে পেলেই ও দুটো কেমন শান্ত, নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সকাল ৮-৪৫ থেকে অপরাহ্নের ৩-৪৮ পর্যন্ত সময়টা নেহাত কম নয়, রুডির সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকে নিনা, একটু একটু করে সে বুঝতে চেষ্টা করে রুডির মন-মেজাজের ওঠাপড়া, রুডির হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, কষ্ট-আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা।
চারটে মাস কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, নিনা জানে না। এর মধ্যে বেশ কয়বার ছেলেমেয়েদের ফিরতি বাসের সময় গড়বড় হওয়ায় নিনা আগ বাড়িয়ে নিজেই রুডিকে নর্থভিল গ্রুপ-হোমে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এই যাতায়াতের সূত্রে রুডির যত্নদাত্রী জেমি ডগলাস আর কেস-ম্যানেজার মিস্টার টাইলার গ্রিফিথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়ে গিয়েছে নিনার। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেয়ার-গিভার পঞ্চাশোর্ধ জেমি যেমন অমায়িক তেমনই দয়ালু ভদ্রমহিলা। প্রথম দেখাতেই নিনাকে খুব আপন ক’রে নিয়েছেন। ইদানিং, শনি-রবিবার এলেই, রুডি আর জেমিকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে নিনা। কাজের চাপ না থাকলে, মিস্টার গ্রিফিথও মাঝেসাঝে ওদের সঙ্গী হন। নিনা জানতই না যে, মিস্টার গ্রিফিথও ওরই মতন একজন ফুটবল পাগল মানুষ আর ‘’ডেট্রয়েট লায়নস’’-এর যাকে বলে এক্কেবারে কট্টর সমর্থক। জানাজানি হতেই ওদের দুজনের মধ্যে ভাবসাব গাঢ় হতে আর বেশি দেরি হয়নি; ওরা এখন দুজন দুজনকে নাম ধরে ডাকে আর ওদের মধ্যে আপনি-আজ্ঞের বালাইও দূর হয়েছে। এখন একসঙ্গে হলেই ওদের আলোচনার মূলবস্তু হয়ে দাঁড়ায় রুডির কেস। এরকমই একদিন কথায় কথায় দারুণ কৌতূহল নিয়ে টাইলারের কাছ থেকে শুনতে চায় নিনা রুডির জীবনের আগুপিছু সব ঘটনা। চশমার কাচটা জামার আস্তিনে একটু মুছে নিয়ে টাইলার শুরু করে সেই গল্প।
মাদকাসক্ত শ্বেতাঙ্গিনী পঞ্চদশী ক্লারা হ্যামিলটন, উশৃঙ্খল জীবনযাপনের ফলস্বরূপ ঐরকম একটা কাঁচা বয়সেই অন্তঃস্বত্বা হয়ে পড়ে। জানুয়ারির এক হাড়হিম সন্ধ্যায় সাংঘাতিক পেট-ব্যথা এবং যোনিদ্বার থেকে রক্তস্রাবের সমস্যা নিয়ে ডেট্রয়েটের শহরতলীর এক হাসপাতালে হাজির হয় সে। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে যে, বাথরুমে আছাড় খেয়ে পড়ার ফলে এই বিপত্তি, যাই হোক ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন যে, ক্লারার আসলে প্রসব-বেদনা উঠেছে, অথচ ওর গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স মাত্র ২৮ সপ্তাহ। অবস্থার জটিলতা অনুধাবন ক'রে গাইনোকোলজিস্ট, পেডিয়াট্রিসিয়ানরা প্রমাদ গনলেন। যাই হোক, যমে মানুষে টানাটানি করে ডাক্তারেরা ক্লারার অকালজাত শিশু পুত্রকে পৃথিবীতে আনলেন বটে, কিন্তু শিশুটির অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে, তাকে মায়ের থেকে আলাদা ক’রে, নবজাতক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হলো, আর ওদিকে তার একদিন পরেই হাসপাতাল থেকে রাতের অন্ধকারে নিঃসাড়ে চম্পট দিল ক্লারা। অতঃপর শিশুটি বেশ কয়দিন হাসপাতালেই থেকে যায়। শিশুটির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের এই সমাজসেবী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে এবং শিশুটিকে জেমির হাতে তুলে দেয়। সেই থেকেই জেমির হেফাজতেই শিশুটি গুটিগুটি করে বড়ো হচ্ছিল। শিশুটির লালচে-পারা নাকের কারণে জেমি সোহাগভরে তার নাম রাখে ‘রুডলফ’-সান্তা ক্লসের লাল-নাক রেইন-ডিয়ারের সাথে মিলিয়ে রাখা নাম, দিনে দিনে সেই রুডলফই সংক্ষেপে সকলের কাছে হয়ে যায় রুডি। জেমির যত্নআত্তি সদা সতর্ক দেখভাল সত্ত্বেও রুডি প্রায় প্রায়ই জ্বর সর্দি কাশি পেটখারাপ ইত্যাদিতে ভুগত, ডাক্তাররা বলতেন অকালজাত শিশুরা অনেকেই এমন ধারা হয়ে থাকে, এই নিয়ে জেমির মনে খুব অশান্তি লেগে থাকত।
কিন্তু নিয়তির পরিহাসে সমস্যা এখানেই শেষ হলো না, রুডির যখন প্রায় এগারো মাস তখন জেমি লক্ষ করে যে, রুডি যেন কেমন আলাদা, আর পাঁচটা সমবয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে ওর ভাবভঙ্গীর কেমন যেন একটা তফাৎ রয়েছে। কাছাকাছি জোরে কোনো শব্দ হলেও রুডির কোনো হেলদোল হয় না, সে নিঃশব্দেই ঠায় চেয়ে থাকে কোনো একদিকে, কোনো সাড়াশব্দ করে না, ওর সামনে খেলনা ঝুমঝুমি, বা প্যাঁক্পেঁকে হাঁস নিয়ে নাড়ানাড়ি করলেও মোটেই সেদিকে তাকায় না, লোকেদের দিকে তাকিয়ে হাসে না, ওর নাম ধরে শতেক ডাকলেও সাড়া দেয় না, ওই বয়সের শিশুরা যা সাধারণত করে যেমন তাদের হাত নিয়ে মুখে ঢোকায় বা মুখের উপর হাত এনে খেলা করে, রুডি সেসব কিছুটা করে না। আশ্চর্যের কথা, নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা বারবার তোলা-নামা করানোয় বা শরীরটাকে আগুপিছু দোলানোয় ছেলেটার কিন্তু কোনো ক্লান্তি নেই। জেমির মনটা কেমন কু ডাকতে লাগল।
সে মিস্টার গ্রিফিথকে সব জানাতে, তিনিও একদিন সরেজমিনে দেখতে চলে এলেন এবং গোটা ব্যাপারটাতে তাঁরও বেশ খটকা লাগল - এই বয়সের বাচ্চারা কথা বলার জন্য বুড়বুড়ি কাটে, চোখে চোখ রেখে আদর আবেগ জানায়, কিন্তু রুডির ক্ষেত্রে সেসবের নামগন্ধও নেই, সে শুধু দুলেদুলে নিজের আঙুলের নড়াচড়া দেখতেই মগ্ন। ‘তারপর?’ —উৎকণ্ঠায় নিনার হৃদপিন্ডটা বুঝি স্তব্ধই হয়ে যাবে এবার! ‘তারপর আর কি?’ -- মাথার চুলে সামান্য আঙ্গুল চালিয়ে নিতে নিতে বলে টাইলার, ‘বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নানারকম পরীক্ষা করে জানালেন, শুধু বাইরে থেকে দেখতেই দুবলা পাতলা নয়, রুডির মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মেও অনেক খামতি রয়েছে, রুডি একজন প্রতিবন্ধী, প্রায়শই নানা রকমের স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হবে আর সাধারণত এদের আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, বড়োজোর ৩৯ থেকে ৪০ বছর।’
‘ওহ,’ একটা আর্ত-চিৎকার অজান্তেই বেরিয়ে আসে নিনার বুকের ভিতর থেকে, মুখে হাত চেপে উদ্গত অশ্রুকে সম্বরণ করার চেষ্টা করে সে, তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে স্থাণুবৎ বসে থাকে , শেষে থেমে থেমে বলে, ‘টাইলার অনেক দিন ধরেই একটা কথা বলি বলি করে তোমায় বলে উঠতে পারিনি, আমি রুডিকে দত্তক নিতে চাই।’
কথাটা শুনে এবার চমকাবার পালা বুঝি টাইলারের, নিনার চোখে চোখ রেখে সে শুধায়, ‘সব জানার পরেও? কত বড়ো ঝুঁকি আছে এতে, সে কথা নিশ্চয়ই তোমাকে আর বলে দিতে হবে না। ভালো করে ভেবে দেখেছ তো, নিনা?’
নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় নিনা, ওর দুচোখে প্রত্যয়ের ঝলক।
‘আচ্ছা বেশ, তবু একবার বলো কেন নিতে চাও, এরকম একটা ঝক্কি? শখ? ক্ষণিকের আবেগ? নাকি লোককে দেখাবার জন্য?’ টাইলারের কণ্ঠে যেন কী এক চ্যালেঞ্জ।
সামান্য ক্ষয়াটে হাসি হাসে নিনা, ‘তিনটের কোনোটাই নয়। জানো টাইলার, রুডি যখন দুরন্ত বেগে ওর দুচাকার বাইসাইকেল ছোটায় আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ওর সোনালী চুলগুলো হাওয়ায় ওড়ে, ঠোঁটে ওর তখন দিগ্বিজয়ের হাসি, আমি দেখি আর দেখি, জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করি, জীবনের উজ্জ্বল আলোয় আমার চোখ পুরো ধাঁধিয়ে যায়, আমার রুদ্ধপথ জীবন যেন তখন সাগরের দিশা পায়।’
টাইলার মাথা দোলায় - ‘রুডির মধ্যে কী যেন একটা আছে, জেমিও এমনটাই কিছু বলে।'
‘টাইলার, এ ক'মাসে আমাকে তো অনেকটাই কাছ থেকে দেখলে তুমি, আমার পিছনের জীবনটার কথা তোমায় সবই বলেছি, তবু কিছু কথা শুধুই অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, হ্যাঁ, আমারও একটা স্বার্থ আছে বৈকি এতে, রুডিকে অবলম্বন করে আমি আবার বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, জীবনটাকে আরেকবার নতুন করে ঝিকিমিকি আঁকা রঙিন স্বপ্নে সাজিয়ে তুলতে চাই। মানুষ হিসাবে কি সেই অধিকারটুকু নেই আমার?’
‘নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তুমি একা মানুষ, এমনিতেই টিকে থাকার জন্য তোমাকে অহরহ লড়াই করতে হচ্ছে, এর উপর আবার এক অটিস্টিক শিশুর মা হওয়া? পারবে তো ঠিকঠাক রুডিকে সামলাতে? এদেরকে নিয়ে হ্যাপা তো কম নয়! টাইলার যেন নিনাকে সবরকমে বাজিয়ে নিতে চায় ।
‘টাইলার আমি কথা দিতে পারি তোমায় যে, আমার প্রাণ থাকতে রুডির গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেব না, আমি ওকে মনের মতন করে বড়ো করে তুলতে চাই, তুমি কি আমায় একটু সাহায্য করবে না বন্ধু?’ টাইলারের হাতটা জড়িয়ে ধরে নিনা।
‘অবশ্যই, বলো কী করতে হবে।’
‘শুনেছি দত্তক নেওয়া একটা দারুণ ঝামেলার ব্যাপার, তার উপর গ্রুপ হোম থেকে একটি শিশুকে দত্তক নেওয়া, বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ত, প্রচুর কাগজপত্র এবং হাজারো আইনি মারপ্যাঁচ রয়েছে। কতরকমের কমিটি-টমিটি, মিটিং নাকি বসে, আমি তো বুঝতে পারছি না কীভাবে এগোব, প্রক্রিয়া চলাকালীন তুমি সঙ্গে থেকো প্লিস টাইলার।’
‘শোনো নিনা, এইসব আইন-কানুন, কমিটি এ সব কিছুরই একটাই উদ্দেশ্য: তুমি রুডির বড়ো হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং যত্ন প্রদান করতে পারবে কিনা সেটা নির্ধারণ করা। পারিবারিক পটভূমি মূল্যায়ন কমিটির কাছে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থীপদ সমর্থন করব, কারণ তোমার সাথে কথা বলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, রুডি তোমার কাছে খুব ভালো থাকবে, নিরাপদ থাকবে, সুস্থ থাকবে; ওর সবরকম চাহিদা পূরণ করার সাধ এবং সাধ্য দুইই তোমার আছে, আর এটাই মোদ্দা কথা, বাকি সব কাগুজে নিয়মকানুন নিয়ে তুমি চিন্তা করো না, ওগুলো নেহাতই লৌকিকতা।’
নিনার চোখমুখ ভেসে যায় কৃতজ্ঞতা র অশ্রুধারায়, টাইলার ওর পিঠ চাপড়ে বলে, ‘আই রেস্পেক্ট ইয়োর কারেজ নিনা, ডোন'ট ওরি, এভরিথিং উইল বি অলরাইট। তবে, তুমি একবার জেমির সাথে কথা বলে নাও, ধাই-মায়ের মতো এতদিন তো ওই রুডিকে কোলেকাঁখে ক’রে বড়ো করল, ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে ওর বুক ফেটে যাবে, তবে ওর বয়স ও তো অনেকটাই হয়েছে, এখন আর আগের মতো অত খাটাখাটনি করতে পারে না।’
তা, সে নিয়ে অবশ্য কোনোই সমস্যা হলো না, জেমি খুব খুশি হলো নিনার প্রস্তাব শুনে, ছলোছলো চোখে নিনার হাত দুটি ধরে শুধু বলল, ‘আমি কিন্তু রুডিকে দেখতে মাঝে মাঝেই হানা দেব তোমার ডেরায়, কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না,’ বলেই হাহা ক'রে হেসে ওঠে সে, নিনাও তার সাথে পাল্লা দিয়ে হেসে ওঠে।
এরপর সকলের সহযোগিতায় খুব তাড়াতাড়ি রুডিকে দত্তক নেওয়ার কাজটা সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেল, নিনার মাথা থেকে একটা বিশাল বোঝা নেমে গেছে, ও এখন মনের সুখে রুডির জন্য বেছে রাখা ঘরটাকে মনের মতো করে সাজানোয় মেতে উঠল। সেদিন ‘পেটকো’ থেকে খাঁচা সমেত দুটো উজ্জ্বল হলুদ রঙের ক্যানারি কিনে আনল – একটা ছেলে, আরেকটা মেয়ে। সারাদিন দুটিতে মিলে খুনসুটি ক'রে বাড়ি একদম মাতিয়ে রাখে; যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি ওদের গান। রুডির নিশ্চয়ই খুব পছন্দ হবে, খেলনা আফ্লাককেই যা ভালোবাসে ছেলেটা, হয়ত ক্যানারি দুটোর সুরে সুর মিলিয়ে গলাই মিলিয়ে বসবে রুডি, কী যে অলৌকিক একটা ব্যাপার ঘটবে তখন! নিনা কোনোদিন ভাবতেও পারেনি যে, ওর নষ্ট জীবনের আবিলতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে এমন সুন্দর দিনও আসতে পারে!
যেদিন রুডিকে বাড়িতে নিয়ে আসতে যাবে, তার আগের রাতে উত্তেজনায় মোটেই ঘুম হল না নিনার, বসার ঘরের রকিং চেয়ারে অন্ধকারে বসে দুলতে দুলতে সে নানা কথা ভাবতে লাগল। আজ মা বেঁচে থাকলে রুডিকে নিয়ে কত না আমোদ-আহ্লাদ করত, নাতিকে প্রতিদিন পঞ্চব্যঞ্জনে খাওয়াবার তাল করত, অন্যথায় তাঁর মনই ভরত না। মনখারাপের মেঘকে দুই হাতে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ে নিনা, অনেক কাজ প'ড়ে আছে, রুডি আসার আগেই সেগুলো ঝটপট সারতে হবে, এরপর তো সকাল সন্ধ্যা রুডির জন্যই ব্যস্ত থাকতে হবে। ভাবতেই নিনার মনে আনন্দের শিহরণ জাগে। এরই মধ্যে টুক ক'রে বাইরেটায় একটু উঁকি মারতেই বিহ্বল হয়ে যায় নিনা। ওর মনে হলো যেন স্বর্গটাই নেমে এসেছে ওর ছোট্ট ব্যালকনিতে। দেয়াল বেয়ে ওঠা লতানো ‘হানিসাকল’- এর গাছে যেন সব ফুল এক সাথে ফুটে গেছে। রাতের আকাশের তারাগুলো হুড়মুড়িয়ে ব্যালকনিতে ঢুকে পড়েছে আর নিনার দিকে তাকিয়ে ওরা মিটমিটিয়ে হাসছে। নতমস্তকে প্রার্থনা করে নিনা সেই অসীম মহাকালের কাছে, ওর আর রুডির সম্মিলিত জীবন যেন খুঁজে পায় এই নশ্বর প্রাণের প্রকৃত অর্থ, অমৃতের সন্ধান।
এর পরের দিনগুলো ঝড়ের মতোই কেটে গেছে, একদিকে রুডির মতো বিশেষ চাহিদার বাচ্চার পরবরিশ, অন্যদিকে রুজিরোজগারের ধান্দা, আর দৈনন্দিন জীবনের সাত সতেরো ঝামেলা- এই সবের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে রাখতে রুডিকে আরো বেশি করে বুঝতে শিখেছে নিনা, আর রুডিও যেন একটু একটু করে নিনার আরেকটু কাছে এগিয়ে এসেছে, নিনার চোখের ভাষা অনেকটাই ধরতে পারে সে এখন।
এখন সোম থেকে শুক্রবার রুডিকে নিয়ে সকালবেলায় ২২১ নম্বর ঘরে চলে আসে নিনা, সারাদিন ওখানে বাচ্চাদের সাথে কাজ ক'রে বিকেল বেলায় রুডিকে বগলদাবা করেই ঘরে ফেরে সে। শনি-রবিতে ওদের মা-ব্যাটার রুটিনটা একটু আলাদা। সেদিন দুজনেই বেশ খানিকটা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে ওরা, অন্যদিনের চেয়ে ব্রেকফাস্টের বহরও যেমন একটু বেশি থাকে, তেমনই তাতে থাকে বিশিষ্টতার ছোঁয়া। সেটা শেষ হলেই ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ে ফুর্তি করতে – কোনোদিন চাক-ই-চিজ, কোনোদিন রেইনবো লীগ বোলিং প্লেস, কোনোদিন বা জ্যাপ জোনে - তারপর শুধু ফান আর ফান। কোথা দিয়ে যে রবিবারের রাতটা ফুস করে’ কেটে যায়, ভোর হতেই আরেকটা সপ্তাহ হুড়মুড়িয়ে দরোজায় এসে কড়া খটখটায়।
নিনার খুব মনে আছে, সেদিনটা ছিল তেমনই এক ব্যস্ত সোমবার, রুডিকে নিয়ে মিউসিক ক্লাসে সবে পা দিয়েছে নিনা,
‘আজকে একটা চমৎকার খবর আছে,’ এগিয়ে এসে সোৎসাহে বললেন মিস্টার গিলফোর্ড।
‘আচ্ছা, কী খবর শুনি?’
‘আসছে মাসে ইন্টারস্কুল মিউসিক প্রতিযোগিতা হবে স্কাইলাইন হাইস্কুলে, আজকেই পেয়েছি ইমেইল-টা। ভাবছিলাম আমাদের গ্ৰুপ থেকে রুডির নামটা দেব পার্টিসিপ্যান্ট হিসাবে, ও কিন্তু ভালো বাজাচ্ছে আজকাল, তুমি কী বলো?’
‘অবশ্যই,’ -- নিনা শুনেই লাফিয়ে ওঠে, উত্তেজনায় গিলফোর্ডের হাতটা চেপে ধরে সে। ‘এর থেকে ভালো সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে মিস্টার গিলফোর্ড, আপনি যখন বলছেন, রুডি তখন নিশ্চয়ই বাজাবে সেখানে। আর কে কে যাচ্ছে এই স্কুল থেকে?’ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে নিনা।
‘আরও চার-পাঁচজন তো বটেই, আজকেই লিস্ট ফাইনাল হয়ে যাবে, নিনার উত্তেজনা গিলফোর্ডকেও স্পর্শ করে।
‘রুডিকে কি আজই বলবেন?’
‘হ্যাঁ, দেখি ও কিরকম রিয়্যাক্ট করে, তুমিও থেকো কিন্তু!’
নিনা কি আর তা কারুর বলার অপেক্ষায় থাকে? কিন্তু এখন থেকেই ওর বেশ নার্ভাস লাগছে।
রুডির কাছে ব্যাপারটা সব আস্তে আস্তে খুলে বললেন গিলফোর্ড, প্রতিযোগিতার বিষয়টা রুডি কতটা বুঝল কে জানে, তবে পিয়ানো বাজাতে হবে শুনেই ওর নীল চোখে উৎসাহ ঝলকে উঠল।
আসলে ওতে তো রুডির কখনোই ‘না’ নেই, বিশেষত যদি তা হয় গিলফোর্ডের কাছে বসে বাজানোর সুযোগ। সুরের বাঁধন বড়োই বিচিত্র! কখন যে কাকে কার কাছে টেনে আনে! দুটিতে মিলেছে ভালো, রুডি আর গিলফোর্ডকে দেখতে দেখতে ভাবছিল নিনা।
‘নিনা আমি রুডির জন্য বিথোভেনের "ফুর এলিস" আর ডেবুসির "ক্লেয়ার ডি লুন" এই দুটো বাজনাই বেছে নিয়েছি, তুমি কী বলো?’ গিলফোর্ডের প্রশ্নে নিনার ভাবনায় ছেদ পড়ে।
‘আমি আবার কী বলব? আমি কি ছাই পিয়ানোর কিছু জানি? বাজিয়েছি নাকি কোনো জন্মে?’
‘না, তাও!’
‘না, না আমি কিচ্ছু জানি না,’
ঠিক আছে, আমরা যখন বাজাব, শুনে বোলো কেমন লাগছ, তুমিই এখন আমাদের একমাত্র শ্রোতা-প্রতিনিধি।’
‘ঠিক ঠিক, হাসতে হাসতে বলে নিনা।’
‘তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুটোই রুডির খুব পছন্দ হবে। আমি তো আগেও কাজ করেছি রুডির মতো বাচ্চাদের সঙ্গে, দেখেছি এগুলো ওদের খুব পছন্দের।’
‘সত্যি? দারুণ তো, কিন্তু, কেন পছন্দ করে ওরা?’ নিনার খুব কৌতূহল হচ্ছে।
‘প্রথম বাজনাটা মানে ‘ফুর এলিস’ ওরা পছন্দ করে কারণ ওটা সহজ অথচ সুরের দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক, আর এটার কাঠামোর মধ্যে পুনরাবৃত্তির একটা ব্যাপার আছে যা ওদের জন্য খুব প্রশান্তিদায়ক; জায়গায় জায়গায় সুরের বেশ ওঠা-পড়াও আছে, তাই একই সঙ্গে বাজনাটা উদ্দীপকও বটে।’
‘আচ্ছা, আর অন্যটা মানে ‘ডেবুসি’র কম্পোজিশনটা?’
‘হ্যাঁ, ওটাও অটিস্টিক বাচ্চাদের আকর্ষণ করে, ‘ক্লেয়ার ডি লুন’-এর মৃদু, বয়ে যাওয়া মিষ্টি সুর রুডিকে কেমন ভাবুক ক’রে তোলে, নিজের চোখেই দেখবে!’
মিস্টার গিলফোর্ড আপনাকে যে কী ব’লে ধন্যবাদ জানাব, চলুন না, আমরা সকলে মিলে একদিন ডেট্রয়েট সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা দেখে আসি!
আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে দেখো রুডি’র কনসার্টটা কীভাবে কী উতরোয়! তারপর আর দিন তো পড়েই আছে!’ লাজুক চোখে কথাগুলো বলেন গিলফোর্ড।
এরপর প্রায় এক মাস ধ'রে স্কুল থেকে ফেরার পর নিনা-রুডির জীবনপাতের নিয়মগুলো একটু বদলে গেল! প্রতি সন্ধেতেই গিলফোর্ড স্কুল-ফেরত চলে আসেন নিনার বাড়িতে, শুরু হয়ে যায় গুরু-শিষ্যের পিয়ানোর বাজনদারী। গিলফোর্ড প্রথমে পুরো অংশটা রুডিকে বাজিয়ে শোনান, তারপর আবার ভেঙে ভেঙে টুকরো ক'রে বাজান। সবশেষে রুডিকে নিয়ে আঙুলে আঙ্গুল রেখে সেই ছোট ছোট অংশগুলো একসাথে দুজনে প্র্যাকটিস করেন। টুংটাং মিষ্টি আওয়াজে মেতে ওঠে নিনার ঘরদুয়ার, নিনা ওর রসুইঘরে ব্যস্ত হাতে ঠুংঠাং করে, কখনো বা ফুলগাছের খিদমত করে, আবার কখনো বা চোখ বন্ধ ক'রে সুরের ঝর্ণায় ডুবে যেতে থাকে। ব্যালকনিতে রাখা ক্যানারিগুলোও রুডিদের দেখাদেখি মিঠিমিঠি গান জুড়ে দেয়। প্র্যাকটিস করতে করতে কখন যে একঘন্টা পার হয়ে যায়, তা বাদ্যিকারদের কারুরই খেয়াল থাকে না। নিনা এসে দরজায় উঁকি মারলে, তখন গিলফোর্ড সেদিনের মতো ক্ষান্তি দেন। আজ এখানেই আমাদের সঙ্গে ডিনারটা করে যান না হয় রবার্ট, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, আর আমি কিন্তু খুব একটা খারাপ রান্না করি না, মুখে ঠিকই তুলতে পারবেন।
হোহো করে হেসে ওঠেন মিস্টার গিলফোর্ড, চোখ নিচু করে বলেন, 'আমি জানি তুমি একজন পাকা রাঁধুনি, কিন্তু আজ নয় নিনা, সে আরেকদিন হবে।’ লজ্জা লজ্জা মুখে বলেন, বিপত্নীক গিলফোর্ড।
'ঠিক আছে, তবে এই টিফিন বক্সটা কিন্তু নিতেই হবে, কী আছে ওতে?'
'কিছু না, সামান্য চিকেন পাস্তা'
‘’Oh, I love that,’ উজ্জ্বল চোখে বলেন গিলফোর্ড, জানলে কী করে তুমি?
রন্ধনকারিনীর মনেও তিরতির করে আবেগ ছড়ায়, ছোট্ট একটু কী এক নাম না জানা ভালোলাগা ঘুরঘুর করে নিনার চারপাশে।
নিনা লক্ষ করেছে, প্রথম প্রথম এই মিউসিক পিসগুলোতে রুডির তেমন মন বসছিল না, বা নতুন বলে হয়তো কোনো অসুবিধে হচ্ছিল, হতাশ হয়ে একটু বাদেই বাদেই সে তার চেনা সুরগুলোতে ফিরে যেতে চাইছিল। একদিন তো এমন জিদ ধরল যে নিনা বেদম ঘাবড়ে গেছিল; পারবে কি রুডি কনসার্টের জন্য তৈরি হয়ে উঠতে? কিন্তু গিলফোর্ড মোটেই দমে যাননি, রুডিকে বললেন, আচ্ছা আজ যা তোমার খুশি তাই বাজাও, রুডি কিন্তু একটু বাদেই লাইনে চলে এসেছিল, একা একা বাজানোয় যে একটুও মজা নেই, সেটা সে বুঝতে পেরেছিল। এইরকমই, গিলফোর্ড কখনো পরম ধৈর্যের সাথে বুঝিয়েছেন, দীর্ঘ অপেক্ষা করেছেন, কখনো বা একটু আধটু ছাড়ও দিয়েছেন, কিন্তু, হাল ছেড়ে দেননি কখনোই। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে গোটা ছবিটাই বদলে গেল, দেখা গেল, মোটামুটি দুটো গান ই তুলে নিয়েছে রুডি, এবং বাজাতে পছন্দ ও করছে। এখন শুধু ঝালিয়ে নেওয়ার পালা। ‘আচ্ছা, মিস্টার গিলফোর্ড, রুডি কি অন্যদের মতো মানে স্বাভাবিক বাচ্চাদের মতোই বাজছে? মানে ও কি ওদের সাথে তাল মেলাতে পারবে?’ বেশ কয়েক দিন ধরেই প্রশ্নটা নিনাকে মাঝে মাঝে খোঁচাচ্ছিল।
‘অন্যরা কী ভাবল, অন্যরা কী আশা করল সেটা বড় কথা নয়, নিনা; এমনকি আমি কী মনে করছি তা ও অনেক সময়ই অপ্রাসঙ্গিক, রুডিকে খুঁজে পেতে দাও ওর নিজস্ব বাজন-শৈলী, দেখো, তাতেই ও স্বচ্ছন্দ থাকবে, আর দিনে দিনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে‘- গিলফোর্ডের চোখেমুখে দৃঢ় প্রত্যয়, নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে নিনা।
কনসার্ট আগের সন্ধেতে, প্র্যাকটিসের শুরুতেই গিলফোর্ড নিনাকে ডেকে নিলেন, বললেন, ‘নিনা আজ তুমিই হলে গিয়ে রুডির পিয়ানো বাজনার বিচারক।‘
‘বা রে, তা কী করে হয়? আমি কি পেশাদার সংগীতজ্ঞ নাকি? বড়োজোর একজন ভালো শ্রোতা হতে পারি, তাতে কি আর চলবে?’
‘চলবে মানে, রীতিমতো দৌড়াবে, শ্রোতাদের বিচার কি কম গুরুত্বপূর্ণ নাকি? বাজনদারের লক্ষ্মী তো ওরাই। আর দেখো যা সুন্দর তা সাধারণত সকলের কাছে সেই মান্যতাই পায়, আমার অভিজ্ঞতা তো সেরমটাই বলে। নাও এই টাইমারটা রাখো, সময় লক্ষ্য করতে সুবিধে হবে; আর এই কাগজটা দেখ, প্রতিটি আলাদা আলাদা বিভাগ, সব ঘর করা আছে। নোট এবং ছন্দের সঠিকতা, স্বর নিক্ষেপের নির্ভুলতা, স্বরের গুণমান, বাজাবার কৌশল, বাজনার গতি, সৃজনশীলতা, বাজনদারের অভিব্যক্তি, এবং সর্বোপরি মিউজিকের সামগ্রিক গুণমান, - তুমি নাম্বার দেবে, প্রতি খাতে, যা সমুচিত বোধ করবে।’
নিনা আবারও আপত্তি করতে যাচ্ছিল, গিলফোর্ড ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘তুমি পারবে, তোমার শক্তিতেই তো রুডি এত শক্তিময়।’
রুডি এসে স্টেজে রাখা পিয়ানোর সামনে থিতু হতেই, গিলফোর্ড উঠে দাঁড়ালেন তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ার থেকে, রুডির কাঁধে একটা হাত রেখে মোলায়েম চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘রুডি আজ তুমি শুধু বাজাবে, হ্যাঁ, আমরা শুনব, বলেই উনি স্টেজ পরিত্যাগ ক’রে ব্যাকস্টেজে অপেক্ষারত নিনার পাশে এসে দাঁড়ান।
রুডি কিন্তু চুপটি করে বসে রইল।
'বাজাও রুডি,' নিনা ও এবার স্টেজে উঠে এসে রুডিকে চাপাচাপি করতে থাকল।
কিন্তু রুডি যেন শুনছেই না কিছু, ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরে আসে নিনা।
মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা দুজনে।
‘আপনাকে মিস করছে ও, নিনা জোর দিয়ে বলে।’
‘হুমম, আমিও সেটাই ভাবছি,’ মাথা নাড়েন গিলফোর্ড।
‘কম্পিটিশনে কি আপনাকে এলাউ করা হবে না?’
‘না, না, রুডিদের তো স্পেশাল গ্রূপ, সেখানে কোচ এবং অভিভাবকদের মঞ্চে থাকার অনুমোদন আছে শুধু তাই নয়, প্রয়োজন পড়লে বাজনায় সঙ্গত করারও বিধান আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই, রুডি এতটাই তৈরি যে, ও একাই বাজনাটা সামলাতে পারবে, কারুর কোনোরকম সাহায্যের ওর প্রয়োজন নেই; আসলে আমার উপস্থিতিটা ওর একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, আর আমি সেটাই এই সুযোগে ভাঙতে চাইছিলাম।’
নিনার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়, পার্কিং লটে ছুট্টে গিয়ে গাড়ির ডিকি থেকে রুডির পুরোনো জিনিসপত্র ঘেঁটেঘুঁটে বের করে আফ্লাকটা, সোজা এনে সেটাকে বসিয়ে দেয় রুডির পিয়ানোর মিউসিক স্ট্যান্ডের কাছে, তা দেখে রুডির সে কী হাসি! ‘আফ্লাক আফ্লাক’ বলে হাঁসটাকে খানিক হাতের মুঠোয় জাপ্টে ধরে’ আদর করে, তারপর তাকে কোলের উপর রেখেই সাগ্রহে কিবোর্ডে আঙ্গুল ছোঁয়ায় রুডি।
আর তারপর? পিয়ানোর কিবোর্ডের মধ্যে বোধয় নিজের অন্তরাত্মাকেই খুঁজে পেয়েছে রুডি, ওর ক্ষিপ্র আঙ্গুলগুলো কিবোর্ডে খেলা করে চলেছে মস্তিষ্কের কোন এক অমোঘ নির্দেশে। সমস্ত হলঘরটা সুরের ঝংকারে কেঁপে কেঁপে উঠছে, একনিবিষ্ট হয়ে সংগীতের মূর্ছনা অনুভব করছেন সমাগত শ্রোতারা, চিত্রার্পিতের মতোই স্থির, সমাহিত ওঁদের অবয়বগুলো। আর নিনা? সে তো তার দ্রবীভূত মন আর দুটি মুগ্ধ আঁখি মেলে অনিমিখে চেয়ে থাকে স্টেজের উপর পিয়ানোর সামনে উপবিষ্ট রুডি নামের সেই আশ্চর্য্য আলোকজ্যোতির পানে, যাকে ও গর্ভে ধারণ করেনি, স্তন্যপান করিয়ে বড়ো করে তোলেনি, কিন্তু যার হৃদয়ের কাছে নিজের হৃদয়টি নিঃশর্তভাবে সমর্পন করেছে সে, যে তার বেঁচে থাকার কারণ, ভালো থাকার উপায়, মুক্তির সাধনা।
নিনার চোখের কোলে বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা, এখুনি গড়িয়ে পড়বে কপোল বেয়ে। মোছার চেষ্টাও করে না সে, এ যে পরম সুখের অশ্রু, অমৃতের আস্বাদন।
অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, প্রতিযোগীরা সব একসাথে সার দিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াল, তারপর একে অপরের হাত ধরে ওরা দর্শকদের কুর্নিশ জানাল। চেয়ারে উপবিষ্ট শ্রোতাবন্ধুরাও হাততালি দিতে দিতে আসন ছেড়ে একে একে উঠে দাঁড়াতে থাকলেন, কিন্তু সে হল ছেড়ে চলে যাবার জন্য নয়, অংশগ্রহণকারীদের আরও বেশি করে সাধুবাদ দেওয়ার জন্য। বিশ্বাস হয় না ওদের যে, এই বাজিয়েরা প্রতিবন্ধী।
হলভর্তি লোক উল্লাসে যেন এবার ফেটে পড়ল, মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি আর শিস্ দেত্তয়ার আওয়াজে সেখানে কারুর কান পাতা দায়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি এরই মধ্যে হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন, তাঁর কথা এখনও শেষ হয়নি। তিনি বললেন, ‘প্রত্যেকেই ভালো বাজিয়েছে, সুরের সাধনায় ওরা সকলেই অনন্য, তবু এরই মধ্যে একজনকে বেছে নিতেই হয়, আমরা সর্বসম্মত হয়েছি যে, রুডি তার বাজনাতে যে সুরের জাদু, স্বরক্ষেপের মাধুর্য্য ও মহান শিল্পীসত্তার পরিচয় রেখেছে, তা সাধারণ বিভাগেও দুর্লভ। প্রতিবন্ধী বিভাগে পিয়ানোতে প্রথম হয়েছে রুডি, দ্বিতীয় মারিও আর তৃতীয় ডানা।’ এক দমক দুর্বার উচ্ছ্বাসে আবারও ভেসে যায় হলঘরের শ্রোতামণ্ডলী।
রুডির হাত জড়িয়ে স্টেজ থেকে নেমে এলেন গিলফোর্ড। গুণমুগ্ধ শ্রোতারা ঘিরে আছে ওদের, সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন, তিনি সোজা নিনার দিকে। নিনার কাছে এসে এই প্রথম স্খলিত কণ্ঠে গিলফোর্ড বলে উঠলেন, নিনা, আমার দীর্ঘ শিক্ষক জীবনের সেরা উপহারটি আজ আমার হাতে তুলে দিলে তোমরা, এমন দিনে চলো না, আমরা তিনজনে মিলে কোথাও নিরুদ্দেশে রওয়ান দিই। গিলফোর্ডের চোখে চিকচিক করছে জল, কিন্তু ঠোঁটের কোণে অনির্বচনীয় এক হাসি।
রুডিকে বুকের ভিতর টেনে নিতে নিতে রবার্টের দিকে পলকহীনভাবে চেয়ে থাকে নিনা।
গল্প


গল্প থেকে ক্রাইমঃ ক্রাইম থেকে গল্প
ডাঃ রুদ্রজিৎ পাল
কসবা, কলকাতা
শিল্প, অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটক বা ফ্ল্যাশ ফিকশান, ইত্যাদি কী জীবনকে অনুসরণ করে, নাকি জীবনের নানা ঘটনা শিল্পের আদলে ঘটে? এই তর্ক চিরকালের। যেমন, আমাদের দেশে অনেক মা-বাবা শিশুদের কিছু কিছু বই পড়তে বাধা দেন। তাঁদের যুক্তি হল যে, এইসব বই বেশি পড়লে শিশুরা মারামারি বা ভায়োলেন্স নাকি বেশি শিখবে। অর্থাৎ, এদের কথা অনুযায়ী, মানুষের চরিত্র নাকি ক্রিয়েটিভ ফিকশান থেকেই গড়ে ওঠে। শুধু আমাদের দেশের মা বাবাদের কথা নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে যে বই নিষিদ্ধ হয়, সেন্সরশিপ হয়, সেই বিচারধারার মূল হল মানুষের ব্যবহারের ওপর শিল্পের প্রভাব নিয়ে এই বদ্ধমূল ধারণা। আবার অনেকে বলবেন যে, এই যুক্তি ভুল। বই পড়ে কেউ খুনি বা ডাকাত হয় না। সেটা মানুষের অন্তরের চরিত্রের বা জিনের পূর্বনির্ধারিত বৈশিষ্ট্য। ক্রিয়েটিভ ফিকশান সেই ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শুধুমাত্র কল্পনার রঙ মিশিয়ে কিছু বিনোদনের সৃষ্টি করে, এই মাত্র।
যাই হোক, এই তর্কের কোনও শেষ নেই। আমি তার গভীরে ঢুকতেও চাই না। আজকে আমার আলোচনার বিষয় হল পৃথিবীবিখ্যাত একটি গল্প; সেই গল্প থেকে “অনুপ্রাণিত” হয়ে সংঘটিত একটি অপরাধ এবং আবার, সেই অপরাধ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরেকটি শিল্পের সৃষ্টি।
শার্লক হোমস্। উনবিংশ শতকের শেষভাগে স্কটল্যান্ডে সৃষ্ট এই গোয়েন্দাচরিত্রটি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। ১৮৮৭ এবং ১৮৯০ সালে আর্থার কোনান ডয়েল হোমসকে নিয়ে প্রথম দুটি উপন্যাস লিখলেও প্রথমে এই চরিত্র জনপ্রিয়তা কিন্তু সেরকম পায়নি। শার্লক হোমসের আসল জনপ্রিয়তা শুরু হল যখন জুন, ১৮৯১ থেকে জুন ১৮৯২-এর মধ্যে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের প্রত্যেক সংখ্যায় (জুলাই ১৮৯১ ছাড়া) একটি করে অপূর্ব গোয়েন্দা গল্প ডয়েল প্রকাশ করলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় গল্প ছিল “দ্যা রেড হেডেড লীগ”। শার্লক হোমসের ৫৬টি গল্পের মধ্যে জনপ্রিয়তা এবং সাহিত্যের বিচারে এই গল্পের স্থান খুব উঁচুতে। আজ থেকে ১৩৫ বছর আগে প্রকাশিত এই গল্পের প্লট কিছুটা এখানে বললে “স্পয়লার” দেওয়ার ভয় বোধহয় এখন আর নেই।
লন্ডনের একজন ব্যবসায়ীর সহকারী তাকে একটা অদ্ভুত কাজের খবর দেয়। মাথার চুলের রঙ লাল, এরকম ব্যক্তির খোঁজ করছে একটি সংস্থা। সেই সংস্থায় কাজ পেয়ে যান সেই ব্যক্তি। কিন্তু দুমাস পরে হঠাৎ সেই কাজের অফিস পুরো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উনি বিপন্ন হয়ে হোমসের শরণাপন্ন হন। হোমস খুঁজে বার করেন যে, এই কাজ ছিল ধোঁকা। আসল উদ্দেশ্য ছিল সেই ব্যবসায়ীকে সারাদিন দোকান থেকে সরিয়ে দেওয়া। কারণ সেই সহকারী ছিল একজন নামকাটা অপরাধী এবং সে সেই দোকান থেকে পাশের ব্যাঙ্কে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। যাই হোক, হোমসের বুদ্ধির বলে সেই ডাকাতি রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।
এই গল্প প্রকাশের ঠিক ৮০ বছর পরে লন্ডনে একই কায়দায় একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি ঘটে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য হল, সেই ডাকাতি ঘটে বেকার ষ্ট্রীটে। মানে, কল্পনার সেই শার্লক হোমসের পাড়ায়। অ্যান্টনি গ্যাভিন নামে এক চোর মাটির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে লয়েড ব্যাঙ্কের বেকার স্ট্রিট ব্র্যাঞ্চে ডাকাতির পরিকল্পনা করে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সেই ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে ঢুকে সিন্দুক খালি করা। এর জন্য তারা সেই ব্র্যাঞ্চের দুটো বাড়ি পরে, ১৮৯, বেকার স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট সুদ্ধ দোকানঘর ভাড়া করে। এই ডাকাত দলের একজন, রেগ টাকার, সেই ব্যাঙ্কে একটি লকার ভাড়া করে এবং বার বার লকার খোলার নাম করে সেই সেফ ডিপোজিট ভল্টে ঢুকে সেই ঘরের মাপজোক করে নিতে থাকে। আর অন্যদিকে, সেই ভাড়া নেওয়া দোকানঘরের মেঝে খুঁড়ে টানেল বানানোর কাজ চলতে থাকে। অবশেষে সেই ডাকাতরা ব্যাঙ্কের ভল্টের নীচে এসে উপস্থিত হয়। ঠিক শার্লক হোমসের গল্পের মত, এক শনি-রবিবারে ডাকাতির পরিকল্পনা হয়, কারণ তাহলে
ডাকাতির কথা জানতে জানতেই তিনদিন চলে যাবে। আসল ডাকাতির সময়ে কোনও শার্লক হোমস্ ছিল না। ফলে এই অপরাধীরা পুরো লকার ভেঙ্গে ডাকাতি করেই চম্পট দেয়। সোমবারে এসে ভল্ট খুলে তারপর ডাকাতির কথা জানা গিয়েছিল। এই ডাকাতরা ব্যাঙ্কের সম্পদে হাত দেয়নি। এরা গ্রাহকদের লকার ভেঙেছিল। ফলে, সঠিক যে কত ডাকাতি হয়েছিল, সেটা জানা যায় না। তবে মনে করা হয়, প্রায়, তখনকার হিসাবে, চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ডাকাতি হয়েছিল। আজকের হিসাবে এটা প্রায় ৪ কোটি পাউন্ড। মানে, প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকার ডাকাতি!! এবং সবথেকে মজার ব্যাপার হল, ডাকাতি করে পালানোর আগে একজন ডাকাত দলের সদস্য নাকি সেই ভল্টের দেওয়ালে লিখে রেখে গিয়েছিল---“এবার শার্লক হোমস এই অপরাধের কিনারা করুক!”
লন্ডন পুলিশের তৎপরতায় কিছুদিনের মধ্যেই ডাকাত দলের অনেকে ধরা পড়ে। “মাস্টারমাইন্ড” গ্যাভিন বিচারের সময় জানায় যে, শার্লক হোমসের গল্পটি পড়েই নাকি সে এই বিশেষ ডাকাতি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। অবশ্য এরকম কথা শুনলেই বিশ্বাস করার কারণ নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি লোক এই গল্প পড়ে চলেছে। সবাই কি এটা পড়েই ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরিকল্পনা করছে? ডাকাতি জাতীয় অপরাধ করার জন্য শুধু “অনুপ্রেরণা”ই যথেষ্ট নয়। এর সাথে “মাইন্ডসেট” লাগে, আরও অনেক “লজিস্টিক” সাহায্য লাগে। ফলে, যদি আমরা ধরেও নিই যে এই গল্প সেই অপরাধীকে কিছুটা সাহায্য করেছিল, সেটা খুবই সামান্য। বাকি পুরো অপরাধ সেই দলের কাজ। লেখকের এখানে কোনও দায় নেই। আর আরেকটা কথা হল, সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সুরক্ষিত ভাণ্ডারে ঢুকে চুরি করা কোনও নতুন অপরাধ নয়। যুগ যুগ ধরেই এই ধরণের অপরাধ হয়ে চলেছে। সেই অপরাধী সত্যিই শার্লক হোমসের গল্প পড়ে এই কাজ করেছিলেন নাকি ব্রিটিশ মিডিয়া ঘটনাকে রোম্যান্টিক মোচড় দেওয়ার জন্য এই তথ্য আবিষ্কার করেছিল, সেটাও এখন বলা মুশকিল। যেহেতু বেকার স্ট্রিটে এই ঘটনা ঘটেছিল আর বেকার স্ট্রিটের সাথে শার্লক হোমসের নাম জড়িত, তাই মিডিয়া এই ১৮৯১ সালের গল্পের সূত্র ইচ্ছে করে টেনে এনেছিল—এটাও হতেই পারে। শিল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাধের কথা তো হল। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। আবার আরেক ধাপ এগিয়ে ২০০৮ সালে এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা নিয়ে জেসন স্ট্যাথামের একটি সিনেমা এল---দ্যা ব্যাঙ্ক জব। আপনারা জানেন যে এই ধরণের সিনেমাকে বলা হয় “হাইস্ট মুভি”। বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এই ছায়াছবি। আসলে সেই ১৯৭১ সালের ঘটনাটা কিন্তু পুরো সমাধান হয়নি। কয়েকজনের জেল হলেও বলা হয় যে বেশ কিছু গ্যাং সদস্য সফলভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিশ্চিন্তেই বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন। আবার বলা হয় যে, সেই ব্যাঙ্কের লকারে নাকি ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ রাজ পরিবারের কিছু সদস্যের এমন সব ছবি লুকানো ছিল, যেগুলো প্রকাশ পেলে সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি হত। ফলে, সরকার থেকেই এই মামলার সব ফাইল চেপে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৮ সালের এই সিনেমায় সেরকম কিছু কিছু “কনস্পিরেসি থিওরি” নিয়ে বেশ কিছু দৃশ্য ছিল। রটেন টমেটোস সাইটে এই ছায়াছবির রেটিং প্রায় ৮০%। সুতরাং পরিচালকের বক্তব্য যে দর্শকের পছন্দ হয়েছিল, সেটা বলাই যায়।
আসলে এটা বার বার দেখা গেছে যে খুব দুঃসাহসিক ডাকাতি বা চুরি হলে বৃহত্তর সমাজে কিন্তু সেই অপরাধীদের প্রতি একটা চোরা “হিরো ওয়ারশিপ” এবং সমবেদনা থাকে। এই ১৯৭১ সালের ডাকাতিও সেরকম একটা ঘটনা। সেই ব্যাঙ্কের ভল্ট ছিল লন্ডনের সবথেকে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী পরিবারগুলির গোপন সম্পদ রাখার জায়গা। ফলে সেই ব্যাঙ্কের ভল্টে ডাকাতি যারা করতে পারে, সাধারণ মানুষের সমর্থন যে তাঁদের দিকে কিছুটা থাকবেই, সেটা বোঝাই যায়।
বন্য রাতের ঘুমহীন চুপকথারা
শাশ্বত বোস
মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী

গল্প

জঙ্গলের আগুন রঙা সবুজের ভেতর গোলাপী রঙের হিসহিস শব্দেরা, সারিবদ্ধ গাছেদের খয়েরী রোমকূপ বেয়ে চুপিসারে নেমে এসে, চারপাশ জুড়ে মহাকরুণার মত গাঢ় হয়ে চেপে বসা অন্ধকারটার মাঝে ভবিষ্যতের পথটুকু এঁকে দিয়েছে। যেন ঘুম ঘুম কুয়াশার চাদরের মায়াজাল ভেদ করে, বিভাজিকা স্তনের মত উল্টিয়ে পরে থাকা এই উপবাসী পার্বত্য উপত্যকা জুড়ে কেউ ছেড়ে দিয়েছে কয়েক হাজার হিলহিলে বিষাক্ত সাপ! সর্পিল এই রাস্তার কোন শুরু বা শেষ নেই! শুধু সন্ধ্যের বুক চিরে গলগল করে নামতে থাকা আবছায়া রঙের মনখারাপটা যে কোন পথচারীকে দিক ভ্রষ্ট করে দিতে পারে এই শাল পলাশ সেগুনের জঙ্গলে। এই বারো মাইল ফরেস্টে কাল বিকেলে ঢুকেছে লক্ষ্মীরাণী। উদ্ভ্রান্তের মত খড়কুটো সাঁতরে বেড়ানোর পর আজ দুপুরের ভেজা ভেজা রোদে জঙ্গলে একটা ময়ূর দেখেছে লক্ষ্মী। সেটার পিছু নিয়েছিল ও। কিন্তু পাহাড়ের খাদ বরাবর অতি দ্রুত ময়ূরটা চলে গেছে আরো গভীর জঙ্গলে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে গিয়েও ওটার নাগাল পায়নি লক্ষ্মী। ময়ূরটার ধীর, শান্ত, আলোময় শরীরটা বেয়ে শেষ বিকেলের কমলা রোদটা যেন সোনা হয়ে ঝরে গেছে, ওর ফেলে যাওয়া পথে। লক্ষ্মীর চোখে মায়া লাগে। ময়ূরটার পেছন পেছন জঙ্গলে ঢুকে এসে লক্ষ্মী সেই আওয়াজটা পায়! এই খসখসে শব্দটা বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে চেনে লক্ষী। সিরিশ কেউটের গায়ের ঘষা লেগে শুকনো পাতার গুটিয়ে মুড়িয়ে যাবার শব্দ! সাপটা ভয় পেয়ে পাতাবোনা প্রান্তরের আরো গভীরে ঢুকে যেতে চায়। লোভী চোখে সেদিকে একবার তাকায় লক্ষ্মী। তড়িৎ বেগে ধাবমান কালো কুচকুচে সাপের লেজটার দিকে চোখ পরে ওর! প্রায় পাথরের মত স্থির দৃষ্টিতে আলগা হাতে সাপের লেজটুকুকে ধরে টেনে বের করে নিয়ে আসে। অন্য হাতে সাপের বুকের কাছটা চেপে ধরে নিজের ঝোলায় রাখা চুবড়িতে ভরে ফেলে। সাপটা তখন বিশাল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে লক্ষ্মীর হাতের কব্জিতে ভর দিয়ে। এই সাপের বিষ বাত-বেদনার অব্যর্থ ওষুধ। তাছাড়া এইসব জঙ্গলে আদিবাসী সমাজে যারা সাপের বিষের নেশা করে, তাদের কাছে এর বিষ বেচতে পারলে ভালো দাম পাওয়া যায়। জঙ্গলের ভেতর দূর থেকে একটা জটিল অথচ ভারি অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসে। যেন অবিকল বন মানুষের আওয়াজ! “আও, আও, আওও!” শব্দটাকে লক্ষ্য করে এগোতে থাকে লক্ষ্মী। অলৌকিক কোন প্রেম যেন তখন পেয়ে বসেছে দূরের আকাশমনি গাছের চাক ভাঙা মৌমাছিদের। একটু দূরেই একটা নালার ওপর একটা বাঁশের সেতু আর তার ওপর একটা ছেলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অনবরত মুখ থেকে আওয়াজটা বার করছে। দীর্ঘ একটানা বিচ্ছিরি রকমের আওয়াজটা মসৃণ মোলায়েম এই নির্জনতার পিঠে যেন সচেতন কোন কালের থেকে ছুটে এসে খোলা তীরের মত বিঁধছে! ছেলেটার বয়স বছর দশেক হবে মাথায় ঝুটির মত করে ময়ূরের পালক বেঁধেছে। হয়তো জঙ্গলে দেখা সেই ময়ূরটার পালক! বল্লমের খোঁচায় সেটার দেহ ফালাফালা করে আঁশ ছাড়াবার মত করে ছাড়িয়ে নিয়েছে পালকগুলো। ছেলেটা মাঝে মাঝে সাঁকোর গায়ের বাঁশের বেড়াকে পায়ে করে পেঁচিয়ে ধরে উল্টো হয়ে ঝুলছে। পায়ে পায়ে লক্ষ্মী ছেলেটার দিকে এগিয়ে যায়। ওর চোখে তখন ভারী হয়ে আসে গাঢ় মায়ার কুহক। যেন শত জাদুগরীর চেতনাবিহীন ইন্দ্রজাল উষ্ণ গান বুনেছে সেই চোখে! ছেলেটার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে রইলো লক্ষ্মী। নিষ্পলক সে দৃষ্টি। জঙ্গলের উঁচু উঁচু গাছের মাথা ভেদ করে চরাচরে নেমে আসা সোহাগী আলোর সাথে যেন সর করেছে, বসন্তের হালকা হিম হিম ভাব। দূর থেকে ভেসে আসা অনামী পাখিটার ঠোঁটের শিসে হয়তো তখন বোনা হচ্ছে নিরাকার কোন জাদুমন্ত্র। লক্ষ্মীর নিখাদ নিটোল কাজল কালো চোখদুটো বেয়ে তখন ফিসফিস সংকেত শব্দেরা ছুঁয়োছুঁয়ি, লুকোচুরি খেলছে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে! ক্রমশঃ সম্মোহিত করে ফেলছে ছেলেটার অবুঝ বন্য চোখদুটোকে। ছেলেটা পেছন ফিরে তাকাল একবার তারপর জঙ্গলের ভেতর পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠে যেতে লাগলো। ছেলেটার পরনে শতছিন্ন একটা হাফপ্যান্ট, কোমর থেকে বেশ খানিকটা নেমে এসে নিতম্ব দেশ প্রায় পুরোটাই উন্মুক্ত। হাতে একটা কাস্তে। কাছেই কোন আধ বোজা ডিহিতে সে এসেছিল মোষ চড়াতে। লক্ষ্মীও ছেলেটার পেছন পেছন হাটতে লাগলো। ওর সন্ধানী চোখ খোঁজ পেয়েছে এই ঘন জঙ্গলে ওর পরবর্তী আস্তানার।
লক্ষ্মীর পুরো নাম লক্ষ্মী রানী মাহাত। বাড়ি পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের পায়ের কাছে, বামনী ডুঙরি নামের ছোট্ট একটা গ্রামে। ওরা কয়েক পুরুষ ধরে সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়। সাপের বিষ তুলে ওষুধ তৈরী করে। ওর বাপ ঠাকুরদা জাঁতমঙ্গল পালা গাইত। জ্যৈষ্ঠের প্রখর তাপে ডিহির ঠিক মাঝখানে ডিঙিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতে হাত তিনেক লম্বা পাহাড়ি কেউটে সাপকে, মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড় করিয়ে রেখে ওর বাপ জনার্দন মাহাত যখন গাইত,
“জয় মা মনসাদেবী জয় বিষহরি।
অষ্টগো নাগের মাথায় পরম সুন্দরী।।
সাতালি পর্বতে যে এই নো আর বাসঘর।
তায় শুয়ে গো নিন্দা করে বেহুলা লখিন্দর।।”
লক্ষ্মী তখন হাঁ করে ওর বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। সদ্য পূর্ণিমা থেকে সরে আসা বিহ্বল চাঁদের জরায়ু থেকে চলকে পড়া নীলচে জ্যোৎস্নায় মাথা ভিজিয়ে ওর বাপ ওকে জামশেদপুরের
গল্প শোনাত। দলমা পাহাড় আর ডিমনা লেকের গল্প, কালিমাড়ির গল্প, দলমার শরীর থেকে নেমে এসে ডিমনায় জল খেতে আসা চিতল হরিণের গল্প। তারপর একদিন পরবের মেলায় এক হাট্টাগোট্টা মরদকে দেখল লক্ষ্মী। ওর বাপের সাথে হাসি মস্করা করছিল লোকটা। পরবের হাটে মাঝে মাঝেই টাটানগর থেকে লোকজন আসতো। তারপর হুট বলে একদিন জনার্দন ওর ছুড়ির বিয়ে ঠিক করে বসল সেই লোকটার সঙ্গে। হলুদবাণীর যোশীলাল ভাট্টি। যোশীলাল আদিবাসী নয় তবু প্রথম দেখাতেই লক্ষ্মীকে ওর মনে ধরে গেছিল। যদিও সেটা ভালোবাসা ছিল না, একেবারেই ছিল না সেটা অবশ্য লক্ষ্মী বুঝেছিল বিয়ের কয়েক মাস পর। হলুদবাণীতে যোশীলালের ভাটিখানা ছিল। সে ব্যবসা ছাড়া সেও সাপের বিষ বেচতও। ডিমনা হাটে বাঁধা খদ্দের ছিল তার। তাছাড়াও বর্ডার পার করেও বিষ চালান দিত এদিক ওদিক। লক্ষ্মীকে দিয়ে জাত সাপকে বশ মানিয়ে বিষ তোলাত। তাছাড়াও নিয়ম করে ওকে ভাটিখানায় বসাত যাতে খদ্দেরের কমতি না হয়। উঠতি বয়সের নধর শরীর লক্ষ্মীর। যৌবন উথলে উঠছে সুন্দরী সুবর্ণরেখার মত। সেরাতে একজোড়া কামাতুর চোখ ভাটিখানায় বসে আপাদমস্তক মাপছিল লক্ষ্মীর একঢাল চুল, শ্যামলী গালের আভা, স্ফীতকায় স্তনের বর্তুল। সারা শরীরময় মাতাল করা একটা অস্বস্তি নিয়েও চুপ করে ছিল লক্ষ্মী। লোকটা যোশীলালের খাস মেহমান, সেটা দিব্যি টের পেয়েছিল ও।
“তোহার মেহরারু কে ইয়াদ বা। কব্ মিল যাই?”
ভোজপুরী তেমন বোঝে না যোশীর আদরের ‘লছমী’। কিন্তু কথাগুলোর প্রেক্ষিতে ওর সাবধানী ইন্দ্রিয়ের পাঠানো বিপন্ন সময়ের শব্দ সংকেত সজাগ করে দিয়েছিল লক্ষ্মীকে। আর দেরী করেনি ও। সেদিন রাতেই যোশীর বিছানা থেকে উঠে গিয়ে, চুবড়ি থেকে ওর প্রাণাধিক প্রিয় সিরিশ কেউটেটাকে ঘরে ছেড়ে রেখে পালিয়ে এসেছিল হলুদবাণী থেকে। বান্দোয়ান হয়ে বাসে সোজা ধাসারা এসেছিল ও। নাহ বাড়ির দিকে আর পা বাড়ায়নি লক্ষ্মী। ও জানত ওর বাপ আর ওকে ঘরে নেবে না। জীবনের বিপরীত ঘূর্ণনে অজানা বাহকহীন এক পালকিতে চেপে বসে লক্ষ্মী। দোল খেতে খেতে পাড়ি জমায় অশোক-পলাশ-শিমুল-শালের জঙ্গল ঘেরা বিপদসংকুল অবিন্যস্ত দুনিয়ায়। এই জগৎটা লক্ষ্মীর অজানা হয়তো কিন্তু অচেনা নয়। ঝিকিমিকি তারার মাঝে উন্মুক্ত বনরাজি তার উত্তাল শরীরী আহ্বানে আপন করে নিয়েছিল লক্ষ্মীকে। দুই নারী যেন শরীরে শরীরে মিলে গিয়েছিল। ঠিক যেমন দুটো নদী এসে মেশে মোহনায়। একজনের উচ্ছ্বাস ঢেকে দেয় অন্য জনের স্নিগ্ধতাকে। জঙ্গলে পলাশের লাল, লক্ষ্মীর সিঁথির সিঁদুর আর পরনের লাল কাঁচুলি বেয়ে ঝরে পড়ে ছড়িয়ে গেছিল গমনপথের মানচিত্র বরাবর। চিল্লা, জিতান, সুপুদি, ঋতুগোড়া, খায়েরবানী এই জায়গাগুলো লক্ষ্মী কখনো পায়ে হেঁটে পেরিয়েছে। তেষ্টা পেলে ডিহি বা ঝর্ণা থেকে জল আঁজলা করে তুলে খেয়েছে। খিদে পেলে বুনো ডুমুর বা ছোলার গাছ শুধু তুলে নিয়ে মুখে পুড়ে দিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে খড় বোঝাই ট্রাক্টরের পেছনে উঠে পড়েছে। ট্রাক্টরের চালক সেই চেনা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে গিলে খেয়েছে ওকে। যখন নিজের ইচ্ছে হয়েছে সঙ্গমে আপত্তি করেনি লক্ষ্মী। অচেনা পুরুষ শরীরের সাথে মিলনের সময় শুধু ওর চোখের সামনে যোশীলালের চেহারাটা ভেসে উঠেছে। গাট্টাগোট্টা সুঠাম একটা মরোদ শরীর। ঘেন্নায় বিদ্রূপে চোখ বুজে ফেলেছে লক্ষ্মী। বিড়বিড় করে যোশীর পৌরুষহীন যৌবনকে গালি দিয়ে গেছে শুধু! আর এদিকে রতিক্রিয়ার সময় এক রমণ তাড়িত কৃষ্ণাঙ্গীর সুমিষ্ঠ গন্ধের বিষমাখা যোনিপথের কুহেলিকায় পড়ে, চূড়ান্ত উন্মাদনা থেকে নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঠান্ডা হয়ে গেছে, নীলচে হয়ে যাওয়া একটা জলজ্যান্ত পুরুষ শরীর। নষ্ট একটা ক্রূর মহোল্লাসে সেই দৃশ্য উপভোগ করেছে লক্ষ্মী।
বেশ কয়েকটাদিন সুতান আর তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রামে কাটিয়ে দিল লক্ষ্মী। এতদিনে নিশ্চয়ই যোশীলালের বাড়ির লোক ওকে খুঁজছে। কয়েকদিন ধরেই ওর ঘরের আশেপাশে দুটো স্থানীয় লোককে ঘুর ঘুর করতে দেখছে লক্ষ্মী। ও বুঝে গেছে এবার এখান থেকে সরে পড়তে হবে। দিন চার পাঁচ ধরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রচার করছে এই বারো মাইলের ফরেস্টে নাকি বাঘ দেখা গেছে! বাঘটাও নাকি ওর মতোই ভিনদেশী, পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে কয়েকশো মাইল, বিস্তীৰ্ণ বনভূমির ভৌগোলিক সীমাকে অস্বীকার করে। যোশীলাল এর পোষা গুন্ডা কিংবা পুলিশের জালে ধরা দেবে না লক্ষ্মী, কিছুতেই না। যে লোক নিজের ঘরের মান ইজ্জত বেচতে চায়...
সেই রাতে জঙ্গলের পথে ঘেঁটুফুলের বনে একটা হাত সাতেকের জাতি সাপকে মরে উল্টে পড়ে থাকতে দেখলো লক্ষ্মী। এই প্রথম কুন্ডলী পাকানো ফুলে ওঠা দেহটাকে দেখে গা গুলিয়ে বমি পেল ওর। অদূরে তখন এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ! গরম ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস এসে পড়ছে লক্ষ্মীর গায়ে। লক্ষ্মী আর বাঘিনী এখন মুখোমুখি! দুজনেই প্রচন্ড ক্ষুধার্ত! কিন্তু দুজনকেই পালাতে হবে, বড় বড় খাঁচাওয়ালা গাড়িগুলো পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে ক্ষরহীন ভীষণ এক জান্তব উদ্দীপনায়। জেগে থাকা রাতটা ক্রমশঃ ঢাকা পড়ে যায় মশালের আলো আর হুলা পার্টির চিৎকারে। একই জঙ্গলের দুই প্রাক্তন প্রেমিকার মত বাঘিনী ও লক্ষ্মী চুপচাপ সরে যায়, আকাশের বুক থেকে খসে পড়া হলদে তারাকে বুকে করে। দুজনেরই এখনো ধরা পড়া বাকি।
প্রবন্ধ
রিভার্স সুইং
সোমা বান্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

তিরতিরে রাঙাদিঘির ধারে সবুজ গ্রামখানার নাম বাদলডাঙা। বর্ষায় তার চোখ জোড়ানো রূপ। এলাকার আর কোনও গ্রামে এত শিক্ষিত লোকের বাস নেই। অন্য গ্রামে যেখানে কেঁদে ককিয়ে একখানা প্রাইমারি স্কুলের দেখা মেলে, সেখানে বাদলডাঙায় একটা ডিগ্রি কলেজও আছে। দূরদুরান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে সে কলেজে। শুধু লেখাপড়াই নয় খেলাধুলোতেও এ কলেজ চ্যাম্পিয়ন। ফুটবল, ক্রিকেট এথেলেটিক্স, ক্যারাটে সবেতেই এই কলেজের ছেলেমেয়েগুলো এত্ত এত্ত মেডেল আর কাপ জেতে।
ঝাউপুকুর গ্রামের দেবু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে উচ্চমাধ্যমিকে। পাঁচবাড়ির এঁটো বাসন মেজে নিজে খেয়ে না খেয়ে ছেলেটার মুখে খাবার জোটায় ময়না। কাজ করতে করতে ইলেক্ট্রিকের তারে যেদিন ঝুলে পড়ল ঘরের মানুষের শরীলটা, ময়নার ছেলেটা তখন বুকের দুধ খায়। সেই থেকে টেনে হিঁচড়ে চালিয়েছে দুটো পেট। দেবুকে ট্যাঁকে করে শীলা দিদিমণির বাড়িতে যেতো ময়না। দিদিমণির মেয়েটা দেবুর পিঠোপিঠি। মেয়ের সঙ্গে দেবুকেও পড়াতে বসাতো দিদিমণি।
“হ্যাঁ রে ময়না তোর ছেলের তো খুব বুদ্ধি রে! ওকে লেখাপড়া করাবি না!”
“কি যে বলো দিদিমণি, পেটের ভাত জোটাতিই কাপড় খুলি যাচ্চে আবার নেকাপড়া।”
“সে কি রে তা বললে হয়! কাল যাবি আমার সঙ্গে আমি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে দেবুকে ভর্তি করে দেব”
সেই শুরু হলো দেবুর লেখাপড়া। ক্লাসে মাষ্টারমশাই বোর্ডে প্রশ্ন লেখার আগেই উত্তর বলে দেয় দেবজিৎ ডোম। দেবুর মেধা দেখে তাক লেগে যায় ছেলেমেয়েদের। হেডমাস্টারমসশাই বলেন এ ছেলে শুধু স্কুলের নয় একদিন গোটা দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। ইস্কুলের সামান্য মাইনেটুকুও দেওয়ার ক্ষমতা নেই ময়নার। পাঁচ বাড়ির জোয়াল ঠেলতে গিয়ে সরকারি টাকা পাওয়ার জন্য ক্যাম্পে যাওয়ার সময়টুকুও হয়না। কোনওরকমে দিন গুজরান করে মায়ে-পোয়ে। ময়নার কাজের বাড়ির বৌদিরা এত ভালো, যে ছেলের বই খাতা পেন্সিল কিছু নিয়েই ভাবতে হয়না ময়নাকে। সারাদিন খেটেখুটে এসে চাট্টি ভাত বসায় ময়না। শরীলটা বুঝি গরম উনুনেই ঢুলে পড়ে যায়। কুপির পাশে বসে কি সব পড়ছে দেবু। ময়না এসবের কিছুই বোঝে না। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবে আজ বাপটা থাকলে হয়তো বড় ইস্কুলে যেতি পারতো ছেলেটা।
“মা ভাত দে”
চমকে ওঠে ময়না। আহা ইস্কুল থেকে এসে ইস্তক পেটে দানা পড়েনি ছেলেটার। তার উপর আবার কিরকিট খেলার নেশা। আরে বাবা যার পেটে ভাত জোটে না তার ওসব বড়নোকের খেলা খেললে চলে?
“ছেলেটা তোর খুব ভালো হয়েছে রে ময়না, যেমন ভালো পড়াশোনায়, তেমনি ভালো খেলে। ওকে একটু ভালো খাবার দাবার দিবি” …বারান্দার ইজি চেয়ারে হুঁকো হাতে নিয়ে বললেন মন্ডল কাকাবাবু।
“কোতায় পাবো বাবু! নুন ভাত জুটতিচে কোনও রকমে এই ঢের। এর ওর বাগানের সবজি, মাজেমধ্যি ধানমাঠের মাছ দু একটা….”
“ওতেই হবে রে। ডাল ভাত খেলেই হবে পেট ভরে”
একসঙ্গে চুটিয়ে লেখাপড়া আর ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছে দেবু। ব্যাটসম্যান হিসাবে বেশ নামডাকও হয়েছে। পাশের গ্রামের হাইস্কুলে দেবুকে ভর্তি নেওয়ার জন্য মাষ্টারমশাইরা মুখিয়ে আছেন। এমন প্লেয়ার পেলে স্কুলের টিমটা খুব ভালো হবে, তার উপর এমন মেধাবী ছাত্র। একেবারে সোনায় সোহাগা। কলকাতার টিমের সঙ্গে খেলার জন্য দূর-দুরান্তের গ্রাম থেকেও ডাক আসে দেবুর। সোনালি মেডেল, ছোটবড় কাপ, এটা ওটা প্রাইজ, সার্টিফিকেটে বোঝাই হয়ে গেছে ময়নার ছিটেবেড়ার ঘরখানা। শ্বশুর বাড়ি থেকে পাওয়া পোঁটবাটাই তো একমাত্র সম্বল। তাতে জামা কাপড়, খুচরো পয়সা, দেবুর বাপের ছবি, দু’চারটে পেতলের গয়না, মায়ের দেওয়া বিয়ের লাল শাড়িটা কিছুই তো বাকি নেই। তার উপরে এইসব ‘জঞ্জাল’ কোথায় যে রাখে ময়না! ছেলের পাইজ বলে কতা, হ্যালাছেদ্দা কল্লি চলবে কেন!
দেবু উচ্চমাধ্যমিক পাশ দেচে। ভালো নেজাল করেচে বলে টিভি থেকে নোক এয়েচিল। ময়নার বাড়ির দাওয়া ভেঙে পড়েছে লোকে। দেবুর কলেজের সব চালাতে রাজি হয়েছেন আলাউদ্দিন চাচা। কাকভোরে উঠে ঘরের কাজ সারে ময়না। কাপড় চোপড় ছেড়ে গোবর নিকিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় মন্ডল কাকাবাবু হাজির।
“এত সকালে আপনি কত্তা! বৌদির কিছু অয়েচে নাকি!”
“ওরে না রে, তোর ছেলেটাকে নিয়ে যেতে এলাম”
“কোতায় নে যাবে কত্তা বাপধনকে আমার!”
“আরে আজ গোঁসাইবাগানে কলকাতা থেকে খেলার মাষ্টাররা আসবে। ছেলেটাকে যদি ওদের চোখে লেগে যায় তাহলে কেল্লা ফতে”
“ছেলটাকে তোমরা কলকাতা নে যেউনি কত্তা। আমার বুকটা যে একদম…..”
“আরে না না। তোর ছেলে তোর বুকেই থাকবে। একবার তো কলকাতার বাবুদের দেখাই আমাদের গাঁয়ে কেমন রত্ন লুকিয়ে আছে!”
দেবুর আনন্দ আর ধরে না। খেলার কোনও সরঞ্জামই ওর নেই। জামা নেই, জুতো নেই, প্যাড নেই তবু ও যেন জেতার জন্যই খেলতে নামবে। মন্ডলদাদুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। মুখে একটু জলও দিল না। ছেলেটা রাস্তার মোড়ের বাঁশঝাড়টার আড়ালে চলে গেলে ময়না দু হাত কপালে ঠেকায়….. “জয় ঠাকুর”।
গোঁসাইবাগানের জমিদার বাড়ির মাঠে জড়ো হয়েছে ছেলেপিলের দল। দেবু তাদের মধ্যমণি। চেহারার গড়নটা ঠিক বাপের মতো। তার মধ্যে মায়ের মতো লাবণ্যভরা মুখটায় হালকা গোঁফের রেখা। হাতে টেঁকে দেওয়া বেগুনি জামাটায় বেশ মানিয়েছে দেবুকে। কলকাতার বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খেলতে হবে। হেলমেট, জুতো, প্যাড পরা ছেলেদের সঙ্গে একই ক্রিজে খালি পায়ে খালি মাথায় দৌড়বে দেবু। প্রায় বাউন্ডারি লাইন থেকে দামি জুতো পায়ে ছুটে আসছে কলকাতার বোলার। বল তো নয় যেন আগুনের গোলা। মন্ডলমশাই একটু ঘাবড়েই গেছেন। ছেলেটাকে এমন জলে ফেলে দেওয়া বোধহয় ঠিক হলো না। ভাবতে ভাবতেই কান ফাটানো আওয়াজে চমকে উঠলেন মন্ডলবাবু। শুধু কবজির জোরে ওই আগুনের গোলাটাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে দেবু। কলকাতার বাবুদের তো চোখ ছানাবড়া। এ ছেলের তো জাতীয় দলে খেলার কথা।
“ঠিক আছে মন্ডলবাবু। ওকে বলুন ওর কলেজ টিমে খেলতে। ওখান থেকে আমরা ওকে সিলেক্ট করে নেবো।”
গোপেন মন্ডলের বুকের ছাপান্ন ইঞ্চি ছাতিটা আরও একটু ফুলে গেল। গোঁসাইবাগানের রত্নটিকে তিনিই তো খুঁজে আনলেন!
ভর্তির কাগজটা নিয়ে বাদলডাঙা কলেজের প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে মাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেবু। ময়না লজ্জায় এক গলা ঘোমটা দিয়েছে। নেহাৎ শীলা দিদিমণি, তাই এসেছে ছেলের সঙ্গে। হাজার হলেও দিদিমণির কাছেই তো দেবুর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। দিদিমণির মস্ত ঘরটায় ঢুকে শরীলটা কেমন যেন আনচান করে ময়নার।
“দিদিমণি তোমার কালেজে নেকে গেলুম দেবুরে। তুমি দেকেশুনে নেকো। ছেলেটার আবার বড্ড কিরকিটের নেশা। বদমাসি করলে দিও দু ঘা” দিদিমণি হতবাক। এখনও কোনও মা এমন কথা বলেন! গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা একটা ধমক দিলে যেখানে ঘুরে দাঁড়ায় ছাত্র, শাসানি দেয় অভিভাবক, সেখানে আজও এমন মা আছেন! “তুই কিচ্ছু চিন্তা করিসনা ময়না। তোর ছেলে লেখাপড়াও করবে, ক্রিকেটও খেলবে।”
ডি এম স্যারের ক্লাসটা করতে বড় ভালো লাগে দেবুর। এত সুন্দর করে সারা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরেন স্যার, মনে হয় সেই দেশেই পৌঁছে গেছে সে। আজকে ক্লাসের পর দেবুকে দেখা করতে বলেছেন ডি এম স্যার।
“শোন দেবু এবারে আমাদের কলেজে জেলাস্তরের খেলা হবে। কাল মিটিং আছে ম্যাডামের ঘরে। তুই থাকিস কিন্তু।”
শীলা দিদিমণিকে ঘিরে একদল অধ্যাপক। যুধিষ্ঠিরবাবু এই কলেজের ক্রিকেট টিমের দায়িত্বে আছেন। “আমার টিম মোটামুটি তৈরী। আর একজন ব্যাটসম্যান হলে খুব ভালো হতো ”ডি এম স্যারের চোখে ভেসে উঠল দেবুর সরল মুখটা…. “আমাদের দেবজিৎ খুব ভালো ব্যাট করে। ওকে দলে নিলে মন্দ হয় না”
“দেবজিৎ! সে আবার কে? সে কি খেলতে রাজি হবে?“ ওকে আমি আজ থাকতে বলেছি। ম্যাডাম অনুমতি দিলে ওকে ডেকে কথা বলা যায়” অনুমতি দেন ম্যাডাম। ভয়ে, উৎকন্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে সকলের সামনে দাঁড়ায় দেবু। মাথা আর উঁচু হয়না। পরনে মলিন একটা জামা। প্যান্টটা গোড়ালির উপরে, পায়ে হাওয়াই চটি।
“তোমার তো জামাকাপড়ই ঠিকমতো নেই তুমি কি করে…..”
“স্যার খেলবো তো ব্যাটে বলে, জামাকাপড়…. মানে….”
“আরে দর্শনদারি বলে তো একটা কথা আছে….. তোর না আছে ঢাল না তরোয়াল”
ইনিয়ে বিনিয়ে যুধিষ্ঠিরবাবু দেবুকে বোঝাতে চান কলেজ টিমে তার জায়গা হওয়া কঠিন। দেবুও নাছোড়বান্দা। কলেজ টিমে সে ঢুকবেই। শীলা দিদিমণিও একটু বোঝানোর চেষ্টা করেন।
“ওকে চাইছেন কেন ম্যাডাম! আপনার পাড়ার ছেলে বলে!”
শীলা দিদিমণির সঙ্গে এভাবে কথা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না দেবু। প্রাণপণে থামানোর চেষ্টা করে যুধিষ্ঠির স্যারকে। এমন দেবতূল্য মানুষটা শুধু ওর জন্য এভাবে অপমানিত হবেন?
“আমাকে তো খেলার জন্য দলে নেবেন স্যার আমি কোথায় থাকি তাতে কি?” মাথা নীচু করে গর্জে ওঠে দেবু।
“কি খেলবি তুই? কতটুকু জানিস খেলার? ডোমের ব্যাটা নোংরা না ঘেঁটে এসেছে সাহেবদের খেলা খেলতে”।
চোখের জল ধরে রাখতে পারে না দেবু। সেই সঙ্গে দিদিমণিও। পদবী তার যাই হোক তার মা কোনওদিন নোংরা ঘাঁটতে দেয়নি দেবুকে। অকথ্য পরিশ্রম করে সংসারের হাল ধরেছে ময়না। দেবুও দিনরাত এক করে মায়ের এই পরিশ্রমের মূল্য দিতে চেষ্টা করেছে। আর আজ! একজন শিক্ষিত মানুষ এভাবে বললেন! চোখের জল সামলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল দেবু।
“কি হয়েছে রে দেবা? কানছিস কেন? এগিয়ে আসে কলেজের এক দাদা। দেবু মুখ ফুটে বলতে পারেনা তার এই অসম্মানের কথা। জন্মের উপর তো তার কোনও হাত নেই। তাহলে কোন অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হচ্ছে আজ!
“এত বড় কথা! চল তো শালা দেখে নিই কত বড় মাতব্বর হয়েছে ওই যুধিষ্ঠির! দেবু না খেললে কলেজের কোনও টিম হবে না।”
সব দেখেশুনে ঘাবড়ে গেছে দেবু। একদল ছেলে মিলে গাছে, পাঁচিলে, দেওয়ালে, ক্লাসরুমে, স্যারদের ঘরে সাঁটিয়ে যাচ্ছে একটা কাগজ। খবরের কাগজে মোটা পেন দিয়ে লেখা-
ধোপা বলে ডোম তোর হাতে কেন কাদা
ডোম বলে আমার ‘হাতে’, তোর ‘সারা অঙ্গে’- দ্যাখ।
স্যারের মুখে ‘ডোম’ শব্দটা শুনে ঠিক এই কথাগুলোই তো মনে হয়েছিল দেবুর। ওরা কেমন করে জানলো সে কথা! ও তো কাউকে বলেনি! উন্মত্ত ছেলেরা দুদ্দাড় করে ছুটে যায় দিদিমণির ঘরের দিকে। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায় দেবু। অনেক চেষ্টা করেও অনর্থ এড়াতে পারেনা সে।
“ম্যাডাম, যুধিষ্ঠির স্যার দেবুকে জাত তুলে কথা বলেছে আপনার সামনে?” লজ্জায় মাথা নীচু শীলা দিদিমণির। গলার স্বর একেবারে ক্ষীণ- “হ্যাঁ বাবা, বলেছেন”
“আপনি ওনার বিরূদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন ম্যাডাম?”
শীলার নাভীমূল থেকে বেরিয়ে আসতে চায় কান্নার রোল। ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে ওঠে দেবুর ছোটবেলার দিনগুলো। মুক্তোর মতো হাতের লেখা দেবুর। সে হাতকে নোংরা বলে দিলেন একজন শিক্ষিত অধ্যাপক? একবারও ভাবলেন না এমন কথা শুনে যে মরমে মরে যাবে ছেলেটা! একি শিক্ষা না শুধুই ডিগ্রি?
“তোমরা শান্ত হও। দেখছি কি করা যায়”।
আলোচনা সভায় ভাষণের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন যুধিষ্ঠির ধূপী। হিংস্র চোখের চাউনি যেন দাবানলের বহ্নিশিখা। কাউকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে শুধু গলার জোরে উড়িয়ে দিতে চান নিজের কৃতকর্মের সমস্ত চিহ্নটুকু। বাইরে উদগ্রীব ছাত্রের দল। দেবু কি সুবিচার পেলো? ডি এম স্যারের পরামর্শ মতো দেবুকে ডাকা হলো সভায়। দেবু অকুতোভয়। ওর না আছে জাত খোয়ানোর ভয়, না আছে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সম্পদ বলতে আছে আস্ত একখানা মেরুদন্ড। সুদৃঢ়, সুঠাম।
“দেবজিৎ, তোমার এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য আছে?”
“আছে স্যার”।
“বলো”।
“আমি দেবজিৎ ডোম, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সচেতন অবস্থায়, কোনওভাবে প্ররোচিত না হয়ে বলছি, যুধিষ্ঠির স্যার আমার জাত তুলে কথা বলেছেন”।
দেবজিৎ বেরিয়ে যায় দমকা হাওয়ার মতো। সমস্ত ঘরটায় শ্মশানের শান্তি। অনেক কষ্টে চোখের জলকে অবাধ্য শিশুর মতো শাসন করছে শীলা।
“দেবজিৎ মিথ্যে বলছে……” মুহুর্তে খানখান হয়ে গেল সমস্ত নীরবতা। বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠলেন দশাসই জয়ন্ত মন্ডল।
“এরকম কোনও কথাই বলা হয়নি ওকে। ম্যাডাম আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি জাতপাত নিয়ে নোংরা খেলা খেলবেন না”।
ঘটনাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শীলা। জীবনে কোনওদিন মানুষ ছাড়া আর কারও কোনও পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি শীলা। কার কি জাত, কে স্পৃশ্য কে অস্পৃশ্য এসব ভাবনাকে মনুষত্বের বিকৃতি বলেই জেনে এসেছে চিরকাল। আজ জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসে এ কেমন কথা কানে বাজছে তার! হে ঈশ্বর এই জন্যই কি অধ্যাপনা করতে আসা! বিস্ময়ের অনেকটাই তখনও বাকি ছিল। ষোলকলা পূর্ণ হলো কয়েকজনের মিলিত চিৎকারে। অনিমেষ সিনহা, পুলক মান্না, সরফরাজ কালাম, তপোব্রত বসু….সব মিলিয়ে প্রায় জনা কুড়ি অধ্যাপক শুধু গলার জোরে দিনকে রাত করে দিলেন। মাকে কথা দিয়েছে দেবু, কখনও মিথ্যে বলবে না। দশচক্রে ভগবান ভূত হওয়ার মতো পাকেচক্রে দেবজিৎ ডোম হয়ে গেল ‘মিথ্যেবাদী’। ঘটনাটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি শীলা দিদিমণি। শুধু দৃঢ় কন্ঠে বললেন…… “আপনারা সকলে অস্বীকার করলেও আমি একাই বলবো দেবজিৎ মিথ্যে বলেনি।”
বকুলগাছের ছায়ায় দেবজিৎকে ঠান্ডা করতে নিয়ে এসেছে তার বন্ধুরা।
“স্যাররা পুরো পালটি খেয়ে গেল মাইরি!” শান্ত ছায়াতল থেকে উঠে আসে বজ্রনির্ঘোষ-
“দেবু ছাড়া ক্রিকেট টিম হচ্ছে না হবে না……।”
বাদলডাঙা কলেজের প্রতিটি ইঁটে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে একের পর এক স্লোগান -
“দেবু তুই খেলবি…… কাপ নিয়ে আসবি…।”
“দেবুর জাত তুলল কে জে ডি স্যার আবার কে……।?"
সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের হয়ে গলা ফাটানো অধ্যাপকের মধ্যে চলছে ফিসফাস………
“ছেলেটাকে টিমে নিলেই তো ঝামেলা মিটে যেতো। এখন কোথাকার জল কোথায় গড়ায় তার ঠিক নেই…।” শিক্ষিত জুজুদের দেখে করুণা হয় শীলা দিদিমণির।
আজ প্রতিপক্ষ গায়ত্রী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে বাদলডাঙা। কোচ যুধিষ্ঠির স্যারের সেরকমই নির্দেশ ছিলো। যদিও সকলে বলছে গায়ত্রী কলেজের ছেলেরা দারুণ ব্যাট করে। প্রথম বল থেকেই উড়িয়ে খেলছে গায়ত্রী কলেজ। যুধিষ্ঠির স্যারের পছন্দের বোলাররা কোথায় বল ফেলবে বুঝেই উঠতে পারছে না। ফিল্ডাররা বল কুড়িয়ে কুড়িয়ে হয়রান। ঘেমে নেয়ে হাঁপিয়ে একসা। উইকেট পড়া তো দূরের কথা, হাউইএর মত বল ছুটে যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে। বিপুল রান তুলে ইনিংস শেষ করলো গায়ত্রী কলেজ। এবার বাদলডাঙার দান। প্রথম বলেই তিনটে উইকেট মাটি থেকে ছিটকে দিল বিল্টু, গায়ত্রী কলেজের ফাস্ট বোলার। বলটা চোখে দেখতেই পেলো না যুধিষ্ঠির স্যারের স্টার ছাত্র অশোক। একে একে শক্তিপদ, বেণুগোপাল, মিরাজ, শইফুল ধরাশায়ী সব তাবড় ব্যাটসম্যান। ডি এম স্যার হাত কামড়ান… “দেবুটাকে এত পিছনে রাখার কোনও মানে হয়?” অবশেষে পার্টনারশিপ জমালো ধীমান আর কামরান। কাকে বলে খেলা! তুমুল হইচই মাঠে। বলে বলে ছক্কা। ক্রিজের ভিতরে বিদ্যুৎ গতিতে জায়গা বদল করছে দুই খেলোয়াড়। যুধিষ্ঠির স্যারের শুকিয়ে আমসি হয়ে যাওয়া মুখটায় ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না।
“দেখেছ! কেমন টিম তৈরী করেছি? আরশোলার পাখি হওয়ার শখ…”
খেলা যখন প্রায় হাতের মুঠোয়, ধীমানের ব্যাটে লেগে বলটা উড়ে গেল উড়নতুবড়ীর মত। গায়ত্রী কলেজের বদরুদ্দিনের হাতে নির্ভুল ক্যাচ। স্কোরবোর্ডে এক বল চার রান। হায় হায় করে উঠলো গোটা মাঠ। তীরে এসে তরী ডুবলো বাদলডাঙার।
ডি এম স্যার কপাল চাপড়ান - “ইসস এখন দেবু নেমে আর কি করবে?"
“মুখ রেখো মা…।” ইষ্টনাম জপেন মন্ডলমশাই।
দেবু দুরুদুরু বুকে মাঠে। যুধিষ্ঠির স্যার উঠে চলে গেলেন। চারিদিক গম গম করছে ছেলেদের কান ফাটানো চিৎকারে… দে এ এ বু…… দে এ এ বু। তুফানের মত ছুটে আসছে বিল্টু। ভূমিকম্প হওয়ার মত কাঁপছে ক্রিজখানা। তার থেকেও বেশি কাঁপন দেবুর সরু খাঁচাটায়। বলটা ব্যাটের সামনে পড়তেই চোখ বুজে উল্টো করে ব্যাট চালালো দেবু। ফিল্ডাররা কিছু বোঝার আগেই সাঁ করে বল চলে গেল মাঠের বাইরে। দেবুর জলে ভেজা চোখে ভাসে ময়নার ঘোমটা দেওয়া মুখখানা। বাতের ব্যাথা ভুলে দেবুকে কোলে তুলে নিয়েছেন মন্ডলমশাই। কোচ বলে কথা কি করেই বা সরে থাকেন। করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন জে ডি স্যার।
“কনগ্র্যাচুলেশান দেবু। কিন্তু এই রিভার্স স্যুইং তুমি কোথা থেকে শিখলে?”
শান্ত, পরিশীলিত গলায় উত্তর দেয় দেবু -
“আপনার থেকে স্যার। আপনি এই শটটা দারুণ খেলেন।”

গল্প
"বিপু’দা সাবধান! সাবধান বিপুদা!" গাড়িটা হালকা ব্রেক কষে, হালকা কাটিয়ে সোজা ফতেপুর রোডের দিকে রওনা দিল মারুতি ওয়াগনার।
বিপ্রতীপ - "মরেনি বোধহয়? তাই না?"
দেবাশীষবাবু - "সাব্বাস দাদা সাব্বাস। দিব্যি বেঁচে আছে।"
গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে ডানদিকের লুকিং গ্লাস দেখে বিপ্রতীপ বলল - "আচ্ছা কি সাপ ছিল ওটা"?
তুহিন উত্তরে বলল - "খড়িস।"
- "কিন্তু আমার যেন মনে হল অন্য কিছু।"
- "আরে না বিপুদা আমাদের এখানে এই খড়িস সাপটাই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।"
- "পাশে পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের ছায়াটা কেমন কেমন যেন মায়াবী করে তুলেছে না" - দেবাশীষবাবু বললেন।
বিপ্রতীপ - হালকা হাসি গাড়ি চালাতে চালাতে জবাব দিল আর আমাদের সে ভাগ্য আছে মায়া ও মায়াবি বোঝার।
দেবাশীষবাবু বললেন - "তা যা বলেছেন ভায়া। ভোর রাত থেকে স্টিয়ারিং ধরে যেভাবে কলকাতা থেকে চলে এলেন একটানা……..বুঝলেন তুহিনবাবু এককাপ চা পর্যন্ত খাওয়ান নি রাস্তায়। ভাবলাম শক্তিগর থেকে একটু ল্যাংচা নেব।"
বিপ্রতীপ বলল - "ব্যাস খাই খাই শুরু হয়ে গেছে।"
দেবাশীষবাবু - "কি কি বললেন?"
- "না মানে ওই….."
ফতেপুর জঙ্গল ফেলে ৫৭ নম্বর ক্রস রোড হয়ে অজয় নদীর দিকে গাড়ি এগিয়ে চলল। (পাস থেকে হর্ন দিয়ে একটা সাদা Hyundai ক্রেটার ওভার্ট্রেক)। অজয় নদীর তীরে বাম দিক চেপে সাবধানে গাড়িটা রেখে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।
তুহিন বলল – "হ্যান্ড ব্রেকটা টেনে দিও।"
একটু আড়মোড়া ভেঙে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে বিপ্রতীপ পাঞ্জাবির পকেটটা সার্চ করে বলল - এই যা! লাইটারটা টেবিলের উপর ফেলে এসেছি।"
তুহিন - "দাঁড়াও আমার দেশলাইটা আছে।"
বিপ্রতীপ - "অজয় নদীর এই দিকটা আগের বাড়ি আসিনি না রে তুহিন?"
তুহিন বলল – "না বিপুদা।"
সকালেই আজ তুহিনের কোয়াটারে বিপ্রতীপ আর দেবাশীষবাবু দুদিনের জন্য নিখাদ ছুটি কাটাতে এসেছেন। সাথে ফতেপুর ড্যামের সানসেট দেখার জন্যে। শীতটা সবে গেছে তবে ঠান্ডার আমেজটা এখানে কিছুটা রয়ে গেছে। পলাশ বনের মাঝ দিয়ে পড়ন্ত বিকেলে বেরিয়ে পড়েছে তিনজন।
তুহিন বিপ্রতীপ এর মামার ছেলে। HDFC রূপনারায়ণপুর শাখার কর্মচারী। মামা CLWতে চাকরী করেন। পেশায় শিক্ষক বিপ্রতীপ। আর দেবাশীষবাবু একজন লেখক। এবছর আর্ন্তজাতিক বইমেলায় কলকাতার নামি নামি প্রকাশনা থেকে তার বেশ কিছু বই ও প্রকাশ পেয়েছে। এই বিপ্রতীপ এবং দেবাশীষবাবু সমবয়সী না হলেও, দারুন বন্ধুত্ব দুজনের মধ্যে। বছর সাতেক আগে রাচি বেড়াতে গিয়ে দুজনের আলাপ। আর যেহেতু দুজনে খুব ঘুরতে ভালবাসে ন তাই ক্রমেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছেন একে অপরের।
****
- "তুহিন লক্ষ্য করেছিস কি?"
- "কি বলতো বিপুদা?"
- "সেই সাদা রঙের ক্রেটাটা না? আমাদের ক্রস করে কেমন চলে গেলো তখন…… আর কি স্পিড এ নদীর চরে গাড়িটা নামিয়ে নিয়ে গেলো দেখলি? সকালে কল্পনার সাথে দেখা করতে এসেছিল যেটা ….কি রে মনে পড়ছে তুহিন? তোর কোয়ার্টারের সামনে একটু এগিয়ে আম গাছ তলায় এই গাড়িটাই দাড় করিয়েছিল না?"
- "হুম অতটা লক্ষ্য করিনি গো।"
- "বাট আই অ্যাম সিওর এবাউট ইট তুহিন। আমি তখন তোর কোয়ার্টার এর বাইরেই ছিলাম। ওর বাঁ দিকের পিছনে একটা ডেন্টিং এর দাগ আছে।"
- "কিন্তু যদি তাই হয় ও……..এটা এখানে কি করছে?"
- "ওটা তো কল্পনার কোন এক পিসতুতো দাদার গাড়ি।"
দেবাশীষবাবু বললেন - "আরে দাদা কি যে বলেন ক্রেটা গাড়ি কি একটাই আছে নাকি?"
বিপ্রতীপ বলল - "আরে না। আমার যেন মনে হলো কল্পনা রয়েছে ভিতরে।"
তুহিন বলল - "বিপ্রতীপদা তবে এর নম্বর প্লেটটা দেখলে JH লেখা ছিল না? কিন্তু ওর দাদা তো কোলকাতা থেকে এসেছে বলেছিল।"
দেবাশীষবাবু বললেন - "আরে আমি এজন্যই বলেছিলাম এটা অন্য গাড়ি। আর হ্যাঁ বিপুদা, কল্পনা বলেছিল সকাল ১১টায় বলেছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে কল্পনা ওর দাদাদের সাথে। তিনদিন ছুটিও নিয়েছে ও।"
বিপ্রতীপ - "আচ্ছা তুহিন তুই কাউকে গাড়িতে দেখতে পেলি না! না?"
- "এত স্পিড এ ধুলো উড়িয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু দাদা কল্পনা তো এমন মিছে কথা বলে না। তাহলে হঠাৎই বা সকালে কাজ করতে এসে মিথ্যে আশ্রয় নিল কেন? কি লুকোতে চাইছে কল্পনা? আমাকেই বা লুকোতে চাইছে কেন?"
বিপ্রতীপ - "হ্যাঁ সেটাই তো বুঝতে পারছি না রে। আচ্ছা চলো আমরা ওই পাথরটার উপর কিছুক্ষণ বসি আর একটু নজরে রাখতে হবে নদীর দিকে।"
দেবাশীষবাবু বললেন - "কি মুশকিল আপনি এখানে এসেও আপনার গোয়েন্দাগিরিটা বন্ধ রাখুন প্লিজ।"
- "একটু বেড়াতে এসেছি আমি" একটা হাই তুলে দেবাশীষবাবু বললেন।
- "তুহিনদা আজ রাতে বারবিকিউটা হচ্ছে তো তাহলে?"
তুহিন বলল - "এই দেবাশীষদা, আপনি আমাকে প্লিজ দাদা বলবেন না। আমি বয়সে অনেক ছোট আপনাদের থেকে।"
পকেট থেকে একটা গোল্ড ফ্লেক কিং বের করে তুহিন বলল - "এস বিপ্রতীপদা এই জায়গাটায় বসো। কেমন নির্জন দেখো। জায়গাটা। পিছনে মেঘটার একটা ছবিটা তুলতেই হবে।"
- "আরে ও বিপ্রতীপদা। আচ্ছা তুহিন, নদীর ও পাশের গ্রামটার কি নাম রে?"
- "ওদিকটা ঝাড়খন্ড।"
- "ওপাশের গ্রামটার নাম কুশবেদিয়া। আচ্ছা তুহিন চলনা ওরা যেখানে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেই জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে একটু যাই কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"
দেবাশীষবাবু বললেন - "আরে…….. আরে কি দরকার দাদা? আপনার না সবকিছুতেই আপনারা একটু বসুন বরং ….আমি ঘুরে আসি ওদিকটা।" বিপ্রতীপ একটা সিগারেট মুখে দিয়ে সোজা চলল নদীর চরে।
- "সাবধান বিপ্রতীপদা। এখানে অনেক অন্য ধরনের লোক ও থাকে। আর সন্ধ্যে ও হয়ে আসছে। বি কেয়ারফুল।"
- "তুই আর দেবাশীষদা বোস আমি আসছি" …..ঢালু বেয়ে বিপ্রতীপ হালকা আলোয় বালির মধ্যে দিয়ে গাড়িটির দিকে এগিয়ে চলল। গাড়িটার কাছে এসে বিপ্রতীপ বললেন -
- "দাদা শুনছেন। এই যে দাদা শুনছেন।"
দুজন লোক নিজেদের মধ্যে চেয়ে গাড়ির দিক থেকে এগিয়ে এলেন। গম্ভীর গলায় বললেন - "কি ব্যাপার বলুন।"
- "না একটু দেশলাই পাওয়া যাবে?"
- "না। দেশলাই নেই।"
- "দেখুন না। আপনাদের গাড়িতে যদি থাকে" …..এই বলে গাড়ির দিকে বিপ্রতীপ এগোতেই লোক দুটি ওর বুকে হাত রেখে বাধা দিলো।
- "বললাম তো নেই।"
- "আরে গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? একটা দেশলাইই তো চাইছি।"
- "কি ব্যাপার বলুন তো? আর আপনি মানে আপনি সকালে এই গাড়িটা নিয়ে আমাদের রাস্তায় এসেছিলেন না কল্পনার সাথে দেখা করতে।"
আর দুপা এগোতেই বিপ্রতীপ যা দেখলো তা একপ্রকার সন্দেহজনক। কে, কল্পনা না। এই কল্পনা।গাড়ির মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পরে আছে কল্পনা।
কাছেই একটা ঝোপের ধারে পরে আছে গাড়ির WB লেখা নম্বর প্লেট। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে কোন একটা অশনি সংকেত এখানে রয়েছে। গাড়িটা নামার সময় স্পষ্ট বিপ্রতীপ দেখেছিল কল্পনা গাড়িতেই ছিল। আর সেটা যে ভুল নয় তা প্রমাণিত।
তার মানে তোমরা মেয়েটাকে পাচার করছো।
সন্ধ্যের পর কুশ বেদিয়া হয়ে পগার পার হবার প্ল্যান তোমাদের। কিন্তু বাছাধনের এ স্বপ্ন যে পূরণ হবে না।
দুজনের মধ্যে একজন অপরজন কে বলল "লালচাঁদ আর দেরি করোনা। ধরো মালটাকে। না হলে সব প্ল্যান চৌপাট হয়ে যাবে। মেয়েটাকে আজই পাচার করতে হবে। সুগত স্যার আপনি গাড়ি স্টার্ট করুন। একে আমি দেখে নেব।"
এই বলে যে মুহূর্তে লালচাঁদ এগোতে লাগল। পাথরের আড়াল থেকে তুহিন বলে উঠলো - "এই দেখুন স্যার এই দেখুন।"
পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর টর্চ জ্বেলে লালচাঁদের মুখে ফেললেন বললেন - "কে রে তোরা? কে?কি করছিস এখানে? কে এই মেয়েটা?"
ততক্ষণে সুগত বালির উপর দিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। তবে তার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করেছে আর একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার।
বিপ্রতীপ তুহিনকে জিজ্ঞেস করল - "কিন্তু তুই এদিকে কিভাবে এলি?"
- "আরে বিপ্রতীপদা পুলিশের ভ্যানটা যে মুহূর্তে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো। আমার যেন মনে হল কোন অসুবিধার সম্মুখীন যাতে তুমি না হও। তার জন্য ওদের সাহায্য চাওয়া যেতেই পারে।"
বিপ্রতীপ বলল - "আরে এই দেখ গাড়ির ভিতরে কল্পনা রয়েছে।"
- "কি বলছো? কল্পনা...কিন্তু কেন?"
- "মনে হয় ওরা কল্পনাকে কোন প্রলোভন দেখিয়ে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছিল। তবে কোন কারণে হাইরোডে ওরা ফেঁসে যেতে পারে এমনটা আন্দাজ করে নদী পেরিয়ে কুশলডিহি গ্রামের ভিতর দিয়ে ওরা পালাতে চেয়েছিল। আর সেজন্য কল্পনাকে অজ্ঞান করে সন্ধ্যা নামার পর নকল নাম্বার প্লেট লাগিয়ে পালাবার ফন্দি এটেছিল।"
গাড়ির মধ্যে থেকে কল্পনাকে নামিয়ে মুখে জল দিতেই কেমন একটা মুখ করে হালকা কাঁদো কাঁদো সরে, কল্পনা বলল - "দাদা। আমি যেতে চাইনি। ওরা আমায় জোর করে …"
তুহিন বলল – "তাহলে তুই যে বললি ওরা তোর দাদা। মিথ্যা কথা বলেছিলি বল।"
- "দাদা ফেসবুকে আলাপ আমার এদের সাথে। আমায় বলেছিল সিরিয়ালে চান্স করিয়ে দেবে।আর তুই নায়িকা হতে চললি।"
- "ও দাদা না গো।তিন বাড়ি ৮০০ টাকা কাজ করে আমার চলে না সংসারে খুব অভাব। বাবা বিছানায় পড়ে ২ বছর। ভাই এর পড়া বন্ধ। কি করব আমি দাদা।" কাঁদতে কাঁদতে বলল কল্পনা।
তুহিন বলল – "এর পর কি করতিস। ইস। তোরা না……" কান্নায় ভেঙে পড়লো কল্পনা।
বিপ্রতীপ বলল - "ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি ওঠ পুলিশ সব সামলে নিয়েছে। তুমি এখন বিপদমুক্ত। তুহিন বলল - "আর আজ বিপ্রদীপদা না থাকলে আরো অনেক বড় বিপদ হতে পারত।পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে লালচাঁদ আর সুগতকে গাড়িতে তুললেন। বললেন - "বেশিক্ষণ এখানে আর থাকবেন না জায়গাটা ভালো নয়। কল্পনা তুমিও একবার থানায় এসো তবে আজ নয় কাল। চোরাচালানকারীদের এটা একটা করিডর বলতে পারেন। মানুষ যাতে ভালো থাকে। আমরা সব সময় চেষ্টা করি সন্ধ্যা ঘনালেই এই সব জায়গায় একবার টহল দিতে।"
- "ধন্যবাদ বিপ্রতীপবাবু। ধন্যবাদ তুহিন। কাল একবার থানায় এসো সাথে কল্পনাকেও নিয়ে এসো
আসবো স্যার।
দেবাশীষবাবু ততক্ষণ পটে এসে উপস্থিত - "বিপ্রতীপবাবু আপনি তো দেখছি সব জায়গায় গিয়ে…… "
- "আরে না না কি যে বলেন দিন একটা সিগারেট দিন তো।" তিনজনে হাত ধরে অজয় এর চড় বেয়ে উপরের দিকে উঠলেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। চাঁদের আলোয় অজয় নদীর বালি গুলো তখন চিক চিক করছে।
প্রবন্ধ

সূর্য তখনও ঢেউ খেলানো হিমের উপর ম্লান অগ্নিরেখা আঁকছিল, যখন আমি এসেছিলাম। ভূস্বর্গের বুক চিরে এক অন্তর্লীন আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছিল বাতাসের শিরা-উপশিরায়। মাটি যেন গৃহত্যাগী সন্তানের মতো শূন্য; নদী, যে প্রতিদিন গোধূলির পর ছেলেমেয়েদের হাসি ভাসিয়ে নিত, সে আজ বোবা, রক্তজমা জলধারা বয়ে চলেছে। প্রত্যন্ত মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিষণ্ণ বটগাছ, যার পাতাগুলো নিঃশব্দে কাঁপে, যেন চরম লজ্জায় মাথা নত করে বয়ান দেয় সেই যন্ত্রণার। তার শিকড়ের কোলে পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন সেই দেহগুলির — অচেনা, অথচ একান্ত আপন, মাটির মতোই।
শস্যক্ষেত্র, যেখান থেকে মাটির গন্ধ উঠতো পূজার ধূপের মতন, আজ সন্ত্রস্ত ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। অদৃশ্য অগ্নিস্রোত পুড়িয়ে দিয়েছে রক্তমাংসের স্বপ্নগুলোকে। আরেক প্রান্তে, পাথরের গায়ে গায়ে আঁচড় কেটে গেছে — সেই পাথর, যারা শতাব্দীজুড়ে রৌদ্র-জল সহ্য করে থেকেছে নীরবে। এখন তাদের শরীরে খচিত হয়েছে বিভেদের শিলালিপি, ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের খোঁজে?
কিছু নরম হাত – সেই হাত যার ছোঁয়ায় ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব পায়, সেই হাত ছুঁয়ে চলেছে শীতল, রাঙ্গা , লালচে নিস্তব্ধ মাটি। কুড়িয়ে নিচ্ছে এক মুঠো ছাই। আর রয়েছে তাঁদের কচি আঙুলে ধরা এক ছেঁড়া জাতীয় পতাকা, যাতে রক্তের ছোপ বসে গেছে। সেই হাত জানেনা ঈশ্বর কী, দেশ কী, বিভেদ কেন — শুধু জানে, বাবা আর হাঁটে না। মায়ের কণ্ঠ, যা একদিন শঙ্খধ্বনির মত ছিল, আজ ঠান্ডা ছাইয়ের মতো নিস্তব্ধ। বুকের ভেতর ছোপ ছোপ দহন, চোখের পাতার কোণে জমে থাকা শুষ্ক বেদনা —এইসব অদৃশ্য ছাইয়ে সেই হাতগুলো ক্রমশ নিজেকে মুড়ে নেয়।
অবিরাম সংঘর্ষের পর পাহাড়ের কোলে গড়িয়ে পড়ে এক মৃত ঘুঘু — উড়তে পারার শেষ স্বপ্নটুকু নিয়েও যেন শূন্যতার দিকে দৌড়চ্ছিল সে। বাতাস তখন বয়ে আনছিল জ্বলন্ত মোমের গন্ধ আর
মৃত চৈতন্যের করুণ রোল। ধর্মের নামাঙ্কিত অসুরেরা মুখোশ পরে এসেছিল, হাতে বোমা আর অশ্রু — যারা ঈশ্বরের ভাষ্য জানত না, জানত কেবল ঘৃণার অন্ধ আবরণ। আমি কে? কী বা আমার পরিচয়? আমি সেই ছাই, সেই একমুঠো ছাই এঁকেবেঁকে পথ ছুঁয়ে চলা ঝড়ের কবলে প্রশ্ন করি —
কোন ঈশ্বরের নামে শিশুর কান্না স্তব্ধ হয়?
কোন ধর্মের আদেশে বাবার বুক চিরে তৈরি হয় ছিন্ন ফুলের উপত্যকা?
কিন্তু উত্তর আর পাওয়া হয় না।গাছেরা থমথম করে দাঁড়িয়ে থাকে, নদী নিজের প্রবাহের শব্দ গিলে ফেলে, পাথর কেবল দেহের ভার বইয়ে চলে নিষ্ক্রিয়ভাবে।শুধু মাটির চিলেকোঠায় পুড়ে যাওয়া কিছু প্রার্থনার শব্দ বৃষ্টির মতো ঝরে, শীতল অথচ জ্বলন্ত, আমি বুঝতে পারি তবে বোঝাতে পারি না।
কিছু দুর এগিয়ে দেখতে পেলাম একটা মরা উটের পাশে গড়িয়ে পড়ে আছে ছিন্ন কোরআনের পাতা, ছিন্ন গীতা আর ছিন্ন বাইবেল —সব মিশে গেছে রক্ত ও ধুলোয়, যেখানে ঈশ্বরের কোনও আলাদা ঠিকানা নেই, আছে কেবল ব্যথার বিশাল শূন্যতা।
সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে দেখি আমার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে এক ম্লান শিশু ফাঁকা আকাশের হাত ধরে, কপালে এক বিন্দু ছাই মেখে। তার মুখ চেয়ে একটা প্রার্থনা আমিও করলাম - "আর কখনও "ঈশ্বরের" নামে যাতে কাউকে মরতে না হয়, তার চেয়ে বরং এই পৃথিবীতে শুধু ঈশ্বরই বাঁচুক।"
– "ভূস্বর্গে সেদিন, "ঈশ্বররা" ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। একমাত্র সাক্ষী ছিলাম আমি।"
গল্প

কমপ্লেক্স
কিশোর ঘোষাল
এস এন রায় রোড, কলকাতা
১
সাইকেলে বাজার থেকে ফিরে নিশীথবাবু রান্নাঘরের দুয়োরের পাশে থলেটা নামিয়ে হাঁক দিলেন, “কোথায় গেলে সব - হ্যারে তনু, এক কাপ চা খাওয়াবি মা?” উঠোনের ধারের কলঘর থেকে মণিকা সাড়া দিলেন, “থলে থেকে মাছগুলো বের করে, ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখ, তনু। ইল্লুতে বেড়ালগুলো ছুঁকছুঁক করে বেড়াচ্ছে… হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে, গোপেশ গোপীকাকান্ত ...”। মণিকাদেবী স্নান সেরে গামছা দিয়ে চুলের খোঁপা বেঁধে বের হলেন। তারপর উঠোনের দড়িতে ডিং মেরে ভেজা কাপড় মেলতে মেলতে বললেন, “পুরোনো তেঁতুল আনতে বলেছিলাম, ভুলে যাওনি তো?” নিশীথবাবু বারান্দাতেই বসেছিলেন, বললেন, “কিচ্ছু ভুলিনি, পুরোন তেঁতুল দিয়ে মৌরলা মাছের অম্বল…”।
তনু বাবার হাতে চিনি ছাড়া লিকার চায়ের কাপ ধরিয়ে বলল, “কোথায়? আমি তো মৌরলামাছ, পুরোন তেঁতুল কিছুই দেখলাম না, বাবা? চিংড়ি আর ভেটকি মাছ দেখলাম”। চায়ের কাপ হাতে নিশীথবাবু অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কী বলছিস?” “দেখবে?” দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দুটো থালা নিয়ে বারান্দায় এল তনু, “এই দ্যাখো”। নিশীথবাবুর হাত কেঁপে উঠল। অবোধ অসহায় চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
বারান্দা পেরিয়ে শোবার ঘরের কোনায় রাখা ঠাকুরের সিংহাসনের দিকে যেতে যেতে মণিকা আড়চোখে মেয়ের হাতের থালাদুটো দেখে মন্তব্য করলেন, “বিয়ের পর থেকে পয়লা মাসেও কোনদিন তোমাকে চিংড়ি-ভেটকি একসঙ্গে আনতে দেখিনি। আজ মাসের ছাব্বিশ তারিখ… লক্ষ্মীস্তং সর্বদেবানাং যথাসম্ভব নিত্যশঃ। স্থিরাভব তথা দেবী মম জন্মনি জন্মনি...”। আসনে বসে দুই চোখ বন্ধ করে মণিকা অতি দ্রুত মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। তারপর ঘাড়ে আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলেন সিংহাসনের ঠাকুরসমূহকে। তারপর দ্রুতপায়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।
রান্নাঘরের মেঝেয় বসেছিলেন নিশীথবাবু, সামনে কন্যা তনুজা আর দুজনের মাঝখানে মেঝেয় ঢালা আনাজের বিস্ময়। কেজি দুয়েক কড়াইশুঁটি, টোমাটো, দুটো নারকেল, ‘হাতিরমাথা’ দুটো ফুলকপি...। নিশীথবাবু অবাক হয়ে মেয়েকে বলছিলেন, “হ্যারে, আমি তো পুঁই-কুমড়ো, বাঁধাকপি, আড়াইশ কড়াইশুঁটি, একটা ছোটসাইজের ফুলকপি কিনেছিলাম। আর ছিল মৌরলামাছের প্যাকেটটা...সে সব এমন বদলে গেল কী করে বল তো, মা? এমনও নয় যে বাজারের থলি বদলাবদলি হয়ে গেছে...এই ব্যাগটা আমাদেরই তো...”।
তনুজা ফিক করে হাসল, বলল, “দশকর্মার দোকানে এমন নকশার থলে অনেক ঝোলানো থাকে বাবা, বদলে যে গিয়েছে, তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু কার সঙ্গে হতে পারে, সেটা মনে করার চেষ্টা করো”
নিশীথবাবু বললেন, “এই বাজারের বদলে, আমার থলেটা যে বাড়ি নিয়ে গেল, সে যে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেবে – সে তো বেশ বুঝতে পারছি”।
এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে মণিকা বাপ-বেটির কাণ্ড দেখে বললেন, “গবেষণা করে করবে কী, শুনি? এক কাজ তো করতে পার – পাড়ায় যত বাড়ি আছে, যত ফ্ল্যাটবাড়ি আছে – তাদের দুয়োরে দুয়োরে গিয়ে শুধিয়ে দেখতে পার...মৌরলার বদলে চিংড়ি-ভেটকি নেবে গো...”।
পত্নীর কথায় নিশীথবাবু খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, “কী যে বলো না, তার ঠিক নেই”।
মণিকা বললেন, “সে কথাই তো বলছি...ভেবে আর লাভ কি? তনু, আনাজগুলো যেমন ছিল থলেতে ভরে রাখ, মাছের থালাদুটো ফ্রিজে তুলে দে। তুমি বাইরে গিয়ে বসো, আমি জলখাবার নিয়ে আসছি। তনু, হাত চালা মা, অনেক বেলা হল...”।
সাততলায় উঠে ফ্ল্যাটের দরজায় বেল দিলেন সোমেশ্বরবাবু। কাজের দিদি সুলতা দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে বাজারের থলিটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “দিদি আজ দারুণ চিংড়ি পেয়েছি, বেশ গুছিয়ে মালাইকারি করো তো। তাছাড়া ভেটকি আছে – ফুলকপি দিয়ে জমিয়ে ঝোল...ওঃ আজ দুপুরের খাওয়াটা জমে যাবে”।
সুলতাদিদি হেসে ফেলে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, “চা খাবে তো”?
“জলখাবার হয়নি?”
“হয়ে গেছে। লুচিকটা ভাজতেই যা দেরি...”।
“তাহলে আর চা নয়, জলখাবারই দাও”। সোমেশ্বরবাবু বসার ঘরের সোফায় বসে নিশ্চিন্তে খবরের কাগজটা খুললেন।
সোমেশ্বরবাবুর স্ত্রী সুলগ্না ছেলেকে নিয়ে ক্রিকেট-কোচিং করাতে নিয়ে গিয়েছেন। কোচিং সেরে ফিরতে ফিরতে ওদের একটা-দেড়টা হয়েই যাবে। অন্য রোববারগুলো ছেলেকে নিয়ে সোমেশ্বরবাবুকেই দৌড়তে হয়। আজ সুলগ্না গিয়েছেন। ওঁর কোন এক বান্ধবীর বাড়ি বিবেকানন্দ পার্কের আশেপাশেই। সে বান্ধবী কেনটাকিতে থাকেন – দিন কয়েকের জন্যে কলকাতায় এসেছেন। ছেলেকে কোচিংয়ে দিয়ে সুলগ্না তার বাড়িতে যাবেন, সুখ-দুঃখের গল্প করতে। রবিবারের এমন নিশ্চিন্ত-নিরিবিলি সকালটাকে বৃথা যেতে দেওয়ার মানে হয় না, অতএব সোমেশ্বরবাবুর ইচ্ছে, জলখাবার সেরেই ভদকা নিয়ে বসবেন।
খবরের কাগজের প্রথম চারটে পাতার বিজ্ঞাপনে চোখ বোলাতে বোলাতেই সুলতাদিদি প্লেটে চারটে লুচি আর আলুর তরকারি নিয়ে হাজির হলেন। গরমগরম ফুলকো লুচির চেহারা দেখেই সোমেশ্বরবাবুর খিদেটা চাগিয়ে উঠল, বললেন, “ওফ দিদি, তোমার জবাব নেই...। বৌদিকে বলতে যেও না, যেন। জিগ্গেস করলে বলবে, ওটের খিচুড়ি খেয়েছি”।
সুলতাদিদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে বললেন, “আরো দুটো দেব, দাদা, তারপর আর নয়, ব্যস। চা খাবে না কফি?”
“আর কিচ্ছু না। সে অন্য ব্যবস্থা আছে”।
“বুজেছি। তাহলে দু পিস মাছ ভেজে দিই?” সুলতাদিদি হাসলেন।
বড়ো তৃপ্তি করে ছটা লুচি শেষ করে সোমেশ্বরবাবু বেসিনে মুখহাত ধুয়ে নিজের ঘরে গেলেন। সেলার থেকে ভদকার বোতল, গেলাস বের করে, ডাইনিং হলে গেলেন, জলের বোতল নিতে।
সুলতাদিদি বাজারের থলি হাতে নিয়ে সামনে এসে বললেন, “এসব কী এনেছ, দাদাবাবু? কোথায় তোমার চিংড়ি আর ভেটকি? এই পুঁই আর কুমড়ো দেখলে বৌদিমণি কিন্তু খুব রেগে যাবেন। সঙ্গে আবার মৌরলা মাছ!”
“তার মানে? কী বলছো?” সোমেশ্বরবাবু থলিটা হাতে নিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে বললেন, “কী সর্বনাশ। তার মানে থলি বদল হয়ে গেছে”। বসার ঘরের সোফায় ধপ করে বসে, হতভম্ব সোমেশ্বরবাবু চিন্তা করতে লাগলেন, কী করে এমন হল? তিনি মাত্র একবারই থলিটা
নামিয়েছিলেন। তিনটে পান আর সিগারেট কিনতে গিয়ে, সেই পানের দোকানের পাশে। মনে পড়ল সেখানে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক দোকানীর সঙ্গে কথা বলছিল। দোকানী নিতাই সোমেশ্বরবাবুর চেনা। ওর থেকে তিনি নিয়মিত সিগারেটের বড়ো প্যাকেট নেন, তার সঙ্গে আজ নিয়েছেন তিনটে পান। দোকানী পান সাজা শুরু করতে সেই ভদ্রলোক বলেছিল, “আমি এখন তাহলে চলিরে নিতাই, দুপ্যাকেট বিড়ি আর দেশলাইটা খাতায় লিখে রাখিস”।
সোমেশ্বরবাবু মনে মনে অশ্রাব্য কিছু গালাগাল দিয়ে চিন্তা করলেন, ওই লোকটাই নির্ঘাৎ ব্যাগটা হাতিয়েছে। শালা চোর-চোট্টায় দেশ ছেয়ে গেল? একটু আনমন হয়েছ কি, ব্যাটারা চোখের কাজলটা পর্যন্ত ঝেড়ে দিচ্ছে! গুম হয়ে বসে সোমেশ্বরবাবু আরও কিছুক্ষণ ভাবলেন, নিতাইয়ের দোকানে ওই বিড়িখোর লোকটার খাতা আছে। তার মানে নিতাই ওকে ভালোভাবেই চেনে। নিতাইকে গিয়ে চেপে ধরলেই ওই পুঁই-কুমড়োখোর ছোটলোকের হদিস পাওয়া যাবে। সোমেশ্বরবাবু সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “দিদি থলেতে যা যা ছিল, কিছু বের করোনি তো?”
সুলতা বললেন, “তা করিনি, কিন্তু যে নিয়েছে তাকে তুমি এখন খুঁজবে কোথায়?” সোমেশ্বরবাবু লুচির আনন্দ এবং ভদকার স্বপ্ন ফেলে দরজা খুলে লিফ্টের দিকে ধেয়ে যেতে যেতে বললেন, “হতভাগাকে আমি খুঁজে বের করবই, দেখো না”।
নিতাইয়ের কাছে সত্যিই হদিস পাওয়া গেল। সোমেশ্বরবাবুর রাগ এবং উত্তেজনা দেখে নিতাই বলল, “উনি তো নিশীথস্যার। উনি আপনার ব্যাগ চুরি করেছেন? না দাদা, হতে পারে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছেন, কিন্তু চুরি? অসম্ভব। উনি এ পাড়ার বহুদিনের বাসিন্দা, ওঁনাকে আমরা ছোটবেলা থেকে চিনি। এ বাজারের সবাই চেনে। আপনি ওই জিতেনদার রিকশয় যান - জিতেনদা, ও জিতেনদা, এঁনাকে নিশীথস্যারের বাড়ি নিয়ে যাও তো। যান জিতেনদাই আপনাকে স্যারের বাড়ি নিয়ে যাবে”।
জিতেনের সাইকেল রিকশায় চড়ে সোমেশ্বরবাবু দুপায়ের ফাঁকে পুঁই আর মৌরলার থলি নিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। নানান অলিগলির প্যাঁচ বেয়ে সাইকেল রিকশ চালাতে চালাতে জিতেন জিজ্ঞাসা করল, “নিশীথস্যার কী করেছেন, দাদা?” সোমেশ্বরবাবু নিতাইকে যে উত্তেজনা নিয়ে তাঁর থলি চুরির কথা বলেছিলেন, এখন আর সেটা বলতে পারলেন না। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, “ইয়ে মানে, মনে হচ্ছে, একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে, ওঁনার সঙ্গে আমার বাজারের থলিটা বদলাবদলি হয়ে গেছে...”।
জিতেন হাসল, বলল, “তাই? বোঝো কাণ্ড। ও নিয়ে ভাববেন না, থলি আপনি পেয়ে যাবেন”।
সোমেশ্বরবাবুর গনগনে রাগটা ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসছিল। মৌরলা-পুঁই-কুমড়ো খাওয়া লোকটাকে এ পাড়ায় সবাই চেনে! আশ্চর্য! তার ওপর পানওয়ালা থেকে রিকশওয়ালা সবারই এত বিশ্বাস! তাঁর সোয়া দুকোটির ফ্ল্যাট, বত্রিশ লাখি গাড়ি। ছেলে বিখ্যাত স্কুলে পড়ে, ক্রিকেটের কোচিং নেয়। তাঁকে তাঁর কমপ্লেক্সেও তেমন কেউ চেনে না। কমপ্লেক্স তো অনেক বড়ো ব্যাপার, তাঁর নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ছতলা কিংবা আটতলার বাসিন্দাদের, তিনিই কি চেনেন? লিফটে ওঠানামার সময় অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, হাই, হেলো, গুড মর্নিং, গুড ইভনিং – ব্যস ওইটুকুই!
নোনাধরা দেওয়ালে সবুজ রঙের দরজার সামনে রিকশ থামিয়ে, জিতেন বলল, “এই যে নিশীথস্যারের বাড়ি”। তারপর ভেজানো দরজা ঠেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকতে শুরু করল, “তনু, এই তনু, স্যার কোথায় রে? এই দাদা স্যারকে খুঁজছে”।
রিকশ থেকে নেমে সোমেশ্বরবাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। সিমেন্ট বাঁধানো ছোট্ট উঠোন। একধারে তুলসীমঞ্চ। উঠোন ঘিরে ছোট ছোট ফুলগাছ, গাঁদা, টগর, জবা...। সামনে লোহার গ্রিল দেওয়া লম্বা বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়ি – বিবর্ণ, নোনাধরা…।
নিশীথবাবু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন, “কী ব্যাপার, বাবা জীতেন?”
সোমেশ্বরবাবু বললেন, “ইয়ে মানে, আজ নিতাইয়ের দোকানে আপনার থলির সঙ্গে আমার বাজারের থলিটা মনে হয় ...”। সোমেশ্বরবাবুর কথা শেষ করতে দিলেন না নিশীথবাবু, উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, “ওফ, আপনি আমায় বাঁচালেন, ভাই...বাড়ি এসে বাজারের থলি আজার করে যা আতান্তরে পড়েছিলাম...ভেতরে আসুন, ভাই, ভেতরে আসুন, হ্যাগো শুনছ, ওঁনার থলিটা গুছিয়ে দিয়ে দাও...”।
তনুজা থলিটা নিয়ে উঠোনে এল, মুচকি হেসে বলল, “কাকু, এই যে আপনার থলে”।
নিশীথবাবু সোমেশ্বরবাবুর হাত থেকে নিজের থলিটা নিয়ে তনুজাকে বললেন, “যা মা, মাকে গিয়ে বল, সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে”।
সোমেশ্বরবাবু বললেন, “থলিটা একবার চেক করে নিন ...”।
নিশীথবাবু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, “ধুর মশাই, পুঁই-কুমড়ো আর মৌরলা বুঝি চেক করা যায়? মৌরলা কেউ কোনদিন গুনেগুনে কেনে নাকি? বরং আপনার চিংড়ি আর ভেটকির পিস গোনাগুনতি...”।
সোমেশ্বরবাবু হাত তুলে কোনরকমে নমস্কারের ইশারা করে বললেন, “আচ্ছা, এখন তাহলে চলি?”
“আপনাকে নাহক হয়রান হতে হল...”
জিতেনের রিকশায় উঠে সোমেশ্বরবাবু পায়ের কাছে রাখা থলি থেকে চিংড়ি আর ভেটকির প্যাকেটদুটো হাতে নিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলেন…পনের পিস চিংড়ি আর ভেটকির পিস ছিল ষোলটা। জিতেন হঠাৎই রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে রিকশাটা দাঁড় করাল, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, “দেখে নিন, সব ঠিকঠাক আছে তো?” সোমেশ্বরবাবু একটু ইতস্ততঃ করেও প্যাকেট খুলে গুনলেন। তারপর মুখে বোদা হাসি ফুটিয়ে বললেন, “ঠিকই আছে”। জিতেন আবার রিকশা চালাতে শুরু করে জিগ্গেস করল, “আপনার কোন কমপ্লেক্স?”
“আকাশপথ”।
“ওঃ ও তো বিশাল কমপ্লেক্স… কমপ্লেক্স মানে অনেক বাড়ি বা মনের জটিল কারবার, তাই না দাদা? নিশীথস্যারের কাছে পড়েছিলাম, উনিই আমাদের স্কুলে ইংরিজি পড়াতেন…ইলেভেনে বাবা মারা গেলেন, তারপর থেকেই এই রিকশ…”।
অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নেমে, সোমেশ্বরবাবুর মনে হল - তাঁর আড়াইহাজারি বাজারের থলিটা দেওয়ার সময় ওই মাস্টার চেক করতে বলল না। কিন্তু দেড়শটাকার বাজারের জন্যে চেক করার কথা কেন তিনি ওই মাস্টারকে বলতে গেলেন? আসলে তিনি যে শুধু মস্তো এক কমপ্লেক্সেই থাকেন তা নয়, তাঁর মনের মধ্যেও গড়ে তুলেছেন গভীর কিছু কমপ্লেক্স, যে কথা মনে করিয়ে দিল জিতেন নামক রিকশাওয়ালাটাও!
গল্প
মহামারীর আড়ালে
ডাঃ রুদ্রজিত পাল
কসবা, কলকাতা

২৭/৩/২০২০ ১৭ঃ ৩৩
প্রিয় ডঃ দাস,
আশাকরি আপনি ভাল আছেন।
আমরা, কোচবিহারের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সেই জাল ওষুধের ব্যাপারটার জন্য আপনার কাছে এখনও কৃতজ্ঞ। আপনার সাহায্য ছাড়া সেই কেসটা সল্ভ হত না।
এই লকডাউন এ কেমন আছেন?
আপনাদের হাসপাতালে করোনার কেস এসেছে?
এখানে লাস্ট সপ্তাহে প্রায় ৩০০ কেস। সব হাসপাতাল ভর্তি।
ভাল থাকবেন।
অর্পিতা বসাক, আই পি এস
ডি সি (ক্রাইম)
কোচবিহার
---------------------
২৭/৩/২০২০ ২১ঃ০৯
হ্যালো অর্পিতা,
অনেকদিন পরে মেল করলে। মেল-এ তোমার নতুন পদন্নোতি দেখে খুশি হলাম। হাসপাতালে রাউনড দিয়ে জাস্ট ফিরছি। এখন গাড়িতে।
এখনও কলকাতা জেনারেল হাসপাতালে করোনার পেশেনট নেই। তবে আমাদের ওয়ার্ড রেডি।এখনও তোমরা আমাকে মনে রেখেছ এটা জেনে ভাল লাগলো।জাল ওষুধের কারবার এখন বন্ধ তো? এখন নিশ্চয়ই তোমাদের ক্রাইম রেট কম?
আমার চেম্বার এখন বন্ধ। তাই বাড়িতে বসে কিছু রিভিউ প্রবন্ধ লিখছি। এই মেলের সাথে একটা করোনার পার্সোনাল সেফটি ডকুমেন্ট জুড়ে দিলাম। করোনার জন্য যা যা সতর্কতা বলা হচ্ছে, সব মেনে চলবে।
ভাল থেকো।
ডঃ মৃণাল দাস
ফিজিশিয়ান, কলকাতা জেনারেল হাসপাতাল
---------------------
৩১/৩/২০২০ ১০ঃ২৩
প্রিয় ডঃ দাস,
আমাদের এখানে স্টেজ থ্রি মহামারি চলছে। কাল প্রায় ৪১০ টা নতুন কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।আমরা লকডাউন করে রেখেছি।
আমাদের এখানে অনেক ডাক্তার কোআরানটাইন-এ। ফলে হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব। একজন নতুন ডাক্তার আছেন, অনির্বাণ মজুমদার। বেশ ভাল। গত মাসে আমার মায়ের ট্রিটমেন্ট করেছেন।
উনি আমাকে একটা কেস নিয়ে একটু আগে ফোন করেছেন। আমি বুঝতে পারছি না এটার মধ্যে পুলিশের কিছু করার আছে কিনা। উনি সিনিয়ার কারুর সাথে কথা বলতে চান।
আপনার নম্বর শেয়ার করব?
অর্পিতা বসাক
---------------------
৩১/৩/২০২০ ১১ঃ৩৮
সরি।দেরি হয়ে গেল উত্তর দিতে। ফোনে টাওয়ার ছিল না। নিশ্চয়ই।আমার হোয়াটসআপ নম্বর টা দিও।হোয়াটসআপ......।।
৩১/৩/২০২০ ১২ঃ০৯
স্যার, আমি অনির্বাণ মজুমদার। স্পেশালিষ্ট এম ও, কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ
হাই। তুমি বোধহয় আমার থেকে ছোট। তাই না? অন্তত প্রোফাইল ছবিটা দেখে মনে হয়। কোচবিহারেই বাড়ি?
১২ঃ১০
না। কলকাতায়। আনন্দপুরে। স্যার আমি এবার এম ডি শেষ করে এখন বণ্ড-এ
১২ঃ১০
আরে আমার বাড়ি কালিকাপুরে! ওকে। কার আন্ডারে থিসিস করলে?
১২ঃ১০
ডঃ অমিত চক্রবর্তী ১২ঃ১১
আরে, এম ডি তে আমার জুনিয়ার। ১২ঃ১১
স্যার আপনাকে এই করোনার কজ অফ ডেথ নিয়ে আমার কিছু বলার আছে ১২ঃ১১
শিওর। ১২ঃ১২
স্যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো মৃত্যুর কারন এ আর ডি এস?তাই না? ১২ঃ১৩
তাই ত পড়লাম। ১২ঃ১৬
কিন্তু স্যার এখানে দেখছি সব এ আর ডি এস কেই করোনা বলা হচ্ছে ১২ঃ১৭
আসলে মহামারির সময় এরকম হতেই পারে। কেস লোড বেশি হলে তখন টেস্টিং এর সময় থাকে না ১২ঃ১৮
স্যার কালকের একটা কেস নিয়ে আপনার সাথে ডিসকাস করতে চাই ১২ঃ২১
---------------------
দেরি হল রিপ্লাই দিতে। সরি।
করোনা ওয়ার্ড এর ব্যাপারে পি ডব্লিউ ডি কথা বলতে এসেছিল।
কিন্তু তোমাদের কেস নিয়ে আমাকে বলার আগে তোমার বসের পারমিশান লাগবে যে ভাই ১২ঃ৪৪
স্যার এখন আমার ওপরে কেউ নেই। আমার বস কোআরানটাইন এ। ইউনিট এর আর এম ও অন্য হাসপাতালে ডিউটি তে। আমাদের প্রিন্সিপাল কে বলেছি। উনি রাজি। ১২ঃ৪৪
তোমাদের প্রিন্সিপাল কে? ১২ঃ৪৬
ডঃ মানব সাহা। ১২ঃ৪৬
আরে, আমার ক্লাসমেট। ব্রিলিয়ানট স্টুডেন্ট ছিল। তাহলে ঠিক আছে। ১২ঃ৪৬
স্যার কালকে আমাদের একটা কেস এসেছে। ৫৬ বছরের মহিলা। এ আর ডি এস। করোনা বলেই রিপোর্ট করা হয়েছে। এখন ভেন্টিলেটর এ। ১২ঃ৪৭
কিন্তু এখন জ্বর নেই। ১২ঃ৪৮
বাড়িতে কারুর হয় নি। আর বাড়ির লোক বলছে একদিনের জ্বরের পর এই অবস্থা। যখন এল, অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৬৯% ১২ঃ৫০
ওকে। আর কিছু? ১২ঃ৫২
আমি আপনাকে এক্স রে টা পাঠাবো? ১২ঃ৫৩
ওকে। কিন্তু আমি এখন দেখতে পারব না। কাজ আছে। পরে দেখে বলব।তুমি সঙ্গে ব্লাড রিপোর্টগুলোও পাঠাও। ১২ঃ৫৪
ধন্যবাদ স্যার। এক্স রে পাঠালাম।১২ঃ৫৪
---------------------
প্রিয় অনির্বাণ। এক্স রে দেখলাম। প্রবলেম কী? ১৫
স্যার, এটা কী করোনার পেশেনট এর এক্স রে? না অন্য কিছু? ১৫ঃ৩৪
কেন? লাংস এর দুদিকে ইন্টারস্তিশিয়াল ওপেসিটি। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম। প্রব্লেম কী?এরকম ই তো সব কেস রিপোর্ট দেখেছি। ১৫ঃ৩৪
না স্যার। আসলে খুব তাড়াতাড়ি এরকম সিভিয়ার নিউমোনিয়া হয়েছে। জ্বরের এক দিনের মাথায় এরকম হয় না। পাঁচ- ছ দিন পরে লাংস এ এরকম মারাত্মকপ্রদাহ হয়।আমি আপনাকে ল্যানসেট এর একটা কেস সিরিজের লিঙ্ক পাঠালাম। দেখুন।তাই আমি ভাবছিলাম এটা অন্য কিছু কিনা......... ১৫:৩৭
দেখলাম। তাহলে অন্য কিছু? তোমরা ইনফ্লুএঞ্জা বা স্ক্রাব টাইফাস দেখেছ? ১৫:৩৮
স্যার সব পাঠানো হয়েছে। ১৫
ওকে। এলে জানিও ১৫ঃ৪৯
কিন্তু তুমি পুলিশে ফোন করেছ কেন? ১৫ঃ৪০
স্যার, আসলে আমার সন্দেহ এটা পয়জনিং। ১৫ঃ৪১
হুম। ঠিক আছে। তুমি আমাকে নতুন রিপোর্ট এলেই জানাবে। ১৫ঃ৪২
---------------------
৩১/৩/২০২০ ২২ঃ৫৫
অর্পিতা,
কেস ডিসকাস হয়েছে।ব্রাইট ডাক্তার।
তোমাকে পরে জানাব।
ডঃ মৃণাল দাস
হোয়াটসআপ......
---------------------
০২/৪/২০২০
স্যার আপনাকে রিপোর্ট পাঠালাম। ১৩ঃ২২
দেখলাম। সব ইনফেকশান নেগেটিভ। পেশেনট কেমন আছে? ১৪ঃ০৩
স্যার খারাপ। হাই অক্সিজেন এ আছে। ইউরিন আউটপুট মাত্র ২০০ মিলি কালকে। ১৪ঃ০৩
আর পরে এক্স রে করেছ? ১৪ঃ০৪
হ্যা স্যার। পাঠাচ্ছি। ১৪ঃ০৫
দেখলাম। অনেক বেড়ে গেছে। একদিকের লাংস তো প্রায় সাদা। পেশেনট অজ্ঞান? ১৪ঃ০৭
হ্যা। ১৪ঃ০৭
তুমি পয়জনিং ভাবছ কেন? ১৪ঃ০৮
আসলে পেশেনট পার্টি হিস্ট্রি ঠিকমত দিচ্ছে না। একবার বলছে চার দিনের জ্বর। একবার বলছে ১ দিনের। তারপর আমাদের এখানে একজন গ্রুপ ডি স্টাফ ওদের পাশের বাড়িতে থাকে। সে বলল যে ওনার সাথে ওনার ছেলের গণ্ডগোল চলছে। ভর্তির আগের দিনও নাকি ছেলে মাকে যা তা বলে হুমকি দিচ্ছিল। ১৪ঃ১১
সে সব ঠিক আছে। কিন্তু পয়জনিং এর আর কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে? ১৪ঃ১২
স্যার একটাই বলার। যেএম ও পেশেনট কে টিউব পরিয়েছিল, সে বলছিল যে ওনার মুখের ভিতরটা ফুলে ছিল। জিভের ওপর একটা আস্তরণ পড়ে ছিল। সেদিন পাঁচটা করোনা কেস ঢুকেই ভেন্টিলেটর এ উঠেছে। ফলে একে নিয়ে ভাবার সময় ছিল না।কিন্তু আমরা আর কোনও কেসে এরকম দেখিনি। করোনাতে মুখে আলসার হবে কেন?
চোখের মণি নরম্যাল। ১৪ঃ১৪
জিভে লেয়ার বললে? মানে করসিভ বিষ? ১৪ঃ১৬
ওকে। পয়জন স্ক্রিন হবে?কোন পয়জন মনে হচ্ছে তোমার?
না স্যার। এখন টেস্ট বন্ধ।আর আমি বুঝতে পারছি না। ১৪ঃ১৯
ঠিক আছে। তুমি মানবকে বলে রাখ। আর হাসপাতালের ডকুমেন্ট যেন ঠিক থাকে। আমি পুলিশকে যা বলার বলছি। ১
---------------------
০২/৪/২০২০ ১৮ঃ৫৫
অর্পিতা,
যে কেসটার কথা বলেছিলে, সেটা একটু গণ্ডগোল মনে হচ্ছে।
খেয়াল রেখো। তবে এখনই ডায়েরি করো না। তাহলে পরে সমস্যা হবে।
আমাদের হাসপাতালে এখন ৩০-৪০ টা করোনা কেস। আমাদের মাস্ক আর গ্লাভস পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাদের ওখানে কী অবস্থা?
ডঃ মৃণাল দাস
---------------------
০৩/৪/২০২০ ০৯ঃ৩২
প্রিয় ডঃ দাস,
কেসটা আমাদের খেয়ালে আছে। আপনার কী মনে হয়?পয়জন?
আমাদের এখানে এখনও রোজ ১০০র ওপর কেস। আমরা পুলিশ থেকে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করছি।
আমার ছেলের কাল থেকে সর্দি হয়েছে। করোনা নয় তো?
অর্পিতা
--------------------------------------
০৩/৪/২০২০ ১১ঃ৪০
অর্পিতা,
ভয় পেয়ো না। সর্দি মানেই করোনা ভাইরাস নয়। ডাক্তার দেখিয়ে নাও। আর নয়ত আগেরবার আমি যে ওষুধ দিয়েছিলাম তাই খাওয়াও।
ডঃ মৃণাল দাস
হোয়াটসআপ......
-------------------------------------
০৫/৪/২০২০
স্যার, পেশেনট খারাপ। ১০০% অক্সিজেন এ অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৭০%। ইউরিন হচ্ছে না। দুদিকের লাংসই পুরো সাদা। ২১ঃ৩২
ঠিক আছে। প্রিন্সিপাল কে বলা আছে? ২২ঃ১৩
হ্যা স্যার। ২২ঃ১৪
মনে হয় বাঁচবে না। ২২ঃ১৯
ঠিক। কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট লিখবে না। সবাইকে বলে রাখ।আর পেশেনট এর মুখের ভেতরের ছবি চাই। ২২ঃ১৯
--------------------------------
০৫/৪/২০২০ ২২ঃ২১
অর্পিতা,
সেই ৫৬ বছরের পয়জনিং সন্দেহ করা কেসটা খারাপ।কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের বেড নাম্বার ২০৭।
আজ রাতেই মনে হয় ডেথ হবে।
ডঃ অনির্বাণ একা আছে।
তুমি কিছু কর।পোস্ট মরটেম লাগতে পারে।
ডঃ মৃণাল দাস
----------------------------------
০৫/৪/২০২০ ২৩ঃ১৯
ডঃ দাস,
আমাদের লোক আছে হাসপাতালে।কিছু হলে বডি মর্গে পাঠানো হবে।
আমি ওর বাড়িতে যাচ্ছি। কিছু এনকয়ারি আছে।
সব ব্যবস্থা আছে। তবে পোস্ট মরটেম করা মুশকিল। এখন যিনি এখানে অটপসি করতেন, তিনি নিজেই করোনাভাইরাস নিয়ে নার্সিং হোমে।
হোয়াটসআপ......
০৬/৪/২০২০
স্যার, পেশেনট ডেড। ০৩ঃ২২
বডি মর্গে। পুলিশ ছিল। বাড়ির লোক কিছু গুন্ডা এনে ঝামেলা করার চেষ্টা করেছিল। আমাকে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছিল যাতে আমি ভয় পেয়ে নরমাল ডেথ বলে লিখে দিই। পুলিশ থামিয়ে দিয়েছে।০৩ঃ২৪
পেশেনট এর লাস্ট এক্স রে, মুখের ছবি পাঠালাম। ০৩ঃ৩০
প্রিয় অনির্বান,সরি।
তবে যা বলেছিলে, তাতে এই মহিলার বাঁচার চান্স ছিল না।
এক্স রে-টা দেখেছি। তুমি যা বলেছ এতদিন, তাতে এটা প্যারাকোআট পয়জনিং মনে হচ্ছে।এত তাড়াতাড়ি ফুসফুসে আক্রমণ আর কিছুতে হয় না।
কাল নাইট ডিউটি ছিল। এক রাতে ৩৩ টা কেস। সবে ফিরছি।[কান্না ইমজি] ০৯ঃ৫৯
--------------------------------
০৬/৪/২০২০ ১১ঃ২৩
স্যার
পেশেনট মারা গেছে।
কাল রাতেই বাড়ি থেকে ছেলেকে তুলে এনেছি। আমার সন্দেহ হচ্ছে। উল্টোপাল্টা কথা বলছে। কিন্তু কিছু প্রমান পাচ্ছি না।
কাল রাতেই আপনাকে ফোন করেছিলাম। পেলাম না।
অর্পিতা
--------------------------------
৬/৪/২০২০ ১২ঃ০৮
প্রিয় অর্পিতা,
কাল নাইট ছিল। ফোন সাইলেন্ট ছিল। একটার পর একটা ইনটিউবেশান করছিলাম।
তুমি ওদের বাড়িতে খুঁজে দেখো তো প্যারাকোআট নামের কোন কেমিক্যালের বোতল পাও কিনা।
এটা বুনো ঘাস বা জংলি গাছ মারার জন্য চাষিরা ব্যবহার করে। আমার মনে হচ্ছে এটাই বিষ। তোমাদের ওখানে ফরেন্সিকের লোক আছে?
জানিও।
আর ছেলে কেমন আছে?
ডঃ মৃণাল দাস
---------------------------------
০৬/৪/২০২০ ১৪ঃ২৩
ডঃ দাস,
আপনি কি যাদুকর?
ওদের বাড়িতে প্যারাকোআট এর বোতল পাওয়া গেছে। মহিলার ছেলে জেরার মুখে স্বীকার করেছে যে সেই মায়ের ওষুধের বোতলে প্যারাকোআট মিশিয়ে দিয়েছিল সেদিন রাতে।
প্রথমে ওর প্ল্যান ছিল এমনি মৃতদেহ পুড়িয়ে দেবে। কিন্তু মহিলা শ্বাসকষ্ট বলায় তার মনে হয় যে ইন্টারনেট এ যেমন দেখেছে, করোনার উপসর্গ, এও সেরকম।
তখন সে করোনা বলে মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। প্ল্যান ছিল যে করোনার মৃত্যুর জন্য সরকার যে টাকা দিচ্ছে, সেটাও আদায় করবে।
আপনি না বললে এই কেসটা করোনা বলেই চলে যেত।
পরে আপনাকে পোস্ট মরটেম রিপোর্ট জানাব। ফরেন্সিকের ডাক্তারবাবু এখন সবে করোনা সারিয়ে ফিরেছেন। উনিও শুনে এই কথাই বললেন। আপনার মেল আই ডি উনি নিয়েছেন।
অর্পিতা
পি এসঃ ছেলে ভালই আছে। কিন্তু আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। একই ওষুধ খাব?
----------------------------------
০৯/৪/২০২০ ১৮ঃ২৩
মৃণাল,
কেমন আছিস? সেই কলেজের পর এই কথা হচ্ছে।
তুই কলকাতায় না এখনও সেই শিলিগুড়িতে?করোনার কেস আসছে হাসপাতালে?তোর ইউনিট এ আছে?
আমি সবে করোনা ইনফেকশান সারিয়ে ফিরেছি। এখন ভালই আছি।
তুই যে কেসটা দেখেছিলি, সেটা প্যারাকোআট বলেই মনে হয়। আমি অটপ্সি করেছি।
আমি গত ১১ বছর কোচবিহারেই। প্রথমে মাথাভাঙ্গা, এখন তুফানগঞ্জ।
তোর হোয়াটসআপ নাম্বারে একটা মেসেজ পাঠালাম।
ডাঃ ইমতিয়াজ আলি
ফরেন্সিক মেডিসিন
তুফানগঞ্জ
হোয়াটসআপ......
-----------------------------------------
০৯/৪/২০২০
স্যার, কেস সল্ভ হয়েছে। প্যারাকোআট পয়জনিং। আপনাকে ধন্যবাদ ০৭ঃ১১
আরে আমি কী করেছি? তুমিই ত যা দেখার দেখেছ। আমি অমিতকে ফোন করেছিলাম। তোমার কথা বলেছি। ০৭ঃ২২
এই ব্যাপারটা লিখে রাখ। পরে পাবলিশ করবে। এবারের মেডিসিন কনফারেন্সে এটা প্রেজেনট করব। কলকাতায় এলে আমার সাথে দেখা করবে।
আমার বাড়ির লোকেশান গুগল ম্যাপ থেকে শেয়ার করলাম।
তুমি কি এখনও একা ডিউটি করছ? আর কাউকে পোস্টিং দিয়েছে? ০৭ঃ২৫
না। এখনও একাই। কলকাতা যেতে দেরি আছে। এখন টানা ১৪ দিন ডিউটি।
তারপর ৭ দিন আইসোলেশান। তারপর যেতে দেবে। ০৭ঃ৪০
--------------------------
১০/৪/২০২০ ১৬ঃ২২
ডঃ দাস,
পোস্ট মরটেম রিপোর্ট পাঠালাম।
প্যারাকোআট বলেই রিপোর্ট দিয়েছে।
আমার সিনিয়ার বলছিলেন যে আগে নাকি এখানে অনেক এরকম কেস আসত।
আমি প্রথম দেখলাম।
আপনি ভাল থাকবেন।
অর্পিতা
---------------------------
১১/৪/২০২০ ১৪ঃ৪৪
অর্পিতা
ভাল কেস ছিল। তবে মহামারির সময় এই ঘটনা দেখা যায়। অপরাধীরা যুদ্ধ বা মহামারির সময় এভাবেই ক্রাইম লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।
আমি একটা পি ডি এফ পাঠালাম। পড়ে দেখ।
আমেরিকায় এরকম কেস এর রিপোর্ট আছে।
আর প্যারাকোআট এর মত বিষ খোলা বাজারে পাওয়া যায়, এটা ঠিক নয়। তুমি এখন ডি সি (ক্রাইম)। দেখ এটা বন্ধ করা যায় কিনা।
ডঃ মৃণাল দাস
হোয়াটসআপ......
-----------------------------
১২/৪/২০২০
স্যার, আজকে এখানকার টিভি তে কেসটা নিয়ে বলেছে। একটু আগে আমার সাক্ষাৎকার নিল। [হাসি ইমজি] আপনার নাম বলল না কেন? [স্যাড ইমজি] [স্যাড ইমজি] [থিঙ্কিং ইমজি] ১৯ঃ৫১
ছাড় তো। একে ২৫০ এর ওপর করোনা কেস। গ্লাভস নেই। মাস্ক নেই। তার ওপর টিভিতে নাম? পাগল হয়ে যাব। আর তুমি এটা ধরতে পেরেছ তাই; এরকম কত কেস যে অন্য জায়গায় হচ্ছে, তার হিসাব আছে?২১ঃ৫০
তুমি এরপর কী করবে? বণ্ড শেষ হলে? আমার মতে তুমি ইংল্যান্ড এ অ্যাপ্লাই কর।
কেসটা লিখে ফেল। নইলে পরে ভুলে যাবে। ২৩ঃ৫৫
---------------------------------
২৩/৪/২০২০ ১৩ঃ২১
প্রিয় ডঃ মৃণাল দাস,
আমাদের চার্জসীট দেওয়া হয়ে গেছে।
আপনাকে বলা হয় নি।
মহিলার দুই ছেলে আর মেয়ে মিলেই এই কাজ করেছে।
মায়ের কাছে তিনটে সোনার বালা আর একটা সোনার হার ছিল। সেগুলো বিক্রি করে কোন চিটফাণ্ডে টাকা রাখবে বলে এই কাণ্ড।কোচবিহারে এলে বলবেন। সেবারে আপনার ক্ষীরদই খাওয়া হয়নি। আমার মনে আছে।
আমাদের এখানে করোনার কেস একটু কমছে। গত তিন-চার দিন ধরে রোজ ৩০-৩৫-টার বেশি নয়।পরের সোমবার লকডাউন খুলে যাবে। আপনাদের কলকাতায় তো এখনও বেশ খারাপ অবস্থা। তাই না?
অর্পিতা
--- ---- ----- ---
Please mention the "name of the article and the author" you would like to comment in the following box... Thank you.






